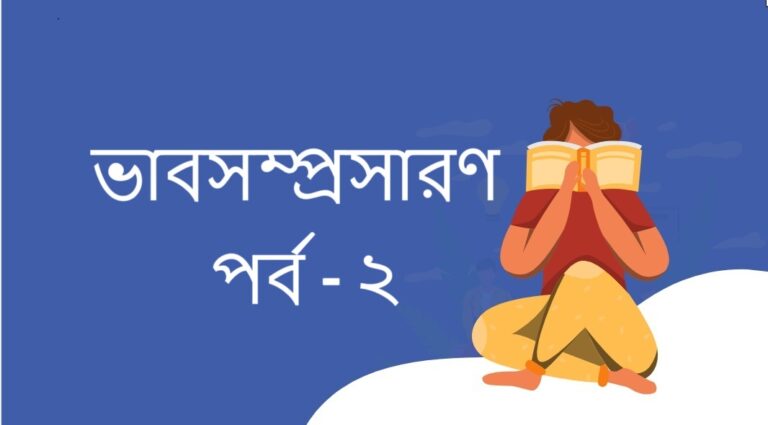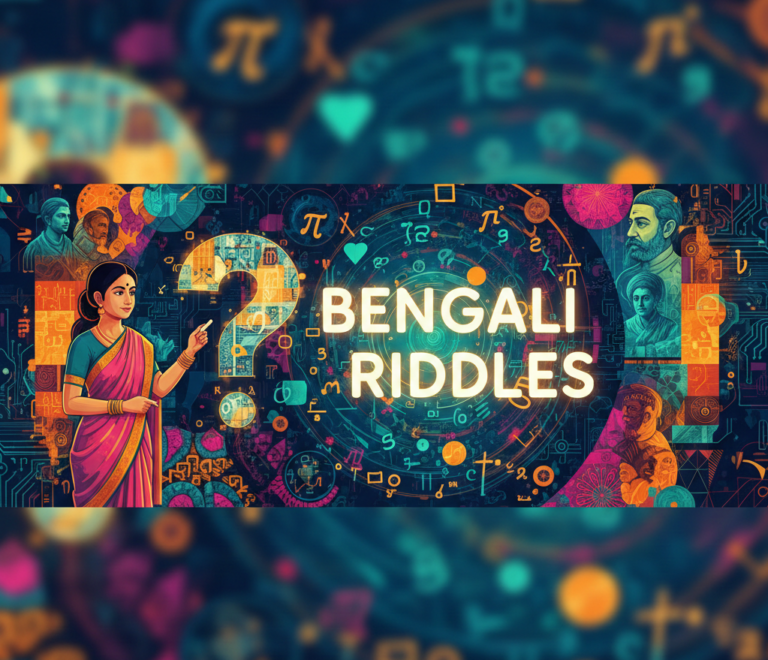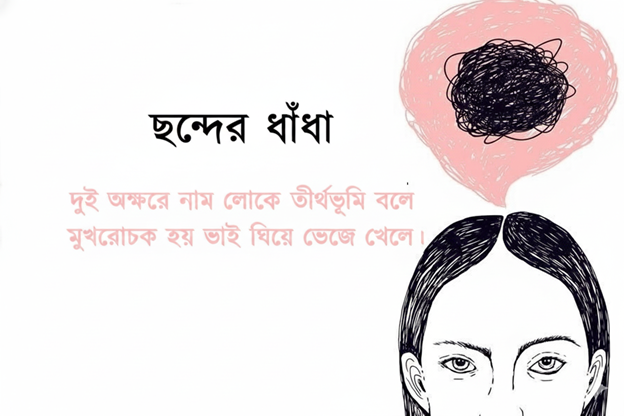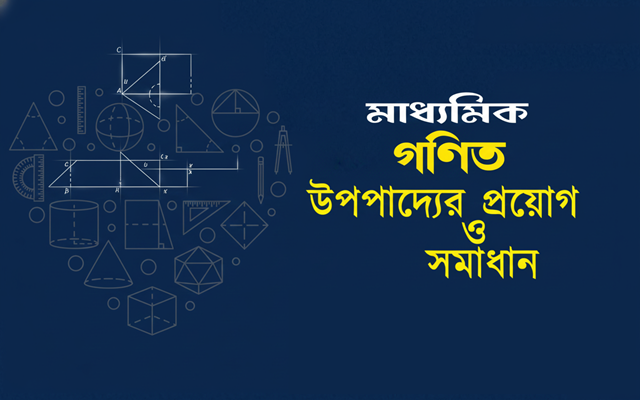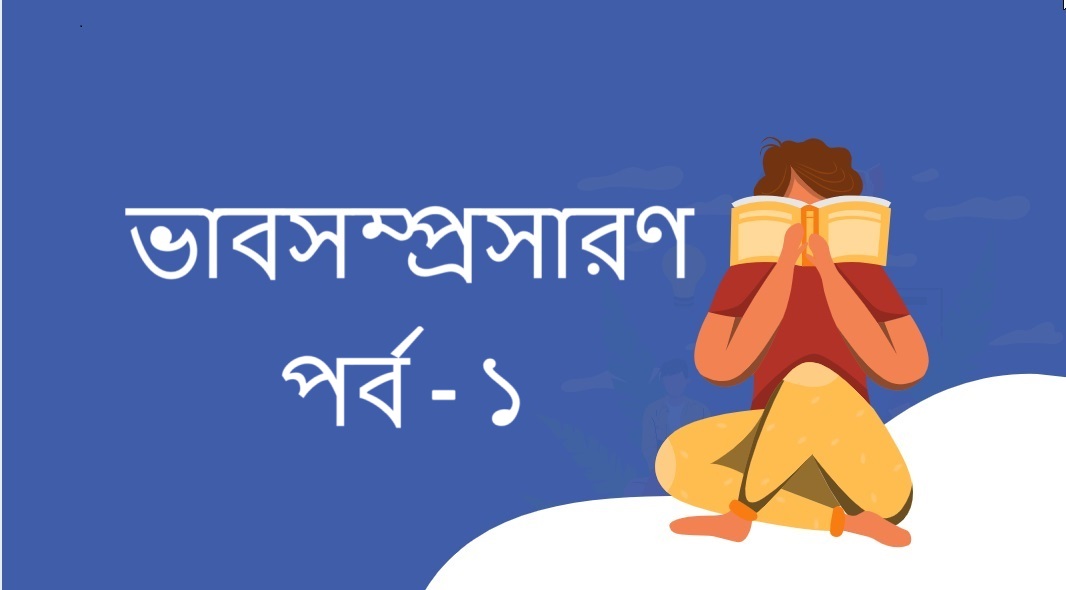
ভাবসম্প্রসারণ
ভাবসম্প্রসারণ | Vab Somprosaron in Bengali Grammar Notes to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapter ভাবসম্প্রসারণ | Vab Somprosaron in Bengali Grammar and select needs one.
Vab Somprosaron-bhabsomprosaron-Vab Somprosaron-bhabsomprosaron-Vab Somprosaron-bhabsomprosaronVab Somprosaron-bhabsomprosaron-Vab Somprosaron
১। কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকরা অনেকসময় তাঁদের চিন্তারাশির ফলে কখনো কখনো অতি অল্প কথায় সন্দররূপে প্রকাশ করেন। শিক্ষার্থীকে সেই ভাবটিকে ভালোরূপে হৃদয়ঙ্গম করে তার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে নিজস্ব প্রকাশ রীতির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে ।
২। উদ্ধৃত অংশটি বার বার পড়তে হবে এবং তার মূল ভাবটি প্রথমে বুঝতে হবে ৷
৩। উপলব্ধ ভাবধারাকে অবলম্বন করে স্বাধীন চিন্তা ভাবনার দ্বারা যুক্তি তর্ক সহযোগে মূল ভাবটি পরিস্ফুটে করতে হবে যা একটি অননুচ্ছেদ বা ক্ষুদ্রাকৃতির প্রবন্ধ বিশেষ হতে পারে।
৪। ভাবসম্প্রসারণ ‘রচনা’ অপেক্ষা দীর্ঘতর হবে ।
৫। মল রচনার শব্দ বা ভাষারীতি বিশেষ ব্যবহার করা উচিত নয়।
৬। প্রয়োজনে রচনার দু একটি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে তবে তার পরিমাণ স্বল্প হওয়া উচিত।
৭। প্রদত্ত রচনার উপমান ও উপমেয়কে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করে উপমেয়কে মূলভাব ও উপমানকে উহার উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করতে হবে । উপমান ও উপমেয় অংশ ব্যাখ্যা করার সময় প্রয়োজনবোধে দুটি অনুচ্ছেদ করা যেতে পারে।
৮। মূলভাবের অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলি সহজ ও সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে নানা রকম দৃষ্টান্ত—প্রাসঙ্গিক আখ্যান, প্রসিদ্ধ উক্তি প্রবচনের ব্যবহার করা যেতে পারে।
৯।ভাবসম্প্রসারণে—প্রদত্ত রচনার রচয়িতার নাম জানা থাকলেও নামোল্লেখ করা সঙ্গত নয়। মূল ভাষাটাকেই শুধু বিস্তৃত করতে হয় ৷
১০। ভাবসম্প্রসারণে নিজস্বতা থাকবার অবকাশ থাকবে, কিন্তু তা যেন প্রদত্ত প্রসঙ্গকে কোনক্রমেই এড়িয়ে না যায়। আবার আলোচনারও একটি পরিমিতি চাই। সম্প্রসারণটি ঠিক পরিমাণের মধ্যে ধরে রাখা দরকার তা পাতার পর পাতা আলোচনা আদৌ বাঞ্ছিত নয় ।
ভাবসম্প্রসারণ | Vab Somprosaron in Bengali Grammar
Here we have given detailed examples of ভাবসম্প্রসারণ | Vab Somprosaron in Bengali Grammar, You have to self practice a lot to master the skill.
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানুষ তাই সমাজবদ্ধ জীব। আর এই সমাজের মধ্যেই একে অপরের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আছে মানুষের প্রতি মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতা। সহযোগিতার বনিয়াদের ওপরেই আজ মানুষের যা কিছ, উন্নতি, প্রগতি ও সাফল্য নির্ভর করছে। সহযোগিতা ব্যতীত মানষ বড়হতে পারে না। হতে পারে না নিজের কোন আত্মিক উন্নতি বা দেশের কোন অগ্রগতি।
যখন কোন মানষ সত্যিকারের স্বার্থের উদ্ধে উঠতে পারে একমাত্র তখনি সে সার্থকনামা সামাজিক জীবে পরিগণিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় এই সমাজের মধ্যেই ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ প্রকট হয়ে ওঠে—তখনি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, এমনকি সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ মানুষের বন্ধনও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে । তাই প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন চেতনাভাবাপন্ন ব্যক্তির ভাবা উচিত এই ধরনের স্বার্থান্ধ আচরণ সমাজের মঙ্গল তথা জাতীয় কল্যাণের কত বড় অন্তরায়।সেই কারণেই সকল মানুষকেই তার স্বার্থ কিছু না কিছু ত্যাগ করতে হয়। তাতে অন্যের যেমন মঙ্গল হয় সমাজের সমধিক কল্যাণসাধন হয়। কোন মানুষের সত্যিকারের পরিচয়ই হল তার পরার্থ পরতায় সহমর্মিতায়, ও সহযোগিতায়।দেশ সেদিনই স্বর্গ হয়ে উঠবে যেদিন মানষ ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে অপরের কল্যাণে নিঃস্বার্থ হয়ে উঠবে শধুমাত্র তাদের মহান সেবাব্রতে। কারণ মানুষ মানষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য ।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে ।
মানব জীবনে চিরকালীন মূল্যবোধগুলো নিয়েই গড়ে উঠেছে মৌলিক ন্যায়- নীতির আদর্শ। সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহানভূতি ও সহযোগিতা নিয়ে বাঁচতে গেলে আমাদের আচার আচরণের প্রাথমিক মান রক্ষা করে চলতে হয় ।
কোন অন্যায় কখনো কারো সমর্থন পেতে পারে না। আবার যে সেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় সেও কখনোই ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না। অন্যায়কারীরা ঘৃণ্য অপরাধী। কারণ ন্যায় নীতির প্রচলিত বিধানগুলিকে এরা লঙ্ঘন করে। এরা নিন্দা এবং ঘৃণার পাত্র। কারণ সুস্থ ,সন্দর সমাজই মানসিকতাকে এবং আদর্শ নৈতিকতাকে এরা ক্ষুণ্ণ করে, তাই এরা সমাজে অকল্যাণ ও অমঙ্গলের সৃষ্টি করে ৷ যারা হয়তো কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়না বা এইসব এই সমস্ত সামাজিক অন্যায়ে যারা জড়িত থাকে তাঁদের অন্যায় কাজকর্ম দেখে তথাকথিত ভালোমানুষ সেজে থাকা নিরীহ গোবেচারা মানষগুলো তাদের প্রতিবাদ করার দায়িত্ব এড়িয়ে যায় যখন–তখনই অন্যায়ের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ অন্যায় কিছু করতে গেলে যদি বাধা না আসে বা ধরা পড়ার পরও যদি তাদের কোন শাস্তি না হয়- তাহলে উত্তরোত্তর ন্যায়নীতি হতে থাকে বিসর্জিত এবং অন্যায়ের হয় প্রতিষ্ঠা, তাই সমাজের চোখে অন্যায় যে করে ও অন্যায় যে সহে দুজনেই সমান অপরাধী।
সুস্থ শান্তিময় ও স্বাভাবিক সমাজ গড়তে গেলে মানষকে সচেষ্ট হতে হয় এবং মানবিক প্রত্যেকটি দায়িত্ব পালন করতে হয়— অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ এবং অন্যায়কারীকে শাস্তি বিধান করলে – সুস্থ পরিবেশ আসবেই। তাতে দেশের, সমাজের, ব্যক্তির সকলেরই মঙ্গল । নইলে অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী উভয়কেই সমাজের ধিক্কার একদিন দণ্ডিত করবেই।
কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে
হেনকালে গগণেতে উঠিলেন চাঁদা
কেরোসিন বলি উঠে, এস মোর দাদা।
অন্ধকারে মাটির প্রদীপ অপেক্ষা কেরোসিনের প্রদীপ অনেক বেশিই আলো দেয়। কেরোসিন বাতির শিখা মাটির বাতির শিখা অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং যথেষ্ট উজ্জল । এখানে কেরোসিন বাতির সঙ্গে ধনী লোকদের এবং মাটির প্রদীপের সঙ্গে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের তুলনা করা হয়েছে। যারা ধনী তারা গ্রাম্য সরল ভালো লোকদের ঠকিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে আরো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে এবং গরিবরা তাদের দারিদ্র্যের চরম সীমার তলায় নেমে যাচ্ছে। এই হোল সমাজ, যখন এই স্বার্থন্বেষী নিষ্ঠুর ধনীরা সংকটের সম্মুখীন হয় তখন আবার সাহায্যের জন্যই এবং এমনকি প্রাণ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় – এই দরিদ্র মানষগুলোকে। কিন্তু সেই আগেকার বঞ্চিত গরিবরা আর চিরজীবন অপরের ভোগের বস্তু হয়ে থাকেনি, থাকতে পারে না । তারাও মানুষ—ঠকতে ঠকতে তারাও ঠেকে শিখেছে ধীরে ধীরে। তাই একদিন যখন ধনীদের খারাপ অবস্থা এসে দেখা দেয় তখন কিন্তু গরিবরা তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। মানষেরই সৃষ্ট দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তখন চলতে থাকে অন্তকলহ । চাঁদ উঠলে কেরোসিন বাতি বা মাটির প্রদীপ উভয়েই নিষ্প্রভ হয়ে যায় নিৰ্মল জোৎস্নায়। অনুরূপ ভাবে এই কলহের সংযোগ নিয়ে বৈদেশিক আক্রমণের ঢেউ যখন দুর্বলভঙ্গর প্রাচীরে একের পর এক এসে আঘাত দিতে থাকে, তখন তাদের কিছুই করার থাকে না। এই অন্তিম মুহূর্তে তথাকথিত ওই ধনী এবং গরিবেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং পরস্পরের সঙ্গে তখন হাত মেলায় ।
কাজ করি আমরা যে তাই করি ভুল
কর্মীরা যখন কর্মোদ্যোগী হয়ে কোন কাজ করে, তখন অনেক সময় তাদের সে কাজে কিছু, কিছু ভুল হয়ে যেতে পারে—কারণ মানুষমাত্রেই ভুল হয় আবার মানষেকেই ভুল শোধরাতে হয়—অতএব ভুল করাটাই স্বাভাবিক; আর সেটাই অর্থাৎ ভুল করাটাই মানষের ধর্ম।
কেউ যদি কোনপ্রকার ভুল করে তবে আমরা তাকে অবশ্যই দোষ দিতে পারিনা । কারণ,—আমরা জানি যে, এই ভুল সে দ্বিতীয়বার ইচ্ছাকৃত ভাবে করার চেষ্টা করবেনা। কিন্তু সত্যিই যারা কর্মবিমুখ, অলস তারা কোন কাজ করার চেষ্টাও করে না। ফলে তাদের কাজে ভুল হবার কোনো আশঙ্কাও থাকে না ।
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না, অথচ সাঁতার শিখবার জন্য জলে নেমেছে, কেবল তারই জলে ডোবার সম্ভাবনা থাকে। যে ব্যক্তি তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে ব্যক্তির এই বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। কাজ করতে গিয়ে ভুল হলে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। কিন্তু যারা কাজ করে না, তারা ভুলও করে না এবং আলোচনার মুখে পড়ে না বা পড়ার সম্ভাবনাও থাকে না। আমরা সচরাচর সমাজে মোটামটি দধরনের মানুষ দেখতে পাই । একদল শোষক আর একদল শোষিত। শোষক যারা তারা শোষিতদের কাছ থেকে অর্থের দ্বারা শ্রম কেনে, কিন্তু কাজে ভুল হলে তাদের অকথ্য নির্যাতন করে। সাংসারিক সংখ শান্তি নষ্ট করে দেবার ভয় দেখায়। কিন্তু শোষকরা টাকার চূড়ায় বসে এই নিষ্ঠার কাণ্ডকারখানা উপভোগ করে। নিজেরা এই অন্যায়ের বলি হয় না । কারণ তারা শোষক, তাদের কাজ করতে হয় না—কিন্তু তাই বলে ভুল করবার আশঙ্কায় কর্ম বিমুখ হওয়া একমাত্র কাপরুষতারই নামান্তর মাত্র ।
ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ, অন্ধকার আলো,
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।
ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ, উত্থান পতন এ সবকিছু নিয়েই গড়ে ওঠে আমাদের এই মানব জীবন। দেশ কাল স্থান ও পাত্র ভেদে সবই আমাদের এই জীবনে কোন না কোন সময় এসে উপস্থিত হয়। ভালো কি, সুখই বা কাকে বলে—এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমরা পেতে পারি যদি কিনা মন্দ, দঃখ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের তেমন কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতা থাকে। কোনো মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ ভাল মন্দের এই অনুভূতিগুলি না এলে জীবনকে কোনদিন সে উপলব্ধি করতে পারবে না।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি অগাধ সুখ, পরম স্বাচ্ছন্দ, দারণ বিলাসিতা ও ঐশ্বর্যের সাগরে হাবুডুবু, খেতে খেতে হঠাৎ যদি সে দারিদ্রের জমাট অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, তাহলে সে তখন উপলব্ধি করতে পারবে সুখটা কি?
অতএব ভালো-মন্দ, সংখ-দুঃখ যখন মনুষ্য জীবনে বাধ্যতামূলক তখন এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই—বরং তাকে মেনে নিতেই হবে। এই জন্যই তো লেখকের উক্তি সখে দুঃখ অন্ধকার আলো এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলময় এই পৃথিবী—তার অনেক পণ্যবলে পাওয়া আমাদের এই মানব জীবন ।
যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে,
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার ।
কোন কোন নদী কখনো বা একটা একটা করে তার নিজস্ব গতি বা স্রোত হারিয়ে ফেলে, চলতে চলতে সে তখন অক্ষম হয়ে পড়ে। ঐ নদী ক্ষয় কার্যের দ্বারা যে সকল নুড়ি, পাথর সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে আসে, তা এই সময় নদীর গতিপথের সম্মুখে পড়ে চলার বাধা সৃষ্টি করে। এই সময় নদী হয়ে পড়ে ক্ষীণ, অতি শীর্ণ সামান্যতম জলপ্রবাহ-স্বরূপ। তার সেই অনিন্দসন্দর, লাবণ্যময়ী, সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ অনন্য তন্বী মূর্তি আর দেখা যায় না ৷
ঠিক সেইরকমই, যে জাতি, নিঃস্ব প্রাণহীন, পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেই জাতি একদিন অবশ্যম্ভাবীরূপে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। আর এই অনগ্রসর হয়ে পড়া মানেই, তাকে পড়তে হবে সমাজের জটিল নাগপাশে আবদ্ধ বিভিন্ন কুসংস্কারের মধ্যে। ফলে এই জাতি হয়ে পড়ে মেরুদণ্ডহীন। তার পক্ষে অগ্রগতি বা উত্থানের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ধীরে ধীরে অদূর ভবিষ্যতে সেই জাতি ধ্বংসের করালগ্রাসে পতিত হয় ।
এ জগতে হায়, সেই বেশী চায়, আছে যার ভুরিভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
ধন এমনই বস্তু, যা সন্তানের মৃত্যু দুঃখও ভুলিয়ে দের। নিরপরাধ ব্যক্তির বুকে নির্বিচারে নির্মমভাবে ছরি বিধিয়ে দিতেও কারো হাত কাঁপে না ৷ সেই ধনের লিপ্সা মানুষ কোনদিনই ছাড়তে পারে না ৷
দাঁড়াতে পারলে কেউ বসতে চায়, বসতে পারলে শুতে চায়, আর একবার শুতে পারলেই আলস্যে ঘামের অতল তলে তলিয়ে যাওয়া যায়। তাই যার একতলা বাড়ি হয়েছে সে দোতালা, তিনতলা করতে চায় ও গাড়ি ঘোড়ায় চাপার বাসনা জাগে তখন এইরূপে চাওয়া ক্রমাগত বেড়েই চলে। তাই এই ধন মানুষ যত বেশি পায়, আরও বেশি সে আকাঙ্খা করে। সুউচ্চ পর্বতসমান এই আকাঙ্খার কোন অন্ত নেই হবেনা কোনদিন এর শেষ ।
আমাদের সমাজে যারা ধনী বলে পরিচিত তাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ থাকা সত্ত্বেও তাদের অর্থলিপ্সা কোনকালেই মিটবার নয়। তাই তারা গরিবদের শ্রম চুরি করে এবং তাদের প্রাপ্য মজুরি না দিয়ে আত্মসাৎ করে নিজেদের অর্থ লিপ্সা মেটাতে চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও তাদের অর্থলিপ্সা মেটে না। যার দরুন তারা পুনরায় এই অসৎ কাজে লিপ্ত হয় ।
এই হোল আমাদের সমাজের বাস্তব রূপ। একশ্রেণীর মানুষ দিন দিন শোষিত হয়ে একেবারে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে, অপরদিকে আর একদল নিজেদের পূঁজি বাড়িয়ে মোটা কোলা ব্যাঙের আকার ধারণ করছে ।
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা
তাহাতে মহত্ব কিবা আর?
শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেইজন দেবতা আমার ।
মানুষ অন্য কোন ব্যক্তিকে বন্ধু, হিসেবে মেনে নেয় সেই ব্যক্তির দ্বারা সখে দঃখে সাহায্য পাবার আশায়—সময়ে অসময়ে বিপদে আপদে তার পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য। সতরাং সেই ভালবাসা উদ্দেশ্যপূর্ণ সকাম এবং স্বার্থ জড়িত। অবশ্যি ভালবাসা মাত্রেই প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা উদ্দেশ্যপ্রনোদিত। সুতরাং তাতে বৈচিত্র্য আর থাকল কি? মহত্ত্বই বা কতটুকু সে নিষ্কাম ভালবাসায়। যদি শত্রুকেও মিত্রের মত ভালবাসা যায়, তবেই তা হবে প্রকৃত প্ৰেম ।
উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তির শত্রু যদি কখনো বিপদে পড়ে, তখন ঐ ব্যক্তির উচিত তাকে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা করা। বিপদের সময় তাকে শত্রুভাবে না নিয়ে অন্য এক বিপদগ্রস্থ মানুষের মতই মনে করা উচিত। তবেই তো সে হবে মানষের মত মানুষ। মানুষ সমাজের জনদরদী নিঃস্বার্থ কল্যাণকামী প্রকৃত বন্ধু। অতএব যে ব্যক্তি শত্রুকেও বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি দেন, তিনি শুধু মহামানবই নন, তিনি দেবোত্তমও বটেন।
যারা শুধু, মরে কিছু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনা সম্মান ।
মানুষ মরণশীল। তাই মানুষের জন্ম নিলেই মরতে হবে। কেউ কখনো চিরকাল বেঁচে থাকে না । জন্মের হাত ধরে মত্যুও আসে। প্রত্যেকটি জীবনে তাই মৃত্যু অবধারিত। সতরাং মৃত্যু মানষের একদিন না একদিন আসবেই ।কিন্তু সেই মৃত্যু যদি পরোপকারার্থে হয়, তবে তা নিদেনপক্ষে সামান্য কিছ মানষের মনেও চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। মনুষ্য জীবন হল জীব-শ্রেষ্ঠ জন্ম।
মানুষ যদি অপরের কাজে নিজেকে নিঃস্বার্থ ভাবে নিয়োগ করতে পারে, প্রয়োজনে মৃত্যুও হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে, তবেই তো জন্ম হবে সার্থক— সুন্দর, শাশ্বত ও অবিস্মরণীয়।
জানি মৃত্যু যখন আসবেই, তখন অপরের কাজে বা দেশের স্বার্থে জীবন ব্যয়িত করলে শত শত মানষের মনের মণিকোঠায় হৃদয়ের দেউলে চিরন্তন বিগ্রহে স্থাপিত হওয়া সম্ভব—স্মৃতির আসনে হয় তাঁর চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা। নশ্বর দেহের মৃত্যু ঘটলেও মানুষের মনে সে বেঁচে রয় চিরকাল। তাইতো কবি বলেছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু কারো উপকারার্থে নয়, সেই ব্যক্তিকে কেউ কোনদিন সম্মান জানাবে না ।
স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে,
সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে ।
স্বার্থমগ্ন যেজন, স্বার্থই যার কাছে অন্যকিছর থেকেও অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়, সে কখনো কোনদিনই বৃহৎ জগৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনা। সে চার দেয়ালের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চায়, তার চিন্তা আপন সর্বস্ব। সে কি করে বৃহত্তর জগৎকে প্রত্যক্ষ করবে? জীবনের প্রকৃত আনন্দের সন্ধানই সে পায়না। অতি সামান্য তুচ্ছ কয়েকটি দিনের আনন্দ বজায় রাখতে সে হাত দিয়ে দূরে ঠেলে দেয় জীবনের প্রকৃত আনন্দকে ।
ছোট্ট চার দেয়ালে বিশিষ্ট ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে থাকতে একদিন তার মনটাও ছোট হয়ে যায়। সেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে উন্মুক্ত হাওয়ায় নিজেকে মিশিয়ে দিতে তখন তার ভয় হয়—পাছে কষ্ট বা বিড়ম্বনা অথবা সমস্যার পাহাড় এসে জগদ্দলের মত সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিজের স্বার্থ ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই সে ভাবতে পারেনা। সেই স্বার্থ’কে রূপ দিতে যে কোন হীন গর্হিত কাজ করা তার পক্ষে তখন কোন ব্যাপারই নয়। প্রয়োজনে অন্যকে ক্ষতি করেও সে স্বার্থকে বড় করে তোলে । অথচ এই পৃথিবী মানষের কাছে অনেক কিছুই আশা করে— যদি অপরের জন্য ভাবতে না পারলাম, অপরের দুঃখে শোকে সমবেদনার ভাগীদার না হতে পারলাম, তবে মানুষ ও পশুর মধ্যে তফাৎটা রইল কোথায় ? তাই স্বার্থপর মানুষ সত্যিকারের সখে ও পার্থিব আনন্দ থেকে একেবারেই বঞ্চিত ।
চলে যাব তবু আজিও যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল ।
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ।
মৃত্যু অনিবার্য । তাই, একদিন না একদিন মৃত্যু আমাদের হবেই। বিশ্বের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এখন সম্পূর্ণরূপে কলুষিত। তাকে এই দূষিত আবস্থা থেকে মুক্ত আমাদেরই করতে হবে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি অঞ্চল এখন দুষিত।পৃথিবীর উর্বর ভূমি হয়ে পড়ছে বন্ধ্যা। ফলে, ভবিষ্যতে হয়ত উত্তর পুরুষদের আয়ু অত্যন্ত হ্রাস পাবে এবং তাদের উপর নেমে আসবে বিকলাঙ্গতা নিদারণ অভিশাপরূপে। সতরাং আমাদের আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের আয়ু, অত্যন্ত সীমিত। তা সত্ত্বেও যতদিন মৃত্যু না আসে ততদিন পৃথিবীর দূষণ রোধ করার চেষ্টা করতেই হবে। নয়তো পৃথিবীর ভবিষ্যত হবে অন্ধকারময় । সতরাং দূষণরোধকে আমরা যদি প্রতিজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি তবে এ পৃথিবীর নবজাতকদের আমরা সুস্থ সবল জীবন যাপন করতে দিতে পারবো। আগামী দিনে সেই শিশুরাই হয়ে উঠবে দেশ ও জাতির কর্ণধার ।
“যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু, তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।”
যে ব্যক্তি অন্যের ভয়ে ভীত, সেই ব্যক্তি যদি তাকে দেখে আরো ভীত সন্ত্রস্ত হয়, তবে সে ঐ ব্যক্তির ওপর আরো চেপে বসবে এবং অকারণ অত্যাচার করবে । কারণ, সে জানে যে ঐ ব্যক্তি দ্বারা প্রতি আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু, দৈহিক বল থাকুক বা না থাকুক সে যদি রুখে দাঁড়ায়, তাহলে আক্রমণকারী কিছুটা অন্ততঃ ভয় পাবেই। কিন্তু, নির্বোধের মত অন্যায় সহ্য করে গেলে অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কোন প্রবৃত্তি বা ক্ষমতাই থাকে না । কারণ, এর মধ্যে আক্রমণকারী তার শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়েই গেছে। ফলে আক্রমণ এলেই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আমাদের যেকোন অবস্থাতে রুখে দাঁড়াতেই হবে ৷ নইলে আক্রমণকারী আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠবে ।
“সর্বজন সর্বক্ষম চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম যেথা নাহি জন্মে কোন মতে;
যেজাতি চলে না কভু তারি পথ পরে
তন্ত্রমন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।”
যে পথে সারাক্ষণ লোকজন চলাচল করে, সেপথে কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। কারণ, সর্বজনের অনবরত পদচালনার মধ্যে কেউ যদি মাথা উঠাতে চায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পদাঘাতে পিষ্ট হয়ে ধলায় পরিণত হয়। সেইরূপ, যে জাতির চারদিকে বিকাশ নেই, সেই জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, ভগ্ন মেরুদণ্ড কি তন্ত্র মন্ত্রে সোজা হয়? তার জন্য চাই নিষ্ঠা। সতরাং মেরুদণ্ডহীন শীর্ণকায় জাতি, কুসংস্কারে আবদ্ধ, সেইজাতির কোনও উন্নতি হবে না। উপরন্তু, দিনে দিনে শীর্ণ হতে হতে একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।
BhabSomprosaron-bhabsomprosaron-Vab Somprosaron-bhabsomprosaron-Vab Somprosaron-bhabsomprosaronVab Somprosaron-bhabsomprosaron-Vab Somprosaron
মৃত্যু কহে ‘পুত্র নিব’, চোর কহে ধন,
ভাগ্য কহে, ‘সব নিব যা তোর আপন ।
নিন্দুক কহিল, ‘লব তোর যশোভার,
কবি কহে, ‘কে লইবে আনন্দ আমার?
মৃত্যুর কাজই হোল স্থান কাল পাত্র এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই গ্রাস করা। ধনী অথবা দরিদ্র কেউই এর কবল থেকে মুক্তি পায় না । একদিন প্রত্যেকেই মৃত্যু কবলিত হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কেহই রেহাই পায় না । চোর যারা তাদের কাজ হচ্ছে চুরি করা। তারা এই চৌর্য বৃত্তিকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। ধনী বা দরিদ্র—যাদের গৃহেই হোক না কেন চোর ঢুকলে কিছু না কিছু, ধন সে চুরি করবেই ।
ভাগ্য এমন একটা জিনিস যা মানুষকে প্রচুর সংখ সমৃদ্ধি যেমন এনে দিতে পারে, তেমনি মহুর্তের মধ্যে মানষকে ঠেলে দিতে পারে দারিদ্রতার নিকষ কালো গহ্বরে। এরাই হোল যথাক্রমে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য। যারা নিন্দক তারা কখনো কারো প্রশংসা করে না। কোন ব্যক্তির উপর যদি তার আক্রোশ থাকে তরে তার সাথে যে দুর্নাম ছড়াতে পারে, অর্থাৎ তার যদি বিশেষ কোন কারণে খ্যাতিও থাকে তবে নিন্দকের ভাষ্যে তা ম্লান হয়ে যেতে বেশী সময় লাগে না। যিনি কবি তার গৃহের জন্য কোন ভাবনা থাকে না। প্রকৃতি, মানুষ প্রভৃতির ভিতর হারিয়ে যেতে তিনি ভালবাসেন । ফলে সখে এবং দঃখ একের মধ্যে যে কোন অবস্থায় পড়লেও তার চিত্ত আনন্দে থাকে। এখানে তাই বলা হয়েছে কেউ কবির আনন্দ নষ্ট করতে পারে না ।
“যে একা সেই ক্ষদ্র, সেই সামান্য।”
সমাজে যে একা, যে এই বিশাল পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে নির্বান্ধব সেই তো জগতে সর্বাপেক্ষা দুর্বল। তার বিপদে আপদে সাহায্যের জন্য কেউ-ই থাকৰে না । তা হলে সে বাঁচবে কি প্রকারে? কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সে সমাজবদ্ধ জীব। সতরাং প্রয়োজনে অপরের সাহায্য তাকে গ্রহণ করতেই হবে। উদাহরণস্বরূপে একটি কাঠিকে একগুচ্ছ কাঠি অপেক্ষা অতি সহজে এবং শীঘ্রই ভেঙে ফেলা যায়। কিন্তু একগুচ্ছ কাঠিকে ভাঙতে বেশ পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়। অনেক সময় তা সাধ্যের অতীত হয়ে যায়। ফলে এটা সহজেই বোধগম্য যে, কোন ব্যক্তি অপরের সাহায্য ছাড়া একাই সব কাজ করতে পারেনা, এবং অপরের সাহায্য থেকে যিনি বিচ্যুত সেই জগতে সর্বাপেক্ষা দুর্বল।
স্তুতি নিন্দা বলে আমি, গুণ মহাশয়,
আমরা কে মিত্র তব? গুণ শুনি কয়,
দুজনেই মিত্র তোরা শত্রু দুজনেই-
তাই বলি শত্রু মিত্র কারো কেহ নেই ।
স্তুতি এবং নিন্দা উভয়েই দুইটি বিপরীত মুখী পরিপূরক বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে উভয় বৈশিষ্টেরই স্থান আছে। কিন্তু কিছু কিছ মানষের ক্ষেত্রে এক একটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে। বাকি বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থিত থাকলেও যথাযথ সময় বিকশিত হয় না অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। কোন ব্যক্তি প্রায়শই নিন্দনীয় কাজে প্রবৃত্ত হলে তাকে নিন্দার্হ ব্যক্তি বলা হয়। অনরূপ যাদের কাজে অকাজে স্তুতি করার স্বভাব তাকে স্তাবক বলতে পারি। কিন্তু প্রকৃত গণেীর কাছে এই দুই ধরনের ব্যক্তিদের কোন স্থান নেই। নিন্দাহ’ ও স্তাবকবৃন্দের বাস্তব ক্ষেত্রে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু আবহমান কাল ধরে তাদের অস্তিত্ব স্বীকার্য। তাই প্রকৃত গণবান সর্বদাই এই সকল ব্যক্তিদের পরিহার করে চলেন । এই প্রসঙ্গে সরহ দোহাকোষের উক্তি প্রণিধানযোগ্য — “প্রিয়ের নিকটেও যাইবে না, অপ্রিয়র নিকটেও যাইবে না। প্রিয়র অদর্শন ও অপ্রিয়ের দর্শন সমান দঃখজনক।”
মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে।
কৃষ্ণবর্ণের সঞ্চারমান মেঘ-কুণ্ডলী ঘোর ঘন ঝঞ্ঝা ও প্রচণ্ড বর্ষণের সূচক। কখনো এই মেঘ-কুণ্ডলী প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবেরও ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া তাণ্ডব – প্রকৃতির উদ্দাম খেয়াল সাময়িক; তারপরেই রৌদ্রকরোজ্জল আবহাওয়ায় দিগন্ত পর্যন্ত সোনালী বর্ণে রাঙা করে তোলে। কবির ভাষায় এই সন্দর আবহাওয়া সুদিনের দ্যোতক ও গ্রাস সঞ্চারকারী মেঘমণ্ডল দুর্দিনের দ্যোতক, সাফল্য ব্যর্থতা কিংবা সংখ-দঃখ প্রত্যেকটি মানব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেন একে অপরের পরিপূরক। তাই সাফল্যকে যেমন হৃষ্ট-চিত্তে গ্রহণ করতে হবে তেমনি করে শত ব্যর্থতাতেও স্থীতধী থাকতে হবে। কারণ, রাত্রি হলে যেমন অনিবার্য ভাবেই দিনের প্রসঙ্গ এসে যায়, তেমনি দুর্দিন অর্থেই সুদিনের আগমনের পূর্বাভাষ। তাই কবি প্রত্যেকটি মানুষকে ‘সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মান’ বলে একাধারে মাভৈঃ দান করেছেন তেমনি অপরদিকে জীবনের পরম সত্যকে অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন।
যথাসাধ্য ভালো বলে, “ওগো আরো ভালো
কোন, স্বর্গ’ পরী তুমি করে থাকো আলো?
আরো ভালো কেঁদে কহে, “আমি থাকি হায়,
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ইচ্ছায়।”
মানুষের হৃদয় উচ্চাকাঙ্খী। সে তার স্বকীয়তাকে ছাড়িয়ে আরো উপরে উঠতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এই চাওয়া পাওয়ার লিসা অনন্ত অসীম। কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসের ভালো দিকের সঙ্গে বিস্ময় ফলও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করলেই তার হৃদয় চরিতার্থ হবে না। উপরন্তু জ্ঞানলিপ্সা হারিয়ে অকর্মণ্য, দাম্ভিকরূপে সমাজের জড় বস্তুতে পরিণত হওয়ার একটা বড় সম্ভাবনা আছে । “বিদ্যা দদাতি বিনয়ং’ কথাটি ঠিক ওই মুহর্তে তাদের কাছে বড় নীরস ঠেকে। তাই উপরোক্ত পংক্তিসমূহের মাধ্যমে এটাই পরিস্ফুট হয় যে, মানষের নিজের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুভ কিন্তু তা কখনোই যেন পণ্ডিতমণ্য- রূপে নিজেক্ষে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় পর্যবসিত না হয়ে যায় । কারণ, এইরূপে ঘটনা ঘটলে তাকে ভালত্ব পরিত্যাগ করে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে যা তার জ্ঞানভাণ্ডারকে ধ্বংস করা পক্ষে যথেষ্ট।
সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধূর॥
কত বর্ণে’ কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পূর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সূমধূর ৷
অসীম করুণাময় স্রষ্টার প্রকাশ তাঁর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির মধ্যে। তাই সর্ব- শক্তিমান ঈশ্বরের উপস্থিতি তাঁর সৃষ্ট পার্থিব জগতের মধ্যে অনভূত হয়। ঈশ্বর- প্রেমিক কবি প্রকৃতিক রূপে রস-গন্ধের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করে পুলকিত হচ্ছেন। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের হৃদয়ের মিলন ঘটে তখন তাঁদের এই অপ্রাকৃত প্রেমের পরিপূর্ণতা আসে। সেই প্রেমের জোয়ারে ভেসে যায় সমস্ত জাগতিক বন্ধন, লীন হয়ে যায় সমস্ত পার্থিব আশা আকাঙ্খা । ভগবান অসীম ও সমস্ত ভক্ত অসীম । তাই ঈশ্বরের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ভক্তের ক্ষুদ্র হৃদয়ান ভূতিতে তখন তার হৃদয় আনন্দ সমারোহে উদ্বেল হয়ে ওঠে ।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।
‘অতীত’—কথাটা আপেক্ষিক। দুই মহূর্ত আগের ঘটনা বর্তমানের তুলনায় অতীত। তেমনি দুই মহূর্ত পরের ঘটনায় বর্তমান অতীত। কিন্তু অতীত বলেই কোন ঘটনা অপাংক্তেয় হতে পারে না। কারণ, প্রত্যেকটি ঘটনারই কিছূ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্রিয়া আছে। স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে সমস্ত ক্লিয়া ফলপ্রসু হোতে পারে না । কিন্তু কিছু কিছ, ঘটনার সন্দেরপ্রসারী খাল আছে যা আমাদের মানসিক স্থৈর্য বিপন্ন করতে সক্ষম।তবে প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে নেতিবাচক মনোভাব আনাটা ভুল কারণ পূর্বোক্ত সন্দরপ্রসারী খাল আনন্দধারাও রোধ করতে পারে ।
তাহলে এটা স্বীকার্য যে প্রত্যেকটি ঘটনা তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শেষ হয়ে যায় না। বহু, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, বিদগ্ধ দার্শনিক মনে করেন যে, ভবিষ্যতের কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই সময়েবৃত্তের ফাটকে বন্দী হয়ে প্রত্যেকটি ঘটনা ঘরে ফিরে আসে। অতীত ভবিষ্যৎ হয়, ভবিষ্যত হয় অতীত। তাহলে, এই সকল যাক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় সাহিত্য ও দর্শনের অন্বিষ্ট সাধক রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নোক্ত উদ্ধৃতি যথার্থভাবে নির্ভুল ।
‘কহিল তারা, জ্বালিব আলোখানি
আঁধার দূর হবে না হবে
সে আমি নাহি জানি।’
স্বাধীনতা পেতে হলে শুধু, হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না, স্বাধীনতার জন্য চাই সংগ্রাম । এই সংগ্রাম রক্তক্ষয়ীত্ত হতে পারে। প্রথম সংগ্রামেই যে স্বাধীনতা আসবে, এটা বাতুলতা মাত্র । বাতুলতা মাত্র। তবে সেই প্রাথমিক সংগ্রামই স্বাধীনতার খড়ে দেবে আগুন । খড়ের গাদা সামান্য একটা, আগুনের ধোঁয়া পেলে যেমন ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠে, সেইরকম এই সংগ্রামই হবে স্বধীনতার প্রথম পদক্ষেপ। তাই লেখক অন্ধকারকে এখানে পরাধীনতারূপে ব্যক্ত করে বলেছেন যে, স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে সামান্য একটা আলোর ছোঁয়া দেখলেই যে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হবে তাতো নয়।স্বাধীনতা আসবেই, তবে ধীরে ধীরে ।
যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
কোন একদিন এই মহান ভারতবর্ষের পণ্যে তপোভূমি মুখরিত করে দিক-দিগন্তে ধ্বনিত হয়েছিল একটি সে মহান বাণী—আমরা সবাই অমৃতের পুত্র। তারই প্রতিধ্বনি উঠেছিল বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাসের কাব্যে — “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই” । কিন্তু কালের কুটিল ভ্রুকুটিতে ভুলে গেল ভারতবর্ষ’ সেই মহামন্ত্র । লোকাচারের নিষ্ঠার বিধানে জন্ম নিল মানুষে মানুষে বিভেদ। প্রাণের ঠাকুর হোল অবহেলিত। জাতিধর্মের ধয়ো তুলে স্বার্থ বাঁচাতে মানুষ মানুষকে দূরে ঠেলে দিল । সেই সব নিম্ন জাতির পতিত মানুষ পদদলিত হতে লাগল ধূলোর মত উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা । শুধু মিথ্যা জাত্যাভিমানের মোহে অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হোল নির্মমভাবে নীচ জাতিদের মাথায় । নির্বাসিত করা হোল অন্ধকারের অতল গহ্বরে, তাই শত সহস্র বছর ধরে অপমান ও অবহেলার বোঝা বইতে বইতে ভুলে গেছে তারাও একদিন মানষ ছিল। মননুষ্যত্বের যা কিছ, দাবি সবই তাদের কাছে আজ তাই অলীক আমার কল্পনায় পর্যবসিত। কিন্তু যারা এই মানবাত্মাকে চরম লাঞ্ছিত করেছে—মানষে হয়ে মানষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে মিথ্যে অপমানের বোঝা অবহেলা আর বঞ্চনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে এ অপমান শধু পতিতের নয়—এ অপমান সমগ্র মানবাত্মার । এ বৈষম্য ও অবিচার দূর করতে না পারলে পৃথিবীর সভ্যতা একদিন ধ্বংসের করাল গ্রাসে . পতিত হবে ।
জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতি মানূষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত একই রবি শশী মোদের সাথী।
বিশাল এ পৃথিবীতে নানা দেশে নানা শ্রেণীর মানুষের বসবাস। সমগ্র এই মানবগোষ্ঠী একই মহামানবধারারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অমৃতের পুত্রা — ঈশ্বরের সন্তান এই মানুষ—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নিখিল বিশ্বের এই মানবসমাজ একই চন্দ্র সূর্যের আলোয় স্নাত—একই স্নিগ্ধ হাওয়া-তাপে বর্ধিত, একই পৃথিবীর স্তন্যে লালিত। সূর্য যেমন তার কিরণ ‘বর্ষণে কোন বিভাগ মেনে আলোক বর্ষণে তারতম্য করে না, পৃথিবীর হাওয়া বাতাস, বৃষ্টিতে তেমনি তারতম্যের স্থান নেই । সতরাং পৃথিবীতে মানষের মধ্যে যে বৈষম্য ও প্রভেদ পার্থক্য তা শঙ্খ, এই মানষই সৃষ্টি করেছে। ধর্ম জাত ও সম্পদের ভারে মানুষে মানুষকে দূরে ঠেলে ফেলেছে। আর্য সমাজের প্রাণস্বরূপ যে আশ্রম ধর্ম তা আজ সমাজের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্মম বিধান শূদ্রকে সমাজের নিম্নস্তরে ঠেলে দিয়েছে। তাঁদের ছায়াস্পর্শেও উচ্চ সম্প্রদায়ের পাপ ৷ সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচবার সাংস্কৃতিক জীবন থেকে আজ পতিতরা তাই আজ বিচ্ছিন্ন । অথচ এই পৃথিবীর বুক থেকে জীবনরস সংগ্রহে যে সংগ্রাম তা সকলকেই করতে হয়— সেকথা উচ্চবর্ণীয়রা ভুলে যায়। বাইরের গায়ের রঙ সাদা আর কালো যাহাই হউক, সমাজের সে উচু নীচু বর্ণের যে বর্ণেরই হোক না কেন একই রক্ত কিন্তু সকলের মধ্যে প্রবাহিত যার রঙ লাল। এই জাতিভেদ সে রক্তে কোনদিন সামান্যতমও মলিনত্ব লাগাতে পারে না ।
মানুষই দেবতা গড়ে তাহারই কৃপার পরে
করে দেবমহিমা নির্ভর
দেবতা কি? তার অবস্থানই বা কোথায় ? এককথায় এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন । দেবতা কি স্বয়ং সৃষ্ট—না তাও নয়। পৃথিবীর এই মানষই দেবতার সৃষ্টি কর্তা । মানুষ যাকে দেয় দেবত্ব, সেই-ই হয় মানষের ভক্তি বেদীতে পূজিত ।
প্রাচীনকালে মানষের সামনে নানা প্রাকৃতিক শক্তি মাঝে মাঝে ভয়াবহ আকার ধারণ করতো, এবং মানষের স্বাভাবিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতো, আর তখন ষাদের জ্ঞানচক্ষ, উম্মীলিত হয়নি, তারা স্বাভাবিক ভাবেই এই বিষম ভয়ঙ্কর শক্তিকে পরম ঐশ্বরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করল, তখন থেকে হোল দেবতার আবির্ভাব । তখন থেকেই দৈবকে মানষ প্রবলভাবে ভেবে এসেছে আর তাই মনুষ্যত্ব ও পুরুষাকার তাদের নিকট তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে। দেবতা আমাদের কাছে অমর ; কিন্তু সে অমরত্ব আমরাই দিয়েছি—। মানষই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দেবতাকে অরূপ সৌন্দর্যে’র অধিকারী ও অলৌকিকতার দাবিদার করে তুলেছি। এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেই মানুষ আগে দেবতাকে খোঁজেনি – খাঁজেছে এই মানষকে। তারপরও তার কণ্ঠে ভাষার সৃষ্টি হলেও সে মানষেরই জয়গান গেয়েছে—ঈশ্বরের মহিমা গণকীর্তন করেছে, যখন প্রকৃতির প্রতিটি কাজের ব্যাখ্যায় অপারগ হয়েছে ; তখনই অমোঘ শক্তির দোহাই দিয়ে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করেছে ।
কিন্তু যে মানুষ নিজের আত্মশক্তিতে ভরপর ; নিজের মানসিক ও বৌদ্ধিক ক্ষমতার উপর আস্থাবান, দৈবকে পরোয়া না করে নিজের মানসিক শক্তিকে রূপ দিয়ে নতুন সৃষ্টির মহিমায় পৃথিবীকে আপ্লুত করে তোলে—তখন পৃথিবীর জনগণ তারই জয়গানে মুখরিত হয়ে ওঠে—একদিন কালে কালে সেই মানষটাই মানুষের কাছে দেবতার মত পূজ্য হয়ে ওঠে—যেমন রবীন্দ্রনাথ, নিউটন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষরা। এঁরা মহাযোগী ঋষি সত্যদ্রষ্টা—কোটি কোটি ভীরু, অমানুষ এমন বিরাট পুরুষের চারপাশে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। এঁদের চরিত্র ভালরূপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দেবতার দেবত্ব নির্ভর করে মানুষের ভক্তির ওপরে যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত – প্রবল পুরুষাকার চাঁদ সওদাগর, তাঁর বিপল পৌরষের কাছে দেবচরিত্রও হীনতর বলে মনে হয় ।
ধন্য করেছ মানূষে একদা মানূষের রূপ ধার
যে মানূষ মরিয়াছে
তোমার পরশে মৃতেরা লভুক প্রাণ!
সকল সৃষ্টির স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বর অজস্র বার মানষকে তার অমানুষিকতা থেকে -মক্ত করার জন্য, এই পৃথিবীতে কতবার যে মানবদেহ ধারণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই ।
কত কষ্ট, কত ত্যাগ আরো কত কৃচ্ছসাধনের পর শাশ্বত মনষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটেছে। কিন্তু মানষের চরম পাশবিকতা, নিষ্ঠুরতা, দয়াহীনতা সেই মনষ্যত্বকে নৃশংসভাবে অমানবিক ও অমানষিকভাবে হত্যা করেছে । মানব কল্যাণের মহাস্রষ্টা যীশু খ্রীষ্ট তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । মানবতার এই অপমৃত্যু পৃথিবীর ইতিহাসে বার বারই ঘটেছে এবং এমনি করেই পরম মনষ্যত্বের কন্ঠরোধ করে তারা পৈশাচিক হাসি হেসেছে ও আগামী পৃথিবীর উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে অবনতি ও অকল্যাণের পথকে সুপ্রসস্ত করে তুলেছে। সেজন্যই মানষের ইতিহাস গাঢ় কালিমাইয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বর ক্ষমাশীল ; তাই পথভ্রান্ত সেই সব মানষকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার মানষ স্বার্থপরতায় নিমগ্ন, সর্বগ্রাসী লোভের শিকার হয়ে মানষ আজ আত্মবিস্মৃত; অসৎ প্রবৃত্তির প্রেরণায় কল্যাণ করার শক্তি হৃদয় থেকে নির্বাসিত তাদের। এই অনন্ত সর্বব্যাপী অন্ধকার থেকে মক্ত করতে ঈশ্বর কবির ওপর ভার দিয়েছেন—কবি যেন তার কবিতার দ্বারা মানুষের সু প্রবৃত্তির উত্তরণ ঘটিয়ে কল্যাণের পথ দেখান । ভয়ঙ্কর এই পরিণতি থেকে মক্ত করে পর্ণে মানবাত্মা ও মননুষ্যত্বের খাঁজে পাওয়ায় পথ শুধু, ঈশ্বর ও কবিই দেখাতে পারেন—যাতে মানবাত্মার পূর্ণ গৌরব সে লাভ করতে পারে ।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।
পরম করুণাময় ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজিত। সকল জীবের মধ্যেই তাঁর অবস্হান। মানষই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু তাই বলে অন্য জীব- জন্তুও তুচ্ছ নয়। কারণ— তারা ঈশ্বরের করুণার দ্বারা লালিত পালিত । তাই জীবকে ভালবাসলে, সেবা করলে পরোক্ষভাবে সেই ঈশ্বরকেই ভালবাসা ও সেবা করা হয় ৷
প্রেম ও ভালবাসাকে যে মানুষ সকল জীবের সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন, তিনিই তো শ্রেষ্ঠ মননুষ্যত্বের অধিকারী। আমরা যদি অতীতের সিঁড়ি বেয়ে একট ইতিহাসের দিকে ফিরে যাই, তাহলে দেখতে পাবো, সকল জীবের প্রতি প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও করুণার জন্য এই মানুষই একদিন দেবতার আসনে অধিষ্টিত হয়েছেন ! বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, বাবা লোকনাথ ঠাকুর তাঁদের প্রাণঢালা প্রেম ও ভালবাসার দ্বারাই আজও মানুষের ভক্তির বেদীমূলে পূজিত হয়ে আসছেন। জীবের প্রতি করুণা ও ভালবাসাই যে ধর্মের মূলকথা তা বুদ্ধ, যীশূ শ্রীচৈতন্য নানাভাবে তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করে গেছেন। নিষ্ঠুর দেবদত্তের তীরে আঘাতপ্রাপ্ত একটি হংসের প্রতি যে প্রেম ও করুণা প্রদর্শন করেছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব তা আজও মানুষের হৃদয়ের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে। যীশ, তাঁর পরম করুনায় কুষ্ঠরোগীর রোগ নিরাময় করেছেন, চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে কলসীর কানায় প্রহৃত হয়ে—রক্তপাত দেখেও দুর্বৃত্ত জগাই মাধাইকে প্রেম বিতরণ থেকে পিছিয়ে আসেননি। ক্রৌঞ্চ মিথুনের উপর নিষ্ঠুর ব্যাধের হানা শরে ব্যথিত আদি কবি বাল্মীকির হাতে রচিত হয়েছিল-রামায়ণ মহাকাব্য । মোটকথা—প্রেম ও ভালবাসার বানী সর্বকালে সকল দেশের মনীষী, ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা আরাধিত ও প্রচারিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় স্বয়ং বিবেকানন্দ ও সেই প্রেমধর্মে’র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানষকে দেবতাজ্ঞান করে সকল ধর্ম সমন্বয়ে এক মহামানবধর্মে’র প্রচার করে গেছেন আজীবন। তিনি উপলব্ধি করেছেন,যে মানুষরূপে ঈশ্বর আমাদের পাশে পাশে রয়েছেন সর্ব সময় সেই মানুষকে ভালবাসলে পরম করুণাময়কেই সেবা করা হয়। জীবের প্রতি এইভাবে সেবার বাঁধনে যিনি বাঁধা পড়েছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মানুষ—এবং তাঁর সেবাই সর্ব শ্রেষ্ঠ।
প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন
ফূটিয়াছে ছোটো ফূল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক বলে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে, ভাল আছ ভাই?
সংসারে যারা ক্ষুদ্র, তাঁরা যদি হঠাৎ কোন গৌরবের কাজ কখনো করে বসে, তবে তাদের সেই গৌরবের স্বীকৃতি দেওয়ার মত উদার মানসিকতা খুব কম লোকেরই থাকে। কিন্তু সত্যিই যাঁরা যথার্থ উদারচিত্ত মানষ, তাঁদের কাছে ছোট বড়, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্রের কোন প্রভেদ নেই । প্রকৃত সমদৃষ্টি সম্পন্ন মানষে তাঁদের দৃষ্টির ব্যাপকতায়, অন্তরের বিশালতায় প্রত্যেকটি মানুষের সৃষ্টিকে স্বীকার করে নেয় এবং আন্তরিক প্রীতিসুধায় সকলকে অভিসিঞ্চিত করে সকল দীনতা মোচন করে মানষকে স্বজন ও বন্ধু করে নেন ।
একটি কাননের রূপকের মাধ্যমে ছোট বড়র মহৎ সত্যটিকে কবি তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সূর্যের অমল আলোয় বিকশিত হয়ে পাপড়ি মেলে অজস্র ফুল। মানুষের সৃষ্ট উদ্যানে সমাদরে স্থান পায় সন্দর এই ফল। হয়তো সেই উদ্যানেরই প্রাচীরের ছিদ্রে হঠাৎ একদিন সসঙ্কোচে ফুটে ওঠে নামগোত্রহীন অজ্ঞাতকুলশীল একটা ছোট্ট ফুল। কিন্তু উদ্যানের অন্যান্য অভিজাত ফলে তখন ওই নামগোত্রহীন ফুলটির দিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ও অবহেলার শানিত তাচ্ছিল্য ছড়ে দিয়ে তাকে বিবর্ণ ও ম্লান করে দিতে চায় । তারা তার সৌন্দর্যকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করে। ঠিক সেই সময় পূর্বদিগন্তে লাল আবির ছড়িয়ে অবারিত আলোর রশ্মি ঢেলে সূর্য উদিত হয়ে সেই অনাদতে অবহেলিত-উপেক্ষিত ফুলটিকে প্রথমেই জানালেন তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন-সম্বোধন করলেন অনুজ বলে ; জানতে চাইলেন তাঁর কুশলবার্তা। সূর্যে আপন মহত্বে মহীয়ান—তাই তার কাছে সবাই সমান। অভিজাত ফুলেরাও যেমন তাঁর কাছে ভালবাসার পাত্র – তেমনি ক্ষুদ্রফুলের ক্ষদ্রত্বের কথা একবারও চিন্তা না করে তাঁর পরিচয়হীনতাকেও মেনে নিলেন না। মহানমানুষের প্রকৃতিও ঠিক সার্যের মত। সমদৃষ্টি সম্পন্ন সংস্কার মুক্ত উদারচেতা মানুষ তাই চিরকাল সুর্যের মতই মানষের নমস্য।
শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই ।
ঈশ্বর তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যে যেমন আছেন, তেমনি বিশ্বচরাচরের সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান। কিন্তু মানুষ তার ঐশ্বর্যের অহংকারে মিথ্যে ঠুনকো জাত্যাভিমানে, ঈশ্বরকে ভুলে নিজের অহমিকার স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষ হয়ে মানষকে পণ্য মনে করে। মানুষকে জীবিকা করে তোলে। ধনৈশ্বর্য অভিজাত্যের গর্বে অশিক্ষিত, দরিদ্র নীচ অবজ্ঞাত শ্রমজীবি এবং সর্বহারাকে পশুতুল্য জ্ঞান করে। কিন্তু সে জানে না—অবিচ্ছিন্ন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে বিশ্বের মানবসমাজ একই পরিবার ভুক্ত। সেখানে একই মানবধর্ম। জাতি-সম্প্রদায় বলে কিছু নেই—যা আছে তা শুধু-কিছু কুচক্রী এবং স্বার্থান্বেষী মানুষ ভেদাভেদ সৃষ্টি করে— মানুষে মানুষে সাদাকালো, উচ্চ-নীচ-ব্রাহ্মণ-হরিজন, শক্তিমান-দুর্বল ধনী-দরিদ্র নানাধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করে চলেছে । শোষণের হাতটাকে আরো নিষ্ঠুর করে তুলছে। কিন্তু মানুষকে এভাবে বিভক্ত করা ভয়ানক অবিচার ও অন্যায়। এইভাবে যারা বিভেদের সৃষ্টি করেছে—ঈশ্বর তাদের প্রতি বিমুখ কারণ ঈশ্বর সেই স্বেদসিক্ত শ্রমিক, নিরন্ন কৃষক ও বেদনার্ত অন্ধ আতুরের অন্তরেই অবস্থান করেন—দেবালয়ের বিগ্রহে তিনি থাকেন না । তাই মানুষ না থাকলে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্বই থাকতো না । ভক্তের জন্যই ভগবান, নর আছেন তাই নররূপী নারায়ণ। তাই মানুষের আসল পরিচয় সে মানুষ। সেই মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব। মানুষই তাই সর্বোত্তম তার উপরে নাই—মানবধর্মের এই সত্যরূপকে মর্যাদা দেওয়াই আমাদের পবিত্র কর্তব্য।
পুস্প আপনার জন্য ফূটে না
পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসূমকে প্রস্ফুটিত করিও ।
অপরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আরো মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলে প্রস্ফুটিত বর্ণোজ্জল, সুরভি-উচ্ছল নানা ধরনের ফুলসম্ভার। ফুটন্ত ফুলের তখনই সার্থকতা যখন সে প্রস্ফুটিত ফুল দ্রষ্টার অনুভূতিতে সাড়া জাগায় তার, সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পথিকের আনন্দে নৃত্য করে ওঠে। নইলে এমনি মানুষের অন্তরালে কত না সহস্র অনামী ফুল ফোটে অনাদরে একটু একটু করে ঝরে পড়ে মাটিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে-রূপে রসে গন্ধে যে ফুল মানুষকে তৃপ্তি না দিতে পারে সে ফুলের মূল্য কতটুকু?
ফুলকে রূপক হিসেবে বর্ণনা করে কবি পরোক্ষভাবে মানুষেরই কথা বলেছেন । এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এককেন্দ্রিক হয়ে বাঁচতে যায়। কিন্তু এই বাঁচার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই—তাই মানুষ অন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে প্রবলভাবে দৃশ্যমান করে তুলতে চায়। অপরের সামনে নিজের সৃষ্টিকে তুলে ধরে, আপন সত্তাকে আরো বড় করে তুলতে চায়—সংকীর্ণ তার গণ্ডী ভেঙে হৃদয়ের দ্বার খুলে নিজেকে ফুলের মত প্রস্ফুটিত করে মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করতে চায় যাতে তার নিবেদিত সত্তাকে মানুষ উপলব্ধি করে আনন্দ পায়—উপস্থিতি আশা করে ও প্রয়োজনীয়তা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অনুভব করে। সত্য সন্দর ও শিবের সাধনাই সর্বোত্তম সাধনা । সেই সাধনার বলে মানষ নিজেকে ফুলের মত বিলিয়ে দিয়ে আপন ঐ বর্ষে বিকশিত হয়ে উঠবে এবং অন্যকে আনন্দের উপলব্ধিতে সন্দর করে তুলবে—এই তো সত্যিকারের জীবন সাধনা ৷
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?
পৃথিবীতে যে কোন আনন্দ ও সংখ সামগ্রী লাভ করতে হলে তার জন্য যেমন কিছু শ্রম দরকার তেমনি করতে হয় অনেক ত্যাগ ও কৃচ্ছ সাধন—সহ্য করতে হয় দারুণ দুঃখ ও কষ্ট। তবেই মেলে সেই বহু প্রত্যাশিত ও আকাঙ্খিত বস্তু । অনায়াসে প্রাপ্ত জিনিস সুলভ তাতে কি বা আনন্দ! যে দুর্লভ জিনিসের উপমা কবি এখানে উপস্থাপিত করেছেন— তা হল কমল -পদ্মফুল। সেই সুন্দের প্রস্ফুটিত পদ্ম মাননুষকে চিরকাল আকর্ষণ করে, মানুষ তাকে হাতের মুঠোয় পেতে চায়, আর হাতের মুঠোয় পেতে গেলে তার যে কিছু, কাঁটা আছে তুলতে গেলে স্বভাবতই কাঁটার জ্বালা সইতে হয়, কিন্তু যে কাঁটার জ্বালার কথা মনে করে ভয়ে পিছিয়ে আসে—তাকে দূরে থেকে পদ্মের শোভা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়— পদ্ম তাঁর আয়ত্বের বাইরেই থেকে যায় ৷
এইরূপে মানষের জীবনে চলার পথে অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়, অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সংগ্রাম করে অগ্রসর হতে হয়—তারপরে একদিন সে পৌঁছে যায় সুখ ও স্বচ্ছন্দের সে অমৃতলোক। চাষী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রৌদ্রে পুড়ে চাষ করে বলেই মাঠ ভরে যায় সোনার ক্ষেতে, তখন চাষীর মুখে ফোটে আনন্দ। তেমনি পাথর কেটে কুলি, মজুর সভ্যতা গড়ে দেয়—বলেই দেশ সুখে স্বচ্ছন্দ সমৃদ্ধি ও উন্নতির দ্বারে উপনীত হয়। বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র কঠোর পরিশ্রমে অধ্যবসায় করেছিলেন বলেই না তিনি সকলের আদরের ও শ্রদ্ধার বিদ্যাসাগর। তেমনি দুঃখ কষ্টকে এড়িয়ে সুখকে যারা পেতে চায় তারা চিরকালই সুখে থেকে বঞ্চিত হয় ।
শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির—
লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।
বিশাল দীঘির আর এক নাম জলাশয়; যে কানায় কানায় ভরে ওঠে শিশিরের সামান্যতম জলে নয় ; বৃষ্টির অজস্র জলধারায়। দিঘির এই জলেই শৈবালের জীবন —অস্তিত্ব। তাকে থাকবার অধিকার দেয় দিঘি—কখনো হিংসাও করেনা যাকে — কিন্তু শৈবাল প্রকৃতি থেকে যখন দু’ এক ফোঁটা শিশির লাভ করে, তখন সে সেই শিশির দীঘিকে দান করে ভাবে দীঘিকে সে কত দিল—অথচ দীঘি কৃতজ্ঞতাহীন এই শৈবালের কাছে কিছু, আশা করে না তাকে বাস করার অধিকার দিয়েও।
এ ধরনের ঘটনা মানব সংসারে নিয়ত ঘটে চলেছে। দিঘির মত বিশাল মাপের উদারচেতা মানুষ নিজেকে উজাড় করে নিঃস্ব হয়ে তাদের যা কিছু, অপরকে দান করে; প্রতিদানের আশা না রেখেই । অথচ ক্ষুদ্র, সংকীর্ণমনা মানুষ তাঁদেরই আশ্রিত থেকে আস্ফালন করে, তাঁদেরকে যদি কখনো সামান্যতমও উপকার করে তখন সেই ক্ষদ্রচেতা মানুষের অহংকার আর গর্বে মাটিতে পা পড়ে না । তাঁদের এই কৃতঘ্নতা দেখে মহতেরা হাসে এবং এই মনে করে সান্ত্বনা পান যে এ ধরনের মানুষ পৃথিবীতে চিরকালই থাকবে ।
দীঘির মত বিশাল মানষেরা ভালো করেই জানেন উপকার করলে একদিন না একদিন সেই উপকৃত ব্যক্তির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হবেন। এ জেনেও তাঁরা নীরবে চিরকাল মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ করে চলেন। তাঁরা তাঁদের সেই আত্মত্যাগের স্বীকৃতি কখনো আশা করেন না । কিন্তু নীচ ব্যক্তিরা শৈবালের মত সামান্য শিশির দান করেও তার হিসেব চায়। এটাই সবচেয়ে হাস্যকর।
চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?
জীবনে যারা কোনদিন দুঃখ পায়নি তারা কি বুঝবে দুঃখের বেদনা? ব্যথিতরাই শঙ্খ, উপলব্ধি করতে পারে ব্যথার সত্যিকারের বেদনা । যারা চিরকাল রাজ ঐশ্বর্যে পালিত, বিলাসিতার আতিশয্যে সখেমার্যায় নিদ্রা যায় তারা কতটুকু উপলব্ধি করতে পারবে দঃখ-কষ্টের কি নিদারণ ক্লেশ ও যন্ত্রণা। কবি সন্দর একটা উপমার মধ্য দিয়ে এই অসম্ভাব্যতাকে সন্দর করে ফাটিয়ে তুলেছেন । সর্প দংশনের উপমা দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে ব্যক্তি কখনো সপে দংশিত হয়নি সে কি করে বুঝবে সর্প দংশনের কি বিষম যন্ত্রণা! একমাত্র যাকে সাপে কামড়েছে সেই জানে সর্প দংশনের যন্ত্রণা ।
তেমনি দুঃখ ও কষ্টের বেদনাকে উপলব্ধি করতে হলে সুখ-শয্যা ছেড়ে দুঃখ ও বেদনা দিয়ে গড়া মাটির বুকে, দুখীর জীর্ণ কুটিরে কাটাতে হবে রাত—তবেই বোঝা সম্ভব হবে দঃখের কি বেদনা! এই কথার মধ্য দিয়ে একটি ঐতিহাসিক সত্যকে উদ্ঘাটন করেছেন কবি। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সঙ্গে কবির কথার অনেক মিল খাঁজে পাওয়া যায়—তদানীন্তনকালে অনেক রাজা তার রাজপোশাক খুলে পরিয়ে দিয়েছেন রাজপথের সর্বহারা কোন পথিকের অঙ্গে এবং তার ছিন্ন বস্ত্র নিজের অঙ্গে তুলে নিয়েছেন—এই ত্যাগ ও মহত্বের জন্য তারা যথার্থই চিরস্মরণীয় করণানিধান।
জন্মমৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা।
চলাই জীবনের ধর্ম । আর তাই চলতে গেলেই মাটি থেকে পা তুলে মাটিতেই আবার পা ফেলতে হবে।পা নড়াবার ভয়ে কেউ যদি সেই নিয়মে পা তোলা ফেলা না করে তবে তার চলার গতিই স্তব্ধ হয়ে যাবে—একই জায়গায় তাকে স্থির হয়ে থাকতে হবে। তাই পদক্ষেপের পরিবর্তন গতির অনিবার্য শর্ত। চলার মত জীবনের ক্ষেত্রে চলার অন্যতম ‘শর্ত’ হোল জন্ম মৃত্যুর পারম্পর্য। জন্ম মৃত্যু আছে বলেই পৃথিবীতে জীবনের প্রবাহ সচল ও সক্রিয় । এর সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটলেই জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যেত । জন্ম ও মৃত্যু তাই পরস্পরের পরিপূরক দুটি অনিবার্য সত্য—কখনোই তা জীবনের পরম্পর বিরদ্ধে নয়। জীবনের বৃহৎ দুটি সত্যের মধ্যে একটি আবার কোনভাবেই চূড়ান্ত সত্য নয় । জন্মের হাত ধরেই আসে মৃত্যু। জন্ম হলেই তাই তার মৃত্যু অনিবার্য । তাই মৃত্যু দঃখময় জন্ম নতুন জীবনের সাচনা করে আর মৃত্যু—নতুনতর জন্মের সম্ভাবনা বয়ে আনে । অনেকে ভাবে মৃত্যু বুঝি বিশেষ জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়। আসলে তা নয়, আগামী জন্মের সম্ভাবনাকে মৃত্যু নিশ্চিত করে তোলে—জাতক আবার নব- জীবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়েই—তাই জন্ম মৃত্যুর সক্রিয়তায় জীবনকে সবসময় সচল করে রাখে ৷
উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি থাকেন তফাতে।
আমাদের মানব চরিত্রের মধ্যে তিন শ্রেণীর মানুষ বিদ্যমান। যাঁরা জ্ঞানে গণে, শিক্ষা দীক্ষায়, চরিত্র মাধুর্যের উদারতায় শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই হলেন উত্তম । ভালমন্দের মাঝামাঝি অর্থাৎ মধ্যপন্থী মানুষেরা হলেন মধ্যম; আর অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অর্ধসভ্য মানুষদেরই অধম হিসেবে বিবেচিত করেছেন পণ্ডিতরা—তথা আপামর জনগণও তাই বিনা তর্কে’ স্বীকার করে নিয়েছেন।
সামাজিক জীবনে মধ্যপন্থীরাই সবচেয়ে ভয়াবহ । তারা না পারেন অধমদের সঙ্গে মিশতে, না মেনে নিতে পারেন উত্তমদের উদারতাকে।
‘উত্তম’রা শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী। তাদের মানসিকতা উন্নত। হৃদয় অনেক প্রসারিত। মন অনেক সংস্কারমুক্ত। তাঁরা হৃদয়ের নির্মল সুপ্রবৃত্তিগুলি মানষেরই কল্যাণে ও মঙ্গলে প্রস্ফুটিত করে তোলেন। সহানভূতিপূর্ণ মনের দুয়ার তাঁরা সব মানষেরই জন্য সর্বদা উন্মুক্ত করে রাখেন। এঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হোল প্রেম ভালবাসার দ্বারা অধমদের বুকে টেনে নেওয়া। অজ্ঞতা,অশিক্ষা বা সভ্য না হওয়া মানুষেরা এঁদের কাছে কখনোই দোষী নয় । এঁরা মনেও করেন না যে ওদের স্পর্শে তাঁদের শুচিতা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু মধ্যমরা নিজের মাঝারি মানের গাণাবলীর জন্য নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। তাই উত্তমের সে অবাধ্য হতে পারে না- তাই যেমন নিচে নামা বা ওপরে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয় না—মাঝপথেই চিরকাল আটকে থাকতে হয় ।
“অত্যাচারীর বিজয় তোরণ ভেসেছে ধুলার পর
শিশুরা তাহারই পাথরে আপন গড়িছে খেলার ঘর”
জগতের পাশব শক্তির ধ্বংস অনিবার্য । খুন, দাঙ্গা, রাহাজানি, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যত বীর্যাবতারই প্রকাশ হোক না কেন তা চিরস্থায়ী হয় না। অত্যাচারীর বেহায়া দম্ভ একদিন না একদিন নিশ্চিহ্ন হবেই। সাময়িকভাবে হয়ত অত্যাচারীর অত্যাচারে আমরা অতিষ্ট হই। কিন্তু এমন একদিন আসে যখন শক্তিমানের প্রবল বিভীষিকা-সৃজনকারী শক্তি ধূলায় পড়ে লুটিয়ে। যে হাতে সে একদিন নারকীয় তাণ্ডব শুরু করেছিল সেই হাত তার বিকল হয়ে পড়ে। তার অতীতের পাশব শক্তির ঘটে পরাজয়। তখন তার দাম্ভিকতার সর্ব প্রকার নিদর্শনই কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। মানুষের উপর চরম আঘাত হানে বলেই এই সমস্ত মানব পশু, মানবিকতার পরম শত্রু। কাল তাই তাদের ক্ষমা করে না । অপরপক্ষে যারা আজন্ম মানব সভ্যতাকেই অশেষ দানে ভূষিত করে তারা মানষের হৃদয়ের সামনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে । তাদের মৃত্যু নেই—তারা অমর শাশ্বত । তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ— মহাত্মা-সুভাষ-ক্ষুদিরামের মত মানুষেরা ।
“অনুগ্রহ দুঃখ করে দিই নাহি পাই
করুণা কহেন আমি দিই নাহি চাই।”
সাধু,সজ্জনের কয়েকটি সুকুমার প্রবৃত্তি থাকে। এইসব প্রবৃত্তির বশে তারা সাধারণ মানুষের থেকে নিজেদের পৃথক করে নিতে পারে । দয়া, মায়া, মমতা, অনুগ্রহ, করুণা ইত্যাদি সেইসব প্রবৃত্তি সমমূহের অন্তর্গত। কিন্তু সমস্ত প্রবৃত্তি সমান মর্যাদার অধিকারী নয়। জীবনে চলার পথে কখনও মানুষ মাননুষকে অনুগ্রহ করে কিছ, দেয়। কিন্তু তার এই অনুগ্রহ নিঃস্বার্থ নয় । তিনি অনুগ্রহ করেন এবং তার প্রতিদানে তার কাছু থেকে কিছু, প্রত্যাশা করেন। কিন্তু যিনি করুণাময়, সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে করুণা করাই যার স্বভাব, তিনি অকাতরে মানষকে করুণাই করেন, প্রতিদানে কিছু পাওয়ার বাসনা তার বিন্দুমাত্র থাকে না। করুণার আকর যিনি, তিনি তাই দৈবী স্বভাব প্রাপ্ত হন । লোকের কাছে তাই পরমপ্রিয়জন হয়ে থাকেন। এই সমস্ত দেবগণে-সম্পন্ন মানুষ সকলের
মানসলোকে চিরভাস্বর হয়ে থাকে। কারণ ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সাধু সজ্জনেরা নিজেদের জীবনকে অপরের জন্যে উৎসর্গ করেই আনন্দ লাভ করতে চান । মরেও যে মহৎ প্রাণে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণে তাঁদের সর্বদা নিবেদিত প্রাণ । মানুষের অন্তরাজ্যে ভগবানের মত ভক্তি ও পূজা পান অনন্তকাল ধরে ।
“শেফালী কহিল আমি ঝরিলাম তারা
তারা কহে আমারও তো হল কাজ সারা,
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের শেফালী”-
জগতে একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা নিজ সংখে নিস্পৃহ হয়ে পরের জন্য আত্ম উৎসর্গ করে। নিজের সংসারের সুখ সাচ্ছন্দ্য তাদের কাছে বড় নয় । দেশ ও বৃহত্তর সমাজই তাদের কাছে শ্রেয়। নিজেদের সংসার সীমার ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে যে বৃহত্তর জগৎ রয়েছে তার কল্যাণেই এরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ৷ কর্মতেই এদের অধিকার । ফলের দিকে এরা ফিরেও তাকায় না। নিস্বার্থভাবে যাঁরা এরকম কাজ করতে পারে তারাই পরবর্তীকালে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে ।পরের জন্য এইভাবে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে তারা হয় মহান। সেবাধর্মে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এইসব মানুষ চিরদিন মানুষের মনোজগতে ভাস্বর হয়ে থাকে ।
“মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যুতে যে বক পেতে দেয় বাঁচতে তারাই জানে”-
এজন্য সংসার জীবনে যারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে কর্মে বিরত হয়, যারা ভীরু কাপরুষের মত কেবলমাত্র সংসার সুখে মগ্ন থাকে, তারা কোনদিনই চিরস্মরণীয় হতে পারে না। মৃত্যুর পর মানুষ নিজ কীর্তির জন্য অমর হয়ে থাকে । এই সমস্ত কুপমণ্ডকের দল মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে কোন মহৎকর্মে ব্রতী হয় না। মৃত্যুর পরই তারা মানুষের মনোজগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু যারা দেশপ্রাণ, দেশ ও দশের কল্যাণে যারা গা ভাসিয়ে বৃহত্তর কর্মে আত্ম নিবেদন করে তারা জগতে কীর্তি রেখে যেতে পারে এবং এই কীর্তিই মৃত্যুর পরও তাদের বাঁচিয়ে রাখে, তাদের অমর করে তোলে ; ইতিহাসে তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ খাঁজে পাওয়া যায়। কত রাজরাজড়া এসেছে কালের চক্রে, এসেছে গুণ্ডা লন্ঠনকারীর দল, কিন্তু কে তাদের সবাইকে মনে রেখেছে। যে মানষের জন্য কিছ, রেখে গেছে সেই তো মরেও অমর হয়ে আছে—তার কীর্তি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন— অরবিন্দ, সুভাষ, মহাত্মা তিলক, ক্ষুদিরাম -এঁরা মৃত্যুকে পরোয়া না করে মৃত্যু জেনেও মানবত্মার কল্যাণে- পশু শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এনেছে স্বাধীনতা, তাই তাঁরা অমর—মাননুষের স্মৃতিটিতে ভাস্বর।
“পূজারী দুয়ার খোল
সুধায় ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজোর সময় হল”-
আমাদের দেশে একশ্রেণীর সাধক আছেন যাঁরা রুদ্ধ দ্বার কক্ষে সাধনা করেই ঈশ্বরকে পেতে চান। তাঁরা ভাবেন সংসার জীবনে কোলাহল মুক্ত স্থানই ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট স্থান। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ঈশ্বর সর্ব ভূতে বিরাজমান । তাই যেখানে পৃথিবীর লক্ষকোটি মানুষ সারাক্ষণ শতকর্মে রত থাকে সেখানেই ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাই ঈশ্বরকে পেতে হলে আগে মানষের সেবা করতে হবে, মানুষের সুখ দুঃখের অংশীদার হতে হবে । আমাদের সংসার সীমার বাইরে শত সহস্র মানুষ বঞ্চিতের বেদনা নিয়ে, অভুক্তের জ্বালা সহ্য করে মর্মে মরে আছে। তাদের মুখে অন্ন জুগিয়ে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইসব আর্তের উপযুক্ত সেবা করে তাদের মানুষের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে । তবেই প্রকৃত ঈশ্বর সাধনা হবে। মানষকে ঘৃণা করে তাকে পায়ে ঠেলে তাকে পাওয়ার সাধনা বৃথা।
“জাতি প্রেম নাম ধীর প্রবল অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়”
এ জগতের সব মানুষেই একই পরম পিতার সন্তান। জন্মেসুত্রে আমরা তাই পরস্পরের আত্মীয়। অথচ দেশের একশ্রেণীর মানুষ সংকীর্ণচেতা হয়ে জাতপাতের গণ্ডী টেনে নিজেদের মধ্যে জোর করে বিচ্ছেদ টানতে চায় । এক বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতকে ভালবাসতে গিয়ে তারা অপর বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতকে ঘৃণা করে। এভাবে তারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে জীবের মধ্যেই শিবের বাস। তাই ভগবানকে পেতে হলে জীবকেই সেবা করতে হবে। সব মানুষকে সমান ভাবে ভালবাসতে হবে। এক বিশেষ শ্রেণীকে ভালবাসার নাম করে অপর সম্প্রদায়কে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা অত্যন্ত অন্যায় এবং নীতি- বিগর্হিত। এই চিন্তাধারাকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না ।
“যে জাত ধর্ম— থুংক, আজ নয় কাল ভাঙ্গবে সে তো
যাক না সে জাত যাহার নামে রইবে মানষ নাই পরোয়া”-
সংকীর্ণচেতা মানুষই কেবল জাতপাতের গণ্ডী টেনে মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় । এই বিচ্ছিন্নতার মনোভাব মানষেরই সৃষ্ট। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ নিজে একটা কৃত্রিম ভেদরেখা টেনে মানুষকে পৃথক করতে চায়। এই মিথ্যা ভেদরেখা তাই চিরস্থায়ী
হতে পারে না । একদিন এর অবসান হবেই। এই সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান মুছে গেলে মানষ মানষকে পরম আত্মীয় বলে ভাবতে পারবে, তাকে কাছে টেনে, তাকে পরমানন্দে গালাগালি করতে পারবে। তাই আজ যারা আভিজাত্যের গর্বের নীচতলার মানষকে পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদের আচরণে ভীত সন্ত্রস্ত হলে চলবে না। একদিন তাদের ভ্রান্ত ধারণার ঠুলি খুলে যাবেই। তখন দেখা যাবে সব মানুষই আপন মর্যাদায় সপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
“চেরাপুঞ্জি থেকে একখণ্ড মেঘ ধার দিতে পার
গোবি সাহারার বুকে”-
বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি বিচিত্র তার রূপ—কোথাও সে মধুরা, কোথাও ভীষণা তাই প্রাকৃতিক জগতে দেখা যায় কোথাও অজস্র বারিপাত আবার কোথাও কোথাও সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা স্নিগ্ধভূমির আবার কোথাও রৌদ্রক্লান্ত বালুকো বহুল ধূধূ মরুভূমি। একদিকে প্রাচুর্য— অন্যদিকে রিক্ততা। তেমনি মানব জীবনেও দেখা যায় প্রাচুর্য, আমোদ আহ্লাদ । অন্যদিকে দেখা যায় শূন্য ভাণ্ড হাতে পাণ্ডর বর্ণ মুখে বিবর্ণ মানষের ভুখা মিছিল। এই বৈপরিত্য স্বাভাবিক ভাবেই মানব- আত্মাকে পীড়িত করে। কিন্তু নীতিকথায় বলে এই পৃথিবীর অন্ন, জলে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু দেখা যায় তা সত্ত্বেও তত্ত্বে এবং প্রয়োগে ভাবনায় এবং বাস্তবে আসমান জমিন ফারাক । প্রত্যাশা করা হয়েছে যারা দরিদ্র, অভুক্ত রোগাক্রান্ত সেইসব অপাষ্টির শিকারের জনতার জন্য একটু, সহানভূতি যাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে মানবসভ্যতার ইমারৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তারা কিন্তু অধিকাংশই ভুখা মিছিলের লোক । কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এক জায়গায় বলেছেন—
“ধূসের মরু, উষর বুকে একটি যদি শহর গড়
একটি জীবন সফল করা তার চাইতে অনেক বড়”।
এই দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ অসহায় বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষকে কিঞ্চিৎ সহানভূতি, কিছুটা সাহায্য, কিছুটা সহযোগিতা করলে তাদের মরুভূমির মত শুষ্ক জীবনে যদি বিন্দুমাত্রও মরূদ্যানের উদ্ভব হয় তবে সেটাই মানবিকতা। সুতরাং আমাদের সেই চেষ্টা করাই উচিৎ।
…দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার ।
অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সে অভিযোগে কতটা সত্যতা আছে তার কতটুকু অপরাধ তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে খতিয়ে দেখার নামই বিচার । খতিয়ে দেখার সেই ভাব ন্যস্ত হয় বিচারকের ওপর, যদি অভিযুক্তের কোন অপরাধ সত্যিই প্রমাণিত হয় তখন সেই অপরাধের তারতম্য অনুসারে বিচারক তাকে শাস্তি প্রদান করেন ৷ কর্তব্যের খাতিরে অভিযুক্তকে শাস্তি দিতেই হয়। কারণ বিচারকের
সেটাই কর্তব্য—তা সে শাস্তি যতই কঠিন হোক না কেন । সাধ করে কেউ অপরাধ নামক কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিতে চায় না। নানা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় মানুষকে নানাপ্রকার অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে হয় তার ফলে সে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করে সেই শাস্তি ভোগে তার নিজেরও যেমন ক্ষতি হয় তেমনি হয় সংসারের ক্ষতি, আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে তাকে হয়ত অনেক দূরে চলে গিয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয় অথবা কখনো তাঁর ভাগ্যে লেখা থাকে মৃত্যুদণ্ড। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমখি হতে হবে তাকে ন্যায়ধর্মের বিধানে। বিচারক দণ্ডদাতা কিন্তু দণ্ডিতের আঘাতের নির্মমতা সবসময়ই উপলব্ধি করেন, এবং তিনি দণ্ডিতের সমব্যথী হয়ে অনভব করেন ওই রকম শাস্তি পেলে কতটা আঘাত পেতেন এবং বিচলিত হতেন। দণ্ডিতের শাস্তি তাঁর মনে দুঃখ জাগায় এবং তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে বস্তুতঃ এধরনের বিচারেই বিচারকের শ্রেষ্ঠত্ব। এ ধরনের বোধের অভাব থাকলে যথার্থ’ বিচারক তিনি কখনোই হতে পারেন না।
বহুদিন ধরে বহু, ক্লোশ দুরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যলোকের আকর্ষণ মানষকে বার বার ঘরছাড়া করে উদাসী বহেমিয়ান করে তোলে। কারণ, মানুষ প্রকৃতিপ্রেমিক ভ্রমণবিলাসী । প্রকৃতি তাই যখন আমাদের হাতছানি দিয়ে তার অমৃত সৌন্দর্য লোকে আহ্বান করে তখন আমরা আর তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না। দূর্গম ও দূরের সৌন্দর্যের দিকেই আমাদের বেশি আগ্রহ। দুর্গম গিরি কন্দরের রহস্যাচ্ছিত সৌন্দর্য ও সাগরের শান্ত সমাহিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপ উপভোগ করার জন্য অজানা অচেনা দেশ ভ্রমণ করি । কারণ অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনাই তো মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। কিন্তু অজানা অচেনাকে দেখতে আমরা কত না পয়সা খরচ করি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েক লাইনের ছোট্ট কবিতার মধ্য দিয়ে সন্দর করে ব্যক্ত করেছেন যে পথ অতিক্রম করে এত সময় অর্থ নষ্ট করে ক্লেশ সহ্য করে পাহাড় ও সমদ্রের সৌন্দর্যের অবগাহন করতে যাই, অথচ প্রকৃতি যে আমাদের ঘরের কাছেই অকৃপণভাবে সৌন্দর্যের পসরা বিছিয়ে রেখেছেন তার খবর কি আমরা রাখি? ঘর থেকে দু পা বাড়ালেই চোখ দুটি আটকে যায় সকালের রৌদ্রস্নাত ধানের ক্ষেতে । ধানের শিষের ওপর মুক্তোর মত ঝলমল করে এক একটি শিশির বিন্দু। ছোট্ট হলেও অপরূপ সে সৌন্দর্য । এর জন্য ব্যয় করা বা দূরে যাওয়ায় প্রয়োজন নেই, দেখার চোখ আর সৌন্দর্য বোধ থাকলে বাড়ির কাছেই প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা সম্ভব। যে চোখ আমাদের নেই বলেই কবির দঃখ, আক্ষেপ ৷
যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি
আশূ গৃহে তার জ্বলিবেনা আর
নিশীথে প্রদীপ বাতি ।
‘অপচয়’ই মানুষের দুঃখ ও অভাবের কারণ। ইংরেজিতে একটি সন্দের প্রবাদ আছে waste not, want not অপচয় করোনা, অভাব হবে না। কবির সন্দর এই কবিতাটি একটি প্রবাদের সমতুল্য। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত করে । আর সেই অভিজ্ঞতাই কবির এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে বাণীরূপ পেয়েছে। ব্যবহৃত ‘রূপক’টি এখানে আলো জ্বালা।’ স্বভাবতঃ আমরা রাতের অন্ধকারে আলো জেলে অন্ধকার দূর করবার চেষ্টা করি। এই আলো জালার জন্য আগে থেকেই তার প্রস্তুতি গ্রহণ করি । তার জন্য গার্হস্থ মানষকে সংগ্রহ করতে হয় বাতি । যা মানষের অন্ধকারে আলো জ্বালাবার সহায়ক হয়। কিন্তু দিনের আলোকজ্জ্বল প্রহরে বিনা প্রয়োজনে বিলাসিতার কালি উল্লাসে অনেকে আলো জালিয়ে সেই বাতির অপচয় করে, পরে যখন রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে তখন আর আলো জ্বালাবার সংস্থান থাকে না, শধুমাত্র অপচয় জনিত অভাবেরই ফলে ।
আমরা এই অপচয়কে রোধ না করে যদি অমিতব্যয়ী হয়ে সঞ্চয় কিছু না করতে পারি, তাহলে আগামী দিনে অভাব ও দারিদ্র হাত ধরাধরি করে আমাদের সামনে এসে উপহাসের অট্টহাসি ছড়িয়ে আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। কারণ সবসময় ভাবা উচিত আজকের স্বচ্ছলতা আগামী দিনগুলিতে নাও থাকতে পারে। অমিতাচারের লজ্জাকর উচ্ছৃঙ্খলতার দূরারোগ্য ব্যধি মানষের শারীরিক সর্বনাশ ও সম্পদই শুধু অপচয় করেনা ব্যাক্তি জীবনের মত সমাজের সমষ্টিগত জীবনেও অন্ধকার নেমে আসে। সংসারের আত্মীয় স্বজনের তাতে দঃখও বাড়ায় ও সমাজ তার থেকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় কিছু, আশা করতে পারে না ।
কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল স্বামী
আমার যেটাকু সাধ্য করিব তা আমি—’
পৃথিবীতে যে ব্যক্তি নানা রকমের অনেক কাজ করে সেই কাজের সংখ্যাধিক্যে তার কোন সার্থকতা মেলে না যদি না সেই কাজে তাঁর আন্তরিকতা থাকে। বিরাট কিছু না করতে পারলে নাম যশ হবে না বলে আমরা অনেক কাজে হাত দিইনা, এটাই সবচেয়ে বড় ভুল। সাধ্যনুযায়ী মানুষকে কিছু না কিছু করা উচিত। বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে সূর্য সন্ধ্যার সময় অস্তাচলগামী হয় ৷ সারাদিন আলো ও তাপ বিকিরণের পর এবার তার বিদায় নেবার পালা । সমস্ত বিশ্বে আলো দেওয়া কঠিন ও দঃসাধ্য ব্যাপার—কিন্তু সূর্য সেই কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করে রাত্রে দেখতে চায় কে তার বাকি কাজ সম্পন্ন করবে অর্থাৎ রাত্রে অন্ধকার দূর করার ভার কে নেবে? কিন্তু — তা দঃসাধ্য জেনে কেউ সে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে, দেখে ছোট্ট মাটির প্রদীপ তার সীমিত সাধ্যনুযায়ী আলো বিতরণ করে কিছুটা অন্ধকার দূর করতে তৎপর হয়ে ওঠে। যদিও ছোট্ট একটা ঘরের অন্ধকারও দূর করবার ক্ষমতা হয়তো তার নেই—তবু তার আছে আন্তরিকতা —এতেই সূর্য সুখী, গর্বিত, আনন্দিত । কারণ কেউ যখন সূর্যের ডাকে সাড়া দিলনা তখন মাটির প্রদীপই গিয়ে বললো প্রভু—আমি জ্বালাবো অন্ধকারে আলো ৷ তেমনি রবীন্দ্রনাথ,বিবেকানন্দ,সুভাষের,গান্ধীর বড় বড় কাজের ভার নেওয়ার মত ক্ষমতা সাধারণ মানষের নেই—কিন্তু নিজের সাধ্যনুযায়ী তাঁদের আদর্শকে সামনে রেখে যদি কিছু কাজ করা যায় তাহলে সকলের চেষ্টায় একদিন অনেক বড় কিছু, হওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে।
নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে-
কহে, যা কিছ,সুখ সকলি ওপারে।
প্রতিটি নদীরই থাকে দুটি তীর।মাঝখানে জলধারা। দুটি তীরের আবার দুটি পার—এপার ওপার। দু পাড়ের মানষ নিজের অবস্থায় কেউই সন্তুষ্ট নয়। এপারের লোক মনে করে—ওপারের লোকগুলো কতনা সখে দিনাতিপাত, করে অন্য পক্ষে একই মানসিকতা কাজ করে—ওপারের মানুষের মধ্যে । তারা একে অপরের প্রতি স্বভাবতই ঈর্ষাকাতর। প্রত্যেক মানুষই সখে স্বাচ্ছন্দের প্রত্যাশী। জীবনের এ এক অদ্ভুত রহস্য। আমরা যে লেখাপড়া শিখি তা কেবলমাত্র অর্থকরী বিদ্যা —। যেন তেন প্রকারে ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডাক্তার কিম্বা উকিল-ব্যারিষ্টার গোছের কিছু একটা হওয়ার প্রতিযোগিতা মানুষের মধ্যে আজ প্রকট ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটাই উদ্দেশ্য অঢেল অর্থ উপার্জন— সম্পদের মিনার যেন আকাশচুম্বী হতে পারে—এমনই বিকৃত মানসিকতার শিকার আজ অনেকেই। কিন্তু এই অগাধ অর্থ-রাজপ্রাসাদের সখৈশ্বর্য বিলাসিতায়ও একদিন মানুষের একঘেয়েমিতা আসে, আসে বিরক্তি, – তখন এই সখে স্বাচ্ছন্দ যন্ত্রণা মনে হয়— ইচ্ছে হয় সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে বিবাগী হয়ে যায়। কিন্তু এ অর্থের নেশা মানুষকে তাড়া করে ফেরে—জাগিয়ে দেয়মনে হিংসা ও প্রতিযোগিতা। ডাক্তার ভাবে ইঞ্জিনিয়ার বোধহয় আমার চেয়ে বেশি অর্থবান—সুখী উকিল মনে করে—জর্জরা তাদের থেকে বেশি সুখী। কিন্তু সর্বত্যাগী, বিষয় সুখে নিরাসক্ত সাধুরা মনে করেন— ত্যাগেই সুখে, মানষকে ভালবাসাতেই আনন্দ। তাই সুখ নামের আলেয়ার পিছনে ধাওয়া করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় কি ?
পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোনো ছুতা
“জান না আমার সাথে সূর্যের শত্রুতা।”
রাতের গাঢ় কালো অন্ধকারই নিশাচর প্রাণী পেঁচার পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ সূর্যের প্রখর আলোয় সে ভালো করে দেখতে পায়না। সূর্যের উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে না পারাটা তার অপারগতা—। সেই অক্ষমতা ঢাকতে সে সেই সূর্য কে তার শত্রু, ভেবে সবার সঙ্গে সেই শত্রুতার কথা বলে নিজের হিংসুটে ও কুটিল মনের পরিচয় দেয়। কিন্তু নিজেও জানেনা তার এই অসম-দ্বন্দের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সমাজে প্যাচার মত কিছু আত্মম্ভরী লোক দেখা যায় তারা মহান উদার মানষের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দির কথা অপরকে শুনিয়ে নিজে সেই উদার মহাপরুষের সমপর্যায়ে হওয়ার চেষ্টা করে। লোকসমক্ষে এমনি করে নিজেকে জাহির করে বসে—কিন্তু সে জানেনা—যে লোকের কাছে মহাপুরুষের দোষগুণ কীর্তন করলে সে ব্যক্তির একটুও বুঝতে বাকি থাকে না যে লোকটি মিথ্যা ভাষণে নিজেকে মহাপুরুষ ব্যক্তির সমগোত্রীয় করতে চাইছে—অথবা নিজেকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চাইছে—এইভাবে তার মিথ্যে আত্মম্ভরিতার পরিমাপ করে— ক্ষুদ্রমনার এই মানুষটার অন্তঃসার শূন্যতায় সবাই আড়ালে হাসে—এবং সে তখন তাদের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে ।
এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান ।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অকাল প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশবন্ধুর মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কবিতাটি লিখেছিলেন। দু লাইন এই কবিতাটি তদানীন্তনকালে দেশে একেবারে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে কবির এই অমর যক্তিপূর্ণ’ কবিতাটি সত্যিই যথার্থ । অনাড়ম্বর এর প্রকাশরীতি। অসাধারণ তার সংহতি। যে দার্শনিক তত্ত্বটি রয়েছে কবিতায় তা সিন্ধুর মত গভীর অথচ বিস্ত্রিত। আসলে জন্ম নিলেই একদিন যে মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে জীবনে তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মরেও অনেক মানুষ অমর হয়ে থাকেন চিরকাল এই মানষেরই স্মৃতির মণিকোঠায়। শত বছরের আয়ু নিয়ে বাঁচাটাই মানুষের সার্থকতা —তাতেও অনেকে অজ্ঞাত অপরিচিত থেকে যায় মানুষের কাছে। কিন্তু স্বল্পায়ু, মানষ চিরকাল বেঁচে থাকেন তাঁর কর্ম ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। সৃষ্টিই তাকে অমরত্ব দান করে, কর্মই তাঁকে মানষের অন্তরলকে চির ভাস্বর করে রাখে—চিত্তরঞ্জন, বিবেকানন্দ তাঁর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন সোনার অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে তাঁদের নাম। শত দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েও তাঁদের সে আত্মত্যাগ ও মানবকল্যানে জীবনকে উৎসর্গ কখনো বৃথা যেতে পারে !
যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি,
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে ।
সঞ্চয় করা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। প্রথম জীবনে সবাই কিছু না কিছু সঞ্চয় করতে চায়—ভবিষ্যত জীবনটাকে নিরুপদ্রবে, একটু শান্তিতে নিঃঝামেলায় কাটানোর জন্য । কিন্তু আমাদের সেই সঞ্চিত অর্থসম্পদ কি ঠিকমত রক্ষিত হয় কিম্বা মৃত্যুর পরেও তা ঠিকমত রক্ষিত থাকে, কবির বক্তব্যনযায়ী আমরা জানতে পারছি সে সঞ্চিত অর্থ সম্পদ চিরকাল রক্ষিত থাকে না বা থাকতে পারে না। নিজের ভোগ বিলাসের জন্য যে অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করা হয় তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক —আত্মসুখের জন্য । অপরের কল্যাণে সে সঞ্চয় কোন প্রকার খরচ হয়না—এজন্য কবির বক্তব্য মৃত্যুর আগে বা পরে সে সঞ্চয় শেষ হয়ে যায়। কারণ, ব্যক্তিস্বার্থে সঞ্চয় কেউ মনে রাখে না। কারণ—স্বার্থপরতার কারণে সে সঞ্চয় কলঙ্কিত। এই মানুষই সে অর্থ গৃ মানষকে সবসময় ঘৃণার চোখে দেখে। এবং একদিন তা যথার্থ ভাবেই ফাঁকিতে পরিণত হয়। কেউ তাঁকে তাই আর মনে রাখেনা। মৃত্যুর পরপরই সে মানষের মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখতে পাই কলকাতার অনেক বিত্তবান ব্যবসায়ী জমিদার গোছের মানুষেরা নিজের সুখের জন্য প্রচুর অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন—কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় একদিন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল— কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা রামমোহনের ব্যক্তিগত সঞ্চয় কিছু অবশিষ্ট ছিল না- কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট রামমোহন কলেজ—রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিকেল, শীলদের কলেজ, হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইত্যাদি আজও স্বকীয় মহিমায় অক্ষয় অমর হয়ে মানুষের কল্যান সাধন করে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠানগগুলি বেঁচে থাকার কারণ, তাঁরা সকলের জন্য এ সঞ্চয় রেখে গিয়েছিলেন তাই আজও এগুলি সযত্নে রক্ষিত। তাঁরা কবেই চলে গেছেন পৃথিবী থেকে কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান আজো তাঁদের স্মৃতি বহন করে চলেছে ।
স্বাধীনতাহীনতায় কে ৰাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাশত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিতে চায় হে
কে পরিতে চায়?
স্বাধীনতা ও পরাধীনতা দুটি বিপরীত ভিন্নধর্মী শব্দ। দুটির অবস্থান দাই মেরুতে—অর্থও ভিন্ন ভিন্ন। স্বাধীনতা হীনতায় মানুষের বাঁচাটা মৃত্যুর সামিল । সেই পরাধীন জীবন অবশ্যি কোন মানুষেরই কাম্য নয় ।
জীবন ধারণের জন্য আলো বাতাস জল অন্ন বাসস্থানের প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। মৃত্যু পর্যন্ত এ সমস্তের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অবশ্যি এগুলো বাঁচবার তাগিদে মনুষ্যেতর প্রাণীরা ও এ কাজগুলি করে থাকে। তাহলে মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্য রইল কোথায়?
কিন্তু প্রশ্ন হোল এগুলোর চাহিদা মিটলেও বাঁচার কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়না যদি তার স্বাধীনতার অভাব দেখা দেয় ৷ স্বভাবতই মানষে চায় তার মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলির সদব্যবহার করতে। কিন্তু সেই ব্যবহার তখনই সম্ভব যখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারে। নইলে তার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক—এক বিড়ম্বিত অধ্যায়। পারিপার্শ্বিক কাউকে কোন ক্ষতিসাধন না করে নিজের কাজের মধ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে আত্মাবিস্কারে মগ্ন থাকা অধিকারের নামই স্বাধীনতা। বেঁচে থাকার আবশ্যিক উপাদন যদিও স্বাধীনতা নয় তবু এর অনুপস্থিতিও কেউ কোন মুহূর্তেই আশা করেনা।
কারণ পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে সুস্থ্য মানুষের বেঁচে থাকা বড়ই দুর্বিসহ। এই পরিবেশে কেউ থাকতে চায় না। যদি কেউ পরাধীনতার শৃঙ্কলে বাধাপড়ে কোন প্রকারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতে হয় তাহলে সে যতই চেষ্টা করে সে বন্ধন থেকে মক্তো হয়ে সুস্থ্য স্বাভাবিক স্বাধীন জীবনে ফিরে আসতে।অপরাধবোধের এই অনুপস্থিতির জন্যেই এতদিন আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেও তাদেরকে উচ্চ জাতির আসনে বসিয়ে রেখে শ্রদ্ধা জনিয়ে তোষামোদ করে চলেছি ।
সপ্তরথী মিলে কি নিষ্ঠুর ও অন্যায়ভাবে সদ্য কিশোর অভিমূন্য কে হত্যা করেছিল—তাদের কে আমরা ঘৃণার আসনে না বসিয়ে, বীর বলে আজো শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেদের পৌরষকে অমর্যদা করে চলেছি।
এসব উদাহরণ থেকে একটা কথাই স্পষ্ট হয় যে – সব সময় সর্বক্ষেত্রেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরই উচিত কর্তব্য। তাহলেই ধ্বংসের হাত থেকে সমাজ জীবনকে বাঁচানো সম্ভব। আর এভাবেই মানষের মধ্যে শুভবোধের জাগরণ ঘটবেই ঘটবে ।
অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা বড় জাতি,
সাত মহারথী শিওরে বধিয়া ফূলায়ে বেহায়া পৃতি
ন্যায় অন্যায় শব্দদুটি শুধু যে বিপরীত ধর্মী তাই নয় দুটোর অবস্থানও দই মেরুতে। ন্যায় যদি হয় মানষের শিরোভূষণ—অন্যায় তবে পদতলে ঠাঁই পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এসব শুধু কথার কথা মাত্ৰ ৷ বাস্তব বড় নির্মম । তা অন্য সাক্ষী দেয়। দেখা যায় সত্য বা ন্যায়ের মূল্য কত স্বল্প । অনাদরে তা পড়ে আছে হয়তো ঘরের এক কোণে—অথচ তারই পাশ দিয়ে অন্যায় সদর্পে বুক ফুলিয়ে হেটে যাচ্ছে।যেখানে সত্যের ও ন্যায়ের জয় হওয়া উচিত এতকাল যা হয়ে এসেছে, আজ যেখানে অধর্ম অসত্য ও অন্যায়ের সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা ।
অথচ এই অন্যায়ই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে চরম ক্ষতিকারকে, জেনেও কিন্তু মানষে সেই অন্যায়কে সাদরে বরণ করে নিতেই ব্যতিব্যস্ত। যে ব্যক্তি সংসারের অন্য সদশ্যকে বঞ্চিত করে ঠকিয়ে অন্যায় ভাবে ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে একদিন সেই বঞ্চিতরাই কিন্তু তার পদলেহনও তোষামোদ করে বেঁচে থাকে । এই ভাবে সুস্থ সমাজকে যারা অসুস্থ করে তোলে—সে সমাজ কিন্তু সংঘবন্ধ হয়ে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় না বরং উল্টে তাকে প্রশংসা ও পরষ্কৃত করা হয়। অর্থাৎ প্রকারণে তাকেই যেন সমাজের মাথা বলে শ্রদ্ধা জানানো হয় । এভাবে যে দেশ বা জাতি অন্য দেশকে স্বীকার করে নেয় তাকে বড় দেশ ও শ্রেষ্ট জাতি বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেওয়া ও তার অন্যায়কে প্রতিবাদ না করা বা কি ক্ষমাহীন মানবতাহীনতার পরিচয় তাঁর হিসেব নেই। তাই কেউ চায় না স্বেচ্ছায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে। এই পরাধীনতা শব্দ মানসিক শাস্তি বয়ে আনে না—দৈহিক নিপীড়ন ও বয়ে আনে এই পরাধীনতায় ।
তাই অর্থ সম্পদের বিনিময়ে মানুষ তার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে পরাধীনতাকে মেনে নিতে চায় না ৷
পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী।
পৃথিবীর সব কিছুই পরিবর্তন শীল। কালের অমোঘ নিয়মে সবকিছু তাই বদলে যায় ৷ একদিন মানুষ বনে জঙ্গলে গিরিকন্দরে পশউদের সঙ্গে বসবাস করতো কিন্তু সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিত্য সন্ধানী প্রবৃত্তি নব নব আবিষ্কারের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে ক্রমশঃ আলোয় উত্তরণ ঘটাচ্ছে। তাদের সেই কল্প শক্তির উজ্জল দ্যুতিতে আবিষ্কার দিন দিন হয়ে উঠছে তিলোত্তমা । আর এমনি করেই মরুপ্রায় পৃথিবীর বুকে ফলিয়েছে তারা সোনার ফসল—মাঠে প্রান্তরে গড়ে তুলেছে সভ্যতার অন্য এক সোপান — শহর বন্দর/শিক্ষা সংস্কৃতির নানা প্রকারের পীঠস্থান। মানুষের এই অবাধ গতির মূলে আছে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় জয়যাত্রা। বিজ্ঞানই আজ সম্ভব করে তুলেছে অসম্ভবকে ।
সেই কালজয়ী কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতীক বিজ্ঞানকে এক ধরণের পরশ্রীকাতর স্বার্থপর মানুষ ভুল পথে চালিত হয়ে তার অবমুল্যায়ন করে চলেছে । দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে হানাহানির বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য বিজ্ঞানকে তারা কাজে লাগিয়েছে ধ্বংসাত্মকে মারণ অস্ত্র তৈরির করে। যার ফলে দুই বিশ্ব যুদ্ধে পৃথিবীকে ঝাঝরা করে দিয়ে গেছে। নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন রেখে গেছে হিরোসিমা ও নাগাধিকার বুকে। মানবতার এমন মৃত্যুর নজির আর কি হতে পারে।এর ফলে ধ্বংস হয়েছে কত শহর গ্রাম কত মানুষ। ওইসব স্বার্থান্বেসীদের পাশব প্রবৃত্তি সুন্দর এই পৃথিবীতে এই ভাবে একের পর এক ধ্বংস যজ্ঞ রচনা করেছে। তিলোত্তমা পৃথিবীকে করে তুলেছে প্রাণ প্রতিকলে মরুক্ষেত্র ।
এতদ্সত্বেও পৃথিবী অকৃপন নয় । পরম আবেগ ও ভালবাসার সুধা রসে সিক্ত করে চলেছে মানুষকে। মূছে দিয়েছে মায়ের মত অমঙ্গলের সব চিহ্ন। অসীম যত্নে অপরিমেয়ো।
তেমনি উদার করতে পারলে। তা থেকে নিয়ত উৎসারিত হবে প্রেম ও ভালবাসা–সেই প্রেম প্রীতির দ্বারা বিশ্ব কে জয় করা অতি সহজ । তার উৎকৃষ্ট প্রমান বিবেকানন্দ,যিশু,চৈতন্যদেব,বুদ্ধ,মহাত্মা ও একালের মাদার টেরেজা।তবে একথা সত্য যে কিছু পাওয়ার আশায় মনকে উদার করা মানেই স্বার্থ পরতার লক্ষান। তাই ত্যাগ ত্যাগই। তার বিনিময়ে কিছু আশা করলে তা আর ত্যাগ থাকে না । যদিও অনেক সময় এই ভালবাসায় নিন্দা ও জোটে— যেমন বিদ্যাসাগরের জুটেছিল। সেই চিন্তা মনে রেখে মানুষকে ভালবাসার সিংহাসনে বসাব না এ হতে পারেনা।
আকাশ অত বিশাল বলেই তার থেকে নির্মল বৃষ্টি ঝরে,
তোমার অন্তরকেও উদার করে তোলো তার থেকে ভালবাসা ঝরবে ।
উদারতা সংকীর্ণতা দুটি পরষ্পর বিপরীত ধর্ম শব্দ। দুটি শব্দের অর্থ ও ভিন্ন ভিন্ন। উদারতা বলতে স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ভালবাসা মায়া মমতা স্নেহ প্রভৃতি শব্দ গুলি এগুলির সমন্বয়ে মানুষের হৃদয়কে উদার করে তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, সেই সেই গণোবলীর অধীকারীকে মহত্ব দান করে ।
অন্যদিকে যত খারাপ গুণগুলি হিংসা, লোভ, আত্মকেন্দ্রিকতা, সার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা সব মনটাকে সংকীর্ণ করে দেয় । তখন সেই সব দোষের অধীকারী মানুষকে আর আপন করতে পারেনা। বন্ধু বান্ধব এমন কি আত্মীয় স্বজন সবাইকে সে শত্রুর দৃষ্টিতে দেখে। প্রেম প্রীতি স্নেহ মায়ার মত সকুমার বৃত্তিগলি তার হৃদয় থেকে চলে যায়, সেখানে আশ্রয় নেয় হিংসা ও নিষ্ঠুরতা । তাই সে মননুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর, সমাজের ঘৃনিত ব্যক্তি ।তার হৃদয় থেকে তখন বিদায় নেয় সুখ শান্তি শ্রী। কারণ ভালবাসা যেমন মানষের ভালবাসা নিয়ে আসে তেমনি কাউকে ভাল না বাসতে পারলে কেউ তাকে শ্রদ্ধা বা ভাল বাসতে পারেনা। কারণ কিছু দিলে তবেই বিনিময়ে কিছু পাওয়া যায় ।
বিশ্ব প্রকৃতির উদারতা থেকে আমরা উদারতার শিক্ষা সহজেই নিতে পারি। অতবড় বিশাল কুলকিনারা বিহীন সমুদ্রের কাছে গিয়ে বসলে আমাদের মনকে উদাস করে দেয় । আর আকাশ। তার বিশালতা ও প্রশ্নাতীত। এই বিশালতা তো উদায়তারই নামান্তর। তারই বুকচিরে নির্মল স্নিগ্ধ বারিধারা নেমে এসে পৃথিবীর শঙ্কে কঠিন রক্ষে বৃক্ষে পতিত হয়ে পৃথিবীর প্রকৃতিকে কেমন নতুন সজীব করে তোলে । এ তার উদারতার প্রকাশ । তেমনি হৃদয়কে—পৃথিবী ক্রমশঃ এই সারাংশের অধিকাংশ মমতায় রক্ষা করে চলেছে তার ভারসাম্য। বারে বারে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসের মধ্যেও তার সৃষ্টি ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে পৃথিবী আজো পরম অমৃতময়ী অনন্ত অসীম প্রাণ সম্ভবা। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্যে তারই প্রকাশ ।
হয়তো আমার এই পথে আর হবেই নাকোত
দুই ধারে যাই রোপন করে বুকের ভালবাসা ।
পার্থিব জগতে কেউ অমর নয়। এই জীবন নশ্বর। পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে মানুষ যে সময়টুকু পায়, সেই সময়টা খুবই স্বল্প খুবই সংক্ষিপ্ত । এই সামান্যতম সময়টুকু হেলা ফেলা বা কোন ভাবেই অবহেলা ভরে নষ্ট করা উচিত নয় । কারণ সময় স্রোতের ন্যায় শুধু চলেই যায় আসেনা কখনো আর ফিরে। তাছাড়া এই মানব জীবনটা অত্যন্ত মূল্যবান ও মহৎ । অনেক পূণ্যের ফলে তবেই মানব জীবনের প্রাপ্তি ঘটে। তাই মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করাটাই মানুষের সৌভাগ্য । শুধু নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখা নিজেকে নিয়ে ভাবা এককেন্দ্রিক ও স্বার্থপরাতার জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে না। পৃথিবীতে জন্মটা মানুষের শুধু খাওয়া পরার জন্যও নয়। এই মানব জীবন দ্বিতীয়বার যে ফিরে পাওয়া যাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই । এই মানব জীবন তাই হেলাফেলা ও অবহেলার নয়। পাথিবীতে মানুষের অনেক কিছুই করার আছে। প্রত্যেকটি মানুষের কাছে অনেক কিছই আশা করে পাথিবী। সতরাং এই সংক্ষিপ্ত মানব জীবনে সাধ্যমত মহৎ কাজে লিপ্ত থেকে প্রত্যেক মানুষকে ভালবেসে নিঃস্বার্থ ভাবে তাদের মঙ্গলসাধন করাই মানষ মাত্রেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ।
ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
চায় দুটো ভাত একটু নুন
বেঁচে থাকার সমস্যাটাই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। আর এই বেঁচে থাকার খাতিরে মানষকে কতরকমই না সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার হিসেব নেই । এই বেচে থাকার সমস্যার মধ্যে দুটি সমস্যাই প্রধান, একটি বৃহত্তর বিষয় সম্বলিত—অন্যথা নিতান্তই অন্নবস্ত্র বাসস্থানের সমস্যা। সম্পূর্ণ আলাদা দুই সমস্যার চরিত্র। দুটির সমন্বয় চেষ্টা যেমন হাস্যকর তেমনিই ব্যর্থ হয় পদে পদে।
মুখে বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন— প্রবাদটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্বরাজ, স্বৈরতন্ত্রের অবসান বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব- বিশ্বশান্তি—এসব গালভরা ভাবগম্ভীর শব্দগুলো শুধুই বক্তৃতায় সম্ভব। কাজে এগুলি – বাস্তবায়িত করা খুবেই দূরূহ এবং কঠিন। অনেকের পায়ের তলায় মাটি নেই তারাও এই আদর্শে’র ধ্বজ্জা উড়িয়ে — বিলাসিতা করতে ভালবাসে । অথচ এসব কাজ যে দু একদিনে সম্ভব নয়—তা তাদের ভাবালু মনে ঠাঁই নাও পেতে পারে। তাই অনেক সময় দৈননন্দিন সমস্যার কথা তারা ভুলে বসে এবং বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যাটই এই সমস্যার শ্রেণীভুক্ত ।
অথচ এই অন্নবস্ত্রের সমাধান না করে আবেগে মানুষ বৃহত্তর সমস্যার কথা ভেবে তাদের সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে—সেদিকেই তাদের মনোযোগ। কিন্তু তারা বোঝেনা যে সমস্যাকে তারা নগন্য করে দেখছে— সেই সমস্যা না মেটা অবধি বৃহত্তর সমস্যায় মনোনিবেশ করা মানেই মূর্খামি। বেঁচে থাকতে গেলে যে অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন সেদিকে খেয়াল না করার ফলে তারা ভবিষ্যতে নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়তে বাধ্য।তাই নিজের ভীতটাই আগে শক্ত করা প্রয়োজন। তা না হলে ঘর কিছু বুঝেও না বোঝার ভান ।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে ।
প্রতি মানুষের মধ্যে যেমন বড় আমিও ছোট আমির অবস্থান, তেমনি সংসারে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কর্মের দ্বারা পরিচালিত মানুষ। বহু প্রকার কর্ম সমষ্টীতে গড়া হয় মানুষ। তার মধ্যে শুভ কর্মের দ্বারা জগতে আসে শান্তি কল্যাণ ও মঙ্গল ।আর অশুভ কর্ম— মানষকে টেনে নিয়ে যায় নরকের পথে। যে পথ বড়ই সহজ ও সোজা।কিন্তু শভকাজের পথে আছে বিস্তর অন্তরায়। নানা ধরনের বাধা বিপত্তি- অসবিধা । এককথায় সেপথ কষ্টকাকীর্ণ। সেপথে আগাতে গেলে ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উদারতায় মন পূর্ণ করে সকল মরুপ্রায় বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই বন্ধর অজানা সস্কুলে পথে পা বাড়াবার সময় মানুষ কাউকে কাউকে সঙ্গীরূপে পেতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে ।
কিন্তু বাস্তবটা বড় রূঢ়। স্বপ্ন দেখা এক জিনিষ -আর তা বাস্তবে পাওয়া আর এক। তাই সঙ্গী হিসেবে কাউকে ডাকলেই সে যে সেই ডাকে সাড়া দেবে তেমন কোন কথা নেই। মানবমুখী কল্যাণ কর্মে নানারূপ অস্তরায়ের ফলে অনেকেই পথে নেমে পিছিয়ে পড়ে। তাই বলে কল্যাণ কারো একজনের জন্য অপেক্ষা করে না। সবাই ফিরে গেলেও একজন সে কাজের ব্রতী হবেই । এটাই মানবতার ধর্ম ৷ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিদ্যাসাগর, রামমোহন, মহাত্মা-সভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দ আরো কত মহাত্মা ।
জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এঁরা মানবকল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করে মানষের অন্তরে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। এভাবে অর্জিত সাফল্যে যে আনন্দ ও তৃপ্তি তা তুলনা হীন। এই পথে কেউ সঙ্গী না হলেও সঙ্গী থাকবে মনের শুভবোধ ভালবাসার প্রেরণা ।
ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
শিশুর কাছে স্বরাজ স্বৈরতন্ত্রের সাম্প্রদায়িকতা এসব শব্দের কিন্তু কোন মূল্যে নেই ৷ তার শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য দুধ বা অন্য খাবার পেলেই সে সখী । তৃপ্ত সে। তাই মানুষ মাত্রই সর্বপ্রথম তার চাহিদা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত কোন একটা সংস্থান, ও নিরাপত্তা। তা না হলে ধ্বংসের চরম সীমায় তারা কোনদিন পোঁছে যায়—যেমন শিশুরা খাবার না পেলে মৃত্যুর দিকে পা বাড়ায় ঠিক তেমনি । তাই—বাস্তব সমস্যা সমাধান করেই বৃহত্তর সমস্যায় মনোনিবেশ করাই বোধহয় শ্রেয়। আর তবেই দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি সম্ভব।
ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।
সাধারণত এ সংসারের মানষ বড়ই অকৃতজ্ঞ ও অহংকারী। উপকারীর উপকার স্বীকার করতে মানষ ইদানীং লজ্জা বোধ করে এবং নিজেকে ছোট ভাবে- অবশ্য এর মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে সংসারে মেলেনা তেমন নয় । অনেকেই যেমন উপকারীর উপকার স্বীকার করে তার মহত্বের পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে কিন্তু অনেকে আবার সেটুকু করতেই হীনমন্যতার স্বীকার হয়। অপরের সাহায্যে
তার উন্নতি এটা ভাবতেও সে তিলে তিলে যন্ত্রণা দগ্ধ হয় । এদের বৃদ্ধি যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না তাই এরা এমন হীনমন্যতার স্বীকার। যদিও এটি এক ধরনের মানসিক বিকার গ্রস্তের লক্ষণ। অন্যদিকে অনেকে যারা বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত তাঁরা উপকারীর উপকার আনন্দে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। ক্ষুদ্রমনা মানষেরা তা তো করেই না উপরন্তু মানসিক যন্ত্রনায় চিরকাল ভোগে ৷ আর সর্বদা উপকারীর নিন্দা অপবাদ রাজ্যময় ছড়িয়ে দিয়ে একধরনের বিকৃত তৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করে নিজের অক্ষমতা ঢাকবার জন্য যতরকম মিথ্যে আছে তা দিয়ে প্রমাণ করতে চায় নিজেকে সক্ষামও স্বাবলম্বী।
ঠিক তেমনি আগে ধ্বনির সৃষ্টি। ধ্বনি থেকেই প্রতিধ্বনির উৎপত্তি। অতএব প্রক্তিধ্বনির তার অস্তিত্বের জন্য যে ধ্বনির কাছে ঋণী তা স্বীকার করতে প্রতিধ্বনির কুণ্ঠা ও লজ্জা গ্রাস করে, কারণ সে জানে যে সে ধ্বনির কাছে ঋণি—তা সত্বেও বিশ্বের কাছে নিজেকে সে ছোট করতে চায়না বলেই ধ্বনি হীন প্রতিধ্বনির অস্তিত্ব নেই জেনেও সাড়ম্বরে ঘোষনা করতে চায়—ধ্বনিকে সে চেনেই না জানেই না ধ্বনির সংগে তার কোন সংশ্রব নেই । অথচ তার এই বক্তব্য যে অন্যে উপহাস করে উড়িয়ে দেয় তা সে বোঝেনা । সে জানেনা তার এই ব্যঙ্গ করার মধ্যদিয়েই তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায় সে ধ্বনির কাছে কতটা ঋণী ।
এধরনের প্রতিধ্বনি সদৃশ মানুষের অভাব নেই সংসারে। যদিও মানুষ তাদের চিনতে ভুল করেনা ।
কারণ বিদ্যাসাগর সম্ভবত সেই মানষকে চিনতে ভুল করেননি।
“বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে”
অতি যত্নে সুনিপুন হাতে পরম পিতা পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তার প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে নিহিত আছে করুনাময়ের কোন সুগুপ্ত উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যবিহীন তিনি কিছু সৃষ্টি করেন না। তাই কোনটাই অপ্রয়োজনীয় বা খোদার ওপর খোদকারী না করে যদি প্রকৃতি ও জীবজগতের দিকে দেখার মত চোখ নিয়ে তাকাই, তাহলে বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হবেনা যে, কি সুগভীর চিন্তার ফসল এগুলি। কি অপরূপ সৌন্দর্য ধরে এরা, অসুবিধা ঘটে তখনই যখন বাহাদুরী করতে মানুষ সেগুলিকে স্থানান্তর করে নিজেদের মত করে সাজাতে চায় ৷ তখন আসল ও অকৃতিম সৌন্দর্যের ঘাটতি দেখা যায়। সেই সেই বিষয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য ও অক্ষুন্ন থাকে না ৷
ঈশ্বর বন জঙ্গল সৃষ্টি করেছেন শধুমাত্র বন্য প্রাণীর জন্য । সেখানে বন্য প্রাণীরা যে অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে চলাফেরা করে তাদের যে ভাবে বিকাশ ঘটে— গৃহে বা লোকালয়ে সেই বিকাশ কি আশা করা যায় ৷ বনের পরিবেশেই বন্য প্রাণী সুন্দর কিন্তু মানুষের তৈরি কৃত্রিম বনে বা চিড়িয়াখানায় তাদের সেই সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকেনা। তাদের দৈহিক বিকাশ ঘটেনা। বরং দিন দিন তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে । কারণ অবাধ চলাফেরা আর রুটীন হীন খাওয়ার স্বাধীনতা তাদের মানাষের সৃষ্ট বনে থাকেনা।
ঠিক তেমনি কোন মানুষকে যদি লোকালয় থেকে বনে নির্বাসিত করা হয় তাহলে সেই বন্য পরিবেশে তাকে একদিন বন্য প্রাণীর মত আচরণ করতে দেখা যাবে তেমনি ভাষা, খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা সবই বন্য প্রাণীর মত হয়ে উঠবে। সতরাং যার যেখানে মানায়, সে সেখানেই সুন্দর । অন্যথায় বিপরীত প্রচেষ্টায় দঃখের ও অসুবিধার সামিল দেওয়া ছাড়া উপায় থাকেনা ।
তাই একান্ত যেমন তাঁর মায়ের কোলেই সুন্দর বন্য প্রাণী ও তাই বন্য প্রকৃতির কোলে অপরূপ । তা না হলে সন্তান হারানো বেদনায় মা ও শিশু, যেমন বিপর্যস্ত বন্য প্রাণীহীন বনও তেমনি অসুন্দর হতে বাধ্য ৷
আমার এ ধুপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি চালে
আমার এ দীপ না জালালে
দেয় না কিছুই আলো।
দুঃখ কষ্ট ও বেদনায় জর্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত না হলে জীবনকে সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করা যায় না । বেদনার আগুণে দগ্ধ হয়েই জেগে ওঠে জীবন বোধ সুখী মানুষরা সুখ আয়েসের দোলনায় দোলন খেতে খেতে ভুলে যায় দঃখের তাপ।বুঝতে পারেনা জীবনের রুঢ় বাস্তবদিক গুলি। অন্যদিকে ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা মনে এনে দেয় এক সহজ সৃষ্টির উৎসাহ ও উদ্দীপনা। ব্যথার মূর্ছনায় মর্মরিত হয়ে ওঠে জীবনের সুপ্ত অভিব্যক্তি। অন্যদিকে বেদনার দহন থেকেই জন্ম নেয় আত্মশীক্ষা ও আত্মপ্রকাশের সামর্থ ।
ধূপকেনাপোড়ালে যেমন তার গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারেনা, মানষও তেমনি দঃখ যন্ত্রনায় দগ্ধ না হলে নিজেকে জানতে পারে না দুঃখ কি জিনিষ। তার উপলব্ধি ঘটে না ও অপরের ব্যথা, বেদনার কতটকু গভীরতা তা ও পরিমাপ করা তার দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠে না ।
না চাইতেই— সহজেই মানুষ যখন সুখেশান্তির বিলাস বৈভবে ডুবে যায় তখন চেষ্টা করে আরো কিভাবে সুখে শান্তি বিলাসের স্রোতে ভেসে ইন্দ্রের স্বর্গ রাজ্যে পৌঁছান যায়। তার জন্য অন্যায় ও অত্যাচারের পথ ও বেছে নিতে হয় তাকে সময় গতিকে—সে কখনোই চায় না সুখশান্তির কামনা থেকে মুক্তি পেতে ৷ কিন্তু একজন দখী মানুষ সব সময় চেষ্টা করে তার দঃখ যন্ত্রণার পাশ থেকে মক্ত হয়েসংস্থা জীবনে ফিরে আসতে। তার জন্য তার যে কঠোর সংগ্রাম সেই সংগ্রামই পৌঁছে দেয় তাকে জীবন সত্যের এক পরম তীর্থে ।
আবার প্রদীপের বুকে লাকিয়ে থাকে আলো, জ্বালালেই চতুর্দিকে আলোয় আলোইয় অন্ধকার দূরীভূত হয়। মানুষের মধ্যেও তেমনি লাকিয়ে থাকে এক আলোর শিখা; সেই শিখা জ্বালতে সাহায্য করে জ্ঞান অভিজ্ঞতাও বেদনা বোধ — সেই আলোকে আলোকিত হয়ে মানুষ অন্ধকার বিশ্বকে আলোকিত হতে সাহায্য করে অপরের কল্যানে নিজেকে উৎসর্গ করার প্রেরণা লাভ করে। মহাকবি বাল্মীকি যেমন ক্রোঞ্ছী ক্রোন্টীর বেদনাকে নিজের হৃদয়ে অনুভব করে মহাকাব্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন— মানষও অপরের বেদনা নিজের করে কবি ও স্রষ্টা রূপে আত্ম- প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। তার উদাহরণ শাহাজাহানের তাজমহল নির্মাণ । বেদনার অনির্বান দহনে দগ্ধ হয়ে মানুষ তাই শুভ প্রবৃত্তির প্রকাশে হয়ে ওঠে বিশ্বাত্মা ও কালজয়ী ।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার।
বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঁচতে গেলে বাহুবলের ও যে প্রয়োজন আছে তা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। লোকবল ও বাহুবল অনেক ক্ষেত্রেই মানষের অস্তিত্বকে দৃঢ় করে । অন্যায় করে বাহুবলে ও লোকবলে বলীয়ান ব্যক্তিকে কেউ ক্ষতি করতে সাহস করেনা। কিন্তু সেই বাহুবল যদি মানুষও সমাজের কল্যান ও মঙ্গলার্থে ব্যয়িত হয় তাহলে সত্যিই তা প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, গুণ্ডামীতে সেই বাহুবল কাজে লাগে তাহলে নিঃসন্দেহে সেই বাহুবল নিন্দনীয়। কিন্তু আত্মরক্ষার্থেও দেশের স্বার্থে যে বাহুবল ব্যয়িত হয় তা যেমন সমর্থিত তেমনি অনু করণীয়ও বটে ।
কিন্তু বাহুবল বলতে কি সত্যি সত্যি হাতের দৈহিক শক্তিকেই কেঝায় না অন্য কিছুও আছে । হ্যা মানসিক শক্তিও এর সঙ্গে জড়িত। শুধু বাহুবলের দ্বারা নিজেকে রক্ষা বা দেশের সেবা সম্ভব নয় যদি না সেই সঙ্গে মনের জোর থাকে । সেই মানসিক শক্তি আবার সমাজের কল্যানেই নিয়োজিত হওয়া উচিত ।
বিদ্যাসাগর অথবা রামমোহনের যে বাহুবলে বলীয়ান ছিলেন তা নয় । ছিলেন মানসিক শক্তিতে অটুট । আর সেই মানসিক শক্তিই একদিন সমাজের অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সত্যের জয়মালা ছিনিয়ে এনেছিলো। বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ নিবারণ প্রথার মত প্রথা প্রচলন করতে পেরেছিলেন। ততদিনকার কুসংস্কারে কুঠারাঘাত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।
অন্যদিকে বাঘাযতীন, ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ দেশের জন্য জীবনকে আত্মোসর্গ করে ছিলেন। বাহুবল সেখানে বড় হয়ে ওঠেনি-মানসিক শক্তিরই জয়- ঘোষিত হয়েছিল । কালে কালে যুগে যুগে এমনি করেই মানসিক ও দৈহিক শক্তি এক হয়ে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজ দেশ ও মানুষকে কল্যাণ ব্রতে দীক্ষা দিয়েছে। অথচ তাঁদের এই ত্যাগ তিতিক্ষা ও মহা আদর্শের মূল্যে কজনই বা দেয়—। অনেকেই তো সেকালে বিদ্যাসাগর বা রামমোহনকে গালমন্দ করতে পিছপা হয়নি, তাই বলে তাঁদের খ্যাতি ও আদর্শে এতটুকু কালিমা কি স্পর্শ করতে পেরেছে ।
চন্দ্ৰ কহে বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ-আলো আঁধার নিয়েই মানুষ । যদি হয় জীবনের অন্ধকার —তবে ভালোটা নিশ্চয় শুভ্র আলোকিত জ্যোৎস্না। তাই মন্দ আছে বলেই ভালোর কদর—যদি এই ভালো মন্দের প্রাচীর না থাকতো তাহলে ভাল মন্দ সুখ দঃখ আলো আঁধার, সব একাকার হয়ে যেত। কোনটার কোন একক অস্তিত্ব থাকতো না। তখন সচল জীবন হয়ে পড়তো অচল। এই মন্দকে দঃখকে পৃথিবীথেকে বিসর্জন দেওয়া যায় না—কারণ মন্দ না থাকলে ভালোর বৈশিষ্ট্য যেতো হারিয়ে। তাইতো অনন্য প্রকৃতি তার খারাপ টকু রেখে ভালো টাকু উজাড় করে দেয় মানষের কল্যা- নার্থে । যেমন শিব কণ্ঠে গরল ধারণ করে বিশ্বকে মরনের হাত থেকে বাঁচিয়ে সম্মানিত হয়েছিলেন নীলকণ্ঠরূপে।
মেঘমুক্ত নীলাকাশের চন্দ্রের সহিত নারী মুখের সৌন্দর্যের তুলনা করেন অনেক কবি । সেই নীলাকাশ ভরা তারকার মেলার মাঝে শুভ্র চাঁদকে দেখে অতিব বড় অসুখী মনেও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়, কারণ রাতের অন্ধকারে চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো সবাই উপভোগ করে আনন্দ লাভ করে। চাঁদের গাঁয়ে অনেক কলংকের দাগ আছে বটে কিন্তু, চাঁদ সে কলংকের কালি নিজের জন্য রেখে তার অমল আলো টকু ছড়িয়ে দেয় সূর্যহীন পৃথিবীতে—রাতের অন্ধকারে সামান্য তার এই কলংকের কথা কিন্তু কেউ মনে ও করেনা বা তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে না। বরং তার আলোক ধায়ায় মানুষ চোখকে ধন্য করে মনকে দিতে চায় তৃপ্তি। চাঁদ কখনোই ভুলেও তাঁর কলংকের রেখার দায় অন্যের উপর চাপায়না। তখনই তার মহত্বের পরিচয় ।
তেমনি মানষের জীবনেও এ ঘটনা সত্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। মানুষ মানুষকে কতটা দিলো, পৃথিবীকে কি দিয়ে গেল সেটাই বিচার্য। তার ব্যক্তিগত চরিত্র কি ছিল না ছিল সেটা ভাববার বা বিবেচনার বিষয় মানষের কাম্য হওয়া উচিত নয় । তার আত্ম নিবেদিত সেবার বা সৃষ্টির স্বীকৃত দান করাটাই সর্বাপেক্ষা সমীচিন। তার ব্যক্তি চরিত্রে কোথায় কোন কালিমা লেগে আছে সেটা আদৌ বিচার্য নয়, এমনই চান্দ্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীতে এখনো আছে বলেই জগৎটা এত সন্দর।
পাখীরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায়
পিপীলিকা বিধাতার কাছে পাখা চায়।
বিধাতা দিলেন পাখা, দেখতার ফল
আগুণে পুড়িয়া মরে পিপীলিকা দল।
সৃষ্টি কর্তা নিজেই শৃঙ্খলা পরায়ন। নতুবা এতবড় বিশ্ব ব্রম্ভাণ্ডকে তিনি যথাযথ রূপে সৃষ্টি করতে পারতেন না। তিনি জানেন এই বিশ্ব প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে আগেই দরকার কঠোর শৃঙ্কলার। তাই দেখাযায় কোথাও এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নেই । প্রতিটি বিষয়ই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পূর্ণ শৃঙ্খলার মধ্যে।এর মধ্যে যদি কেউ নিয়মের রাজত্বে অনিয়ম ঘটাতে চায় তাহলে তাকে পেতে হয় চরম শাস্তি। এ শুধু প্রকৃতির রাজ্যে কেন আমাদের বাস্তব জীবনেও নিয়মের বাত্যয় ঘটলেই কোন না কোন অঘটন ঘটা অবশ্বাম্ভাবী। এই নিয়ম ও শঙ্খলার ধারা চলছে অনাদিকাল থেকেই । যে যেখানে থাকার কথা যেরূপে আচরণ করার কথা যাতার করণীয়–সেই ভাবে চললেই সৃষ্টি ধারা সম্ভব এবং সেই সেই ভাবে বিশ্বে সবকিছ সন্নিবিষ্টে আছে।
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ সেই গণ্ডীথেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই কারো, কিন্তু তবু, যদি কেউ সেই গণ্ডী থেকে বাইরে যায় সেক্ষেত্রে তাকে চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। আর যদি কেউবা মুক্ত হয়ে যায় কোন প্রকারে তবে বুঝতে হবে সে দৈবক্রমে, অলৌকিক ভাবে।এই ভাবে যদি কেউ পাহাড় অতিক্রম করতে চায়—মরুভূমি ও সাগর হেঁটে পার হয়ে যেতে চায়। তবে তাকে মৃত্যুকে সঙ্গী করেই পথে বেরতে হবে। এভাবে কজনই বা সফল হতে পারে। একে অপরের ক্ষতি করার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও ক্ষতি করে কিন্তু কেউ কি হলফ করে বলতে পারে সে বিবেকের দংশন থেকে অব্যাহতি পেয়েছে ।
তেমনি পাখীরা ডানা মেলে মনের আনন্দে মক্ত বাতাসে গা এলিয়ে বিশ্ব চরাচরে উন্মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ায়—দেখে মাটীর পিপীলিকার মনে সাধ জাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সে আশার কথা বিধাতাকে বলেও ফেলে তার যদি পাখীর মত বিধাতা একজোড়া ডানা দিতো, তাহলে তারাও মনের আনন্দে পাখীর মত উড়ে বেড়াতে পারতো। বিধাতা ও সানন্দে—এক জোড়া ডানা দিলো।
যখন তার পাখা ছিলনা তখন আগুনের আকর্ষণে আকর্ষিত হলেও কাছে যেতে পারতো না। কিন্তু যখনি পাখা পেলো ওমনি আগুনের কাছে যাওয়ার ক্ষমতা হোলো। সেই ক্ষমতায় অন্যান্যকে আলিঙ্গন করতে গিয়েই পুড়ে মরলো। তাই নিয়মের রাজত্বে নিয়ম ভাঙার অপরাধে পিপীলিকার এই চরম প্রাপ্তি। তবু, আমরা অবুজ । এমনও হয় হচ্ছে। এই নিয়ম ভাঙার উদগ্র কামনায় নিয়ত আমরা জ্বলে মরছি। স্বার্থপরতা ও উচ্ছাকাক্ষা নিয়ত যোগাচ্ছে আমাদের নিয়ম ভাঙার ইন্দন । এই ইন্দনে বিশ্বের গুটাকয়েক মানুষ সাড়া দেয়নি শধু । তাই অন্তিমে রোষ থেকে কেউ আমরা বিধাতার রোষ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছিনা ।আমরা জেনে শুনেই বিষ পান করে চলেছি— অনন্ত কাল ধরে ।
“পরের বেদনা সে-ই বুঝে শুধু, যে জন ভূক্তভোগী
রোগ যন্ত্রণা সে কভু বুঝে না হয়নি যে কভূ রোগী।”
মানুষের চিরসঙ্গী তার নিত্যদিনের সঙ্গী জালা যন্ত্রণা, দঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা । অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, একজনের দুঃখ-কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণার গভীরতা অন্যে কিন্তু পরিমাপ করতে পারে না। কারণ হয়তো সকলের ব্যথা-বেদনাটা ঠিক এক ধরনের নয় সম্পূর্ণ আলাদা ভিন্ন।
আমাদের চারপাশে অসংখ্য দীন-দরিদ্র দুঃখী সর্বহারা গৃহহারা-অনাহারী মানুষ নিরস্ত্র-আশ্রয়চ্যূত মানুষ সমস্ত সুখ-সবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে হাহাকারে বুক ভরিয়ে নীরবে নিঃশব্দে মৃত্যুর পথযাত্রী হয়ে দিন গুজরান করে চলেছে। অথচ আমাদের সমাজের একশ্রেণীর বিলাসপ্রিয় মানুষ সে সব দেখেও মুখে বুজে চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে তাঁদের মানবিক অনুভূতিগুলো গলা টিপে হত্যা করে না দেখার ভান করে। ভালো মানুষ সেজে মুখে বড় বড় কথার ফুলঝুরি ঝরায়। এ ধরনের আচরণ মানবতার চরম অবমাননা তা তারা কোনদিনই উপলব্ধি করবে না ।
রাজার সঙ্গে প্রজার, ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের যে বিরোধ বা সংঘর্ষ তার ও মালে একে অপরের অবস্থান সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত অননুধাবন করার অসমর্থতা । আর এই জন্যই ইদানীং চতুর্দিকে জন্ম নিছে হিংসা প্রতিহিংসা প্রতিশোধের স্পৃহা—যা পরিণামে আমাদের সুস্থ্য সামাজিক জীবনকে করে তুলছে দুর্বিসহ ও যন্ত্রণাদায়ক ।
অথচ রাজা যদি মানবিক দৃষ্টিতে প্রজার দঃখ-কষ্টগুলো অনুধাবন করে প্রজা যদি রাজার কণ্টকাকীর্ণ জীবনধরা উপলব্ধি করে অথবা ধনী দরিদ্রের অভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয় কিম্বা মালিক শ্রমিকের কষ্টটা বুঝে তা সমাধান করার চেষ্টা করে তাহলে আবার এই পৃথিবীতে ইন্দ্রের স্বর্গ নেমে আসতে বাধ্য।
এইভাবেই দেখা যায় অন্যের বেদনা শুধু সেই বঝতে পারে যে সেই বেদনার সামিল হয়েছে। একজন রোগী বোঝে আর এক রোগীর রোগ যন্ত্রণা ৷ যেমন—
চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদনা বুঝিতে পারে,
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ।
তাই ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন রচনা করা তখনই সম্ভব যখন হৃদয় বৃত্তির জাগরণ হবে অতএব সেই হৃদয়েরই অনশীলন করা মানুষ হিসাবে আমাদের একান্ত কর্তব্য ।
এই বিশ্বে যাঁরা মানব হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসনলাভ করে অমর ও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তারা ধর্ম গর্বে গর্ব নন—নন মানব বিদ্বেষী তাঁরা সবাই প্রেমের পূজারী। তাই প্রেমের দ্বারা শধুমাত্র বিশ্বকে জয় করা সম্ভব আর বিশ্ব জয় করা মানে মানুষের হৃদয়কে জয় করা যা যুদ্ধে জয় করা সম্ভব নয় সম্ভব নয় অর্থে সম্পদে, সম্ভব শুধু প্রাণঢালা নিঃস্বার্থ ভালবাসায় ।
প্রীতি প্রেমের পুন্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুড়ে ঘরে ।
বিশ্বের শান্তিকামী সকল মানুষেরই একান্ত কাম্য ; হৃদয়ের একটি স্বতঃসারিত সুর তা হোল, যদ্ধ নয় : শান্তি চাই । দ্বন্দ্ব নয় সমগ্র বিশ্বে কল্যাণ, মঙ্গল ও পরম প্রশান্তি বিরাজমান হউক। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, সেই মঙ্গল ও শান্তি অধরা রয়ে গেছে আজো, অথচ পৃথিবীতে এই শান্তি আনার জন্যে শহরে নগরে গ্রাম গঞ্জে প্রান্তরে বিদগ্ধ জনেরা কত না সভা, মিছিল পথ পরিক্রমা নতুন নতুন পথের সন্ধান সৃষ্টি করে চলেছে তার ইয়ত্বা নেই । এতদ্ সত্ত্বে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে হিংসা যুদ্ধভীতি হানাহানি চলেছে সমান তালে। হিংসার অশান্ত তাণ্ডবে অকারণে ভাঙছে ঘর, অকালে ঝরে যাচ্ছে কত তাজা প্রাণ তার কোন হিসেব নেই ৷ অথচ ভাবলে বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে না, যে শান্তির জন্য এত প্রচেষ্টা সেই শান্তির বীজমন্ত্র লুকায়িত আছে আমাদেরই হৃদয় নিঃসারিত প্রেম প্রীতি ও সঞ্জীবনী সুধায় ।
তবু আমরা নিরূপায় । হয়তবা ইচ্ছাকৃত ভাবেই আমাদের সেই হৃদয় নামক বস্তুটিকে জাগরিত করবার চেষ্টা করি না। সেই হৃদয়ের এক কোণে মরিচা ধরে গেছে প্রেম প্রীতির ৷ অথচ কি মহিমা এই প্রেম প্রীতির। সমস্ত বিশ্বে যার দ্বারা উদ্ভাসিত করে এক অখণ্ড শান্তির বাণী পৌঁছে দেওয়া যায় আব্রাহাম লিঙ্কন, শ্রীরামকৃষ্ণ, মাদার টেরেজা যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ—ভালবাসার আহ্বানে সাড়া দেয়না এমন মানুষ কি সংসারে আছে!
যে প্রেম প্রীতি ভালবাসা অর্জন করতে পয়সা কড়ির ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয় না, হয়না কোন কায়িক শ্রমের যা জন্ম থেকেই হৃদয়ের ধন সেই ভালবাসা অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ায় কি কার্পণ্যতা! যা দান করলে কমে না বরং বেড়েই চলে—তা আমরা কেমন বন্দী করে রেখে আমাদের সংকীর্ণতাকে কেমন নির্লজ্জ, নির্মম ও উলঙ্গভাবে প্রকাশ করি, আমাদেরই জৈবিক হিংসা ও স্বার্থপরতায় মানষকে ঠকিয়ে রূঢ় ভাষা ব্যবহার করে। অথচ ভাবলে অবাক হতে হয় ।
সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই
যে যুদ্ধে ভাইকে মাৱে ভাই ।
সারা পৃথিবী জুড়ে যে একটি সর্ব শ্রেষ্ঠ জাতির অবস্থিতি সে জাতির নাম মানব জাতি। জ্ঞানে গুণে বিদ্যা বুদ্ধি ও মানসিক বিকাশে সকল প্রাণীর চেয়ে মানষই শ্রেষ্ঠ। তাই মানষ সমাজবদ্ধ হয়ে একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃ প্রতিম সম্পর্ক’ নিয়ে বসবাস করে। মানুষের মধ্যেকার কদাকার সংকীর্ণতা মাঝে মধ্যে এই সম্পর্ক কে কলুষিত করে তোলে। তখন মূর্খের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক বিরোধের বাতাবরণ । আমাদের সাধারণ মানুষই তাদের শ্রমদ্বারা এই পৃথিবীকে সৃষ্টিশীল করে তোলে । তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বার্থের কোন সংঘাত সৃষ্টি হয় না । শুধুমাত্র স্বার্থন্বেষী মানুষ নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছায় ভেদ সৃষ্টি করে লাভবান হতে চায়। ভাষা-ধর্ম রাজনীতি দেশজয়ের সংকীর্ণতায় শাসক শ্রেণী যুদ্ধ বাধায় অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে এবং সেই যুদ্ধের যাবতীয় ভার চাপিয়ে দেয় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ওপর। শান্তিকামী মানুষ তখন অশান্তির আগুনে পড়ে ঝলসে যায় ৷ এইভাবে মানুষের মধ্যে শাসকশ্রেণী যুদ্ধের ভাবাবেগ সৃষ্টি করে । তখন এই মানষই অন্য মানুষের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে দ্বিধা করে না। শুরু হয় হিংসা হানাহানির তাণ্ডব নৃত্যে। এইভাবে মানুষের মথ্যে যে সুন্দরতম ও মহত্তম হৃদয় আছে সেটা বিধ্বস্ত হয়। মনুষত্ব বিনষ্ট হয়। মানুষ মানুষকে তখন আর ভাই বলে ভাবতে পারেনা। তখন সবাই শত্রু হয়ে ওঠে ।
অথচ এই মাননুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বাসস্থান। তাই মানষকে অস্ত্রাঘাত করা মানেই ঈশ্বরকে অস্ত্রাঘাত করা। মানুষকে হিংসা ও অবহেলা করে দূরে সরিয়ে দেওয়া মানেই ঈশ্বরকে অবমাননা করা ৷
সাম্রাজ্যলোভী নিষ্ঠুর শাসকশ্রেণী এইভাবে সাধারণ মানুষকে দিয়ে যুদ্ধের ভাবাবেগ সৃষ্টি করে একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে যে যুদ্ধে ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে। মনুষ্যত্ব বিসর্জিত এই যুদ্ধ ঈশ্বরের অনুশাসনকেই আঘাত করে ।
পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়;
পথের দু’ধারে আছে মোর দেবালয়।
পরম পিতা ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। পৃথিবীর সবকিছুর নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক তিনিই স্বয়ং। তাই তার একটু করুণা ও কৃপা লাভের আশায় মানষে পথ প্রান্তে এখানে সেখানে গড়ে তোলে দেবতার মন্দির। আর দেবতার মন্দির গড়ার জন্য দেবতাকে বড় করার জন্য পারিপার্শ্বিক জড় জগৎকে তারা অস্বীকার করে। ছুটে যায় তীর্থ পরিক্রমায় দেশে বিদেশে। ভীড় করে পূজো দেয় মন্দির মসজিদ গীর্জায়। এসব করতে গিয়ে তারা ভাববার অবকাশ পায়না যে, এই মানুষকে অস্বীকার করে মাটির পাতলকে দেবতার আসনে বসানো এক ধরনের ভণ্ডামী ও কুসংস্কারচ্ছন্ন ছাড়া কিছুই নয় । কারণ সর্বজীবেই ঈশ্বরের অবস্থান । প্রত্যেক মানুষের হৃদয় মন্দিরেই তাঁর অবস্থান। সেই মানুষের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় ঈশ্বরের ভালমন্দ ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা। সেই মানষের,পী ঈশ্বরের সেবা ভালবাসা ও কল্যাণের মধ্য দিয়েই তো ঈশ্বরকে সেবা করা যায়, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করার পথ সংগম হয়ে ওঠে। আসা যায় ঈশ্বরের কাছাকাছি। তা নইলে এই মানব জীবনই বৃথা হয়ে যায় ৷
তবু আমরা ছুটে যাই তীর্থে তীর্থে। খুঁজে বেড়াই হন্যে হয়ে দেবতাকে । মানষের ধারণা পবিত্রতম স্থানেই তাঁর বাস তাই গড়ে উঠেছে লোকালয় থেকে অনেকদরে পাহাড় পর্বতের গুহায় তাঁর তীর্থক্ষেত্রে।পূর্ণ লোভাতুর মানুষ তাই অনন্তকাল ধরে ছুটে চলেছে সেই তীর্থের পথে । এখানেই তার কুসংস্কারচ্ছন্নতা। আসলে ঈশ্বরকে পেতে হলে অর্থ ব্যয়, কায়িক শ্রম বা তীর্থে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না—মানষকে ভালবেসে ঘরে বসেই তার কাছাকাছি থাকা সম্ভব ।
প্রকৃতির এই যে অনন্ত অসীম সৌন্দর্য এরই মধ্যে তার প্রকাশ তার লীলা তেমনি মানুষের মধ্য দিয়ে মানষের আদর্শ ও ভাল কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ । একথা মানতে চাইনা বলেই- গড়ে তুলি বিপুল অর্থ ব্যয়ে দেবমন্দির। তার অসীম করুণা প্রতি নিয়তই ঝরে পড়ছে—যেখানে সেখানে তাই তিনি যেমন সত্য এই বিশ্ব প্রকৃতি ও তাঁরই পায়ের চিহ্ন আঁকা ধূলি ধূসরিত পথ ও পবিত্র । সর্বত্র তিনি আমাদের চারপাশে বিরাজ করে প্রেম প্রীতি চেয়ে চলেছেন ।
BhabSomprosaron-bhabsomprosaron-Vab Somprosaron-bhabsomprosaron-Vab Somprosaron-bhabsomprosaronVab Somprosaron-bhabsomprosaron-Vab Somprosaron