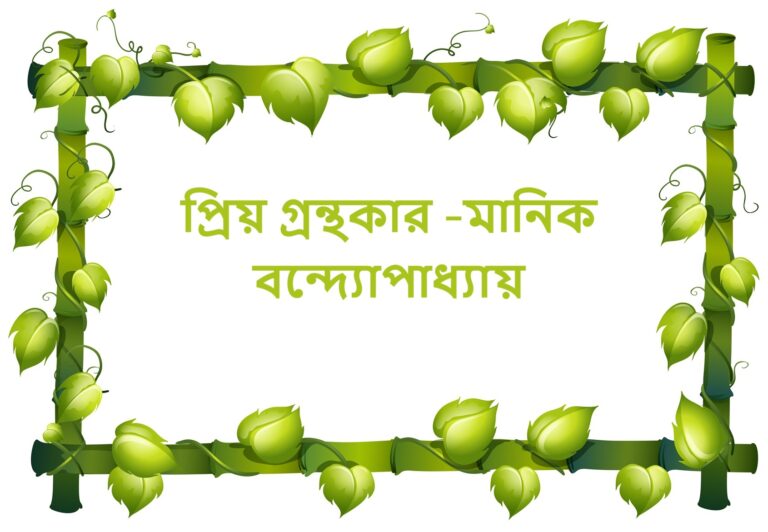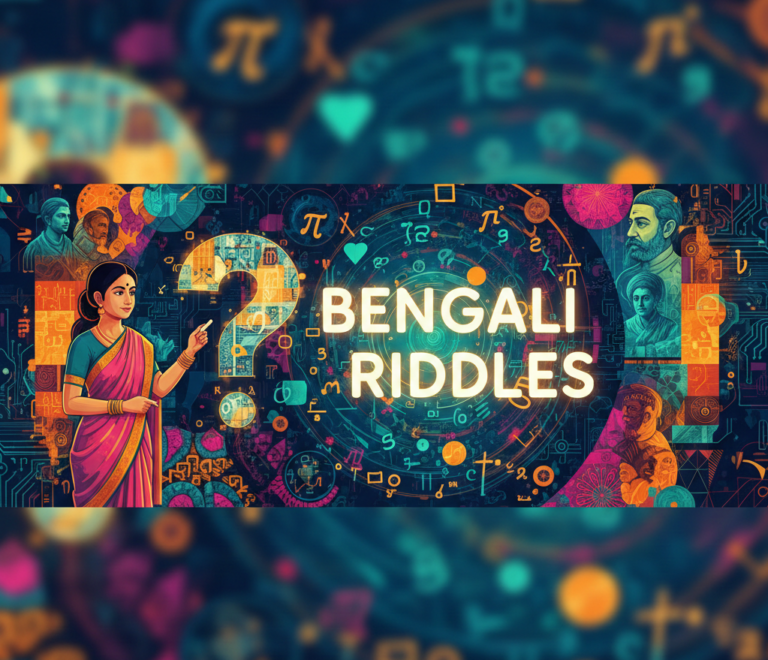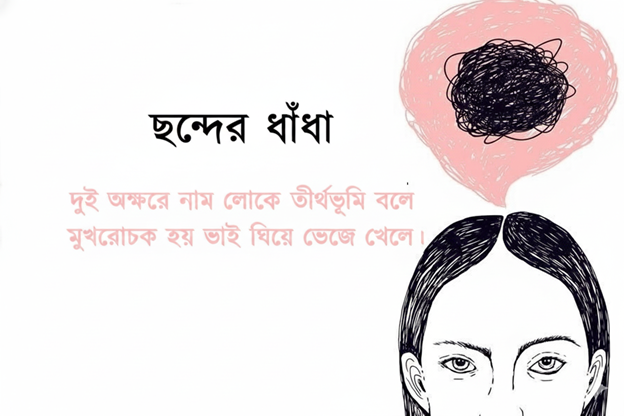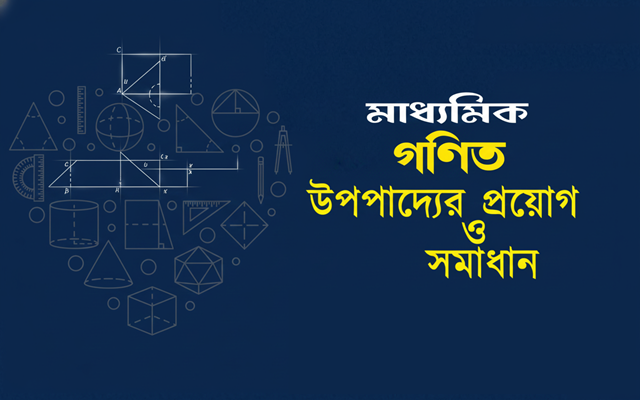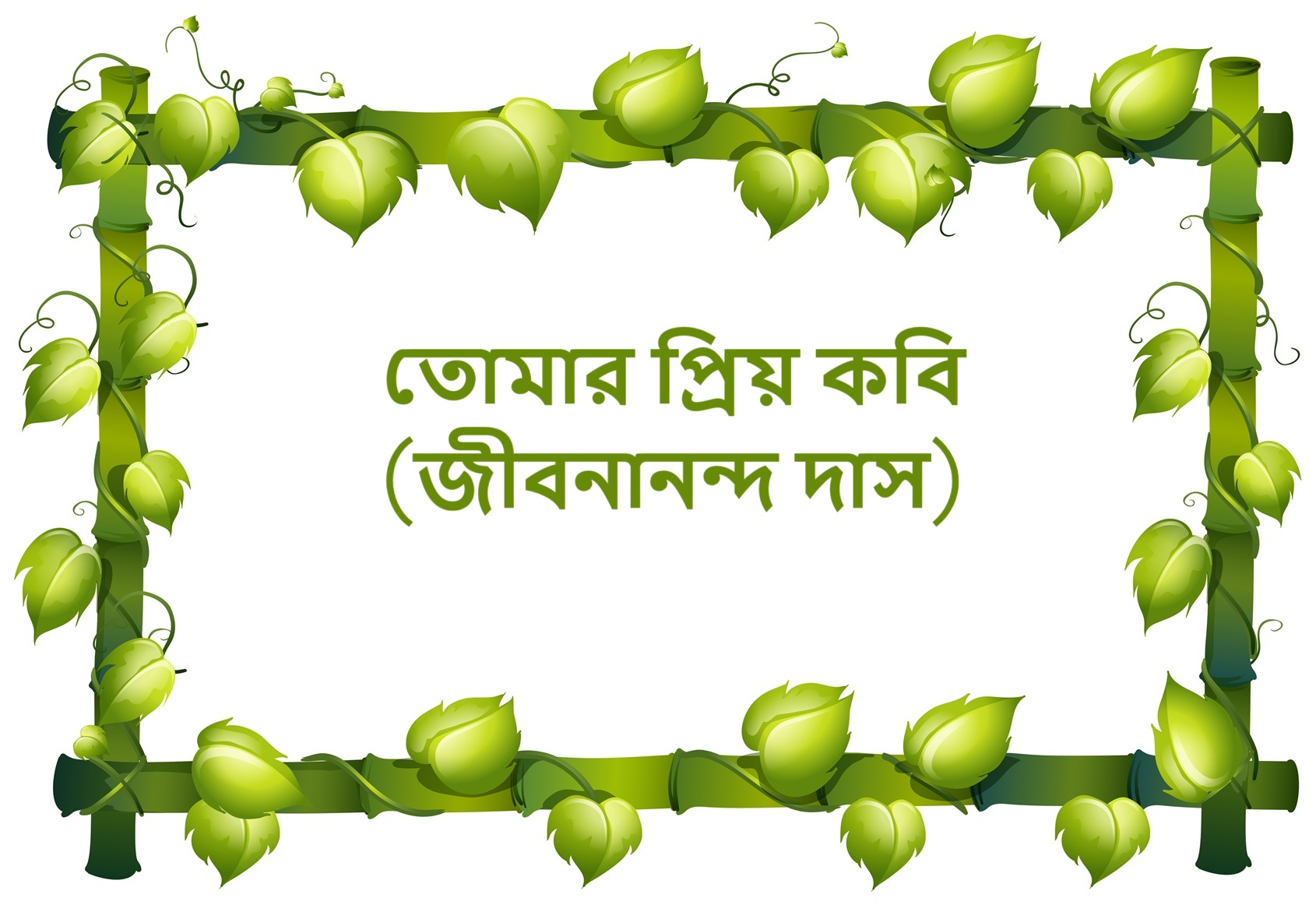
Tomar priya kabi (Jibanananda das)
তোমার প্রিয় কবি (জীবনানন্দ দাস )
Tomar priya kabi (Jibanananda das)
[ ভূমিকা – জন্ম ও বাল্যকাল – শিক্ষা ও বাল্যজীবন—কাব্যরচনা—মৃত্যু— সমাজের উপর রচনা প্রভাব — রচনার বৈশিষ্ট্য, কাব্যজগতে কবির স্থান– উপসংহার ]
ভূমিকাঃ বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য অনুসারে বলা যায় রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা একদিক থেকে শহীদ হয়েছেন ; কেননা তাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ছিল রবীন্দ্র–অনুকরণ কিন্তু অসম্ভব ছিল রবীন্দ্র–অনুসরণ। রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ যাঁরা করলেন তাঁরা দিনের তারার মতো গেলেন মিলিয়ে । বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সার্থক কবিতা রচনা করলেন, কাব্যকার হিসাবে তাঁরা সার্থক হয়ে উঠতে পারলেন না। এরই পরে কেউ –কেউ এলেন রবীন্দ্র–বিরোধী ভাবধারা নিয়ে। আবার কেউবা এলেন প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্র বিরোধী হয়ে। জীবনানন্দ এদের কোন দলের দলী নন । আপন মনের জগতে সৃষ্টি করলেন এক স্বতন্ত্র কাব্য লোক–নতুন কাব্য লোক। যা কিছু দেখেছেন তাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে হাজির করেছেন কাব্য–রসিকের দরজায় । চিত্রাঙ্কনে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি নিজেকে । দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে নিজেকে দিয়েছেন ছড়িয়ে । বাস্তব মনের অভাবনীয় প্রকাশ তাঁর কাব্য। তাই রবীন্দ্রোত্তর যুগের অনন্য– সাধারণ কবি জীবনানন্দ। রবীন্দ্র–বিরোধী না হয়ে, আবার রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ না করেও জীবনানন্দ আপন সৃষ্টির স্বাতন্ত্রে স্বতন্ত্র। তাই আমার কাব্যানুভুতির জগতে আসা–যাওয়ার পথে তাঁর নিত্য আনা–গোনা ।
জন্ম ও বাল্যকালঃ রূপসী বাংলার কবি রূপসী বাংলার বুকে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ সালে ( ৬ই ফাল্গুন, ১৩০৫ ) পূর্বে বঙ্গের বরিশাল শহরে। বাবা সত্যানন্দ দাস, মা কুসুম কুমারী দাস। বাবা কম বয়সে স্কুলে ভর্তি‘র বিরোধী ছিলেন, তাই মায়ের কাছে বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত। সকালে বাবার উপনিষদ আবৃত্তি আর মায়ের গান ছিল তাঁর প্রতিদিনের আকর্ষণ ।
শিক্ষা ও বাল্যজীবনঃ প্রথমে বরিশালে ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজে শিক্ষা শেষ করে এলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন । অধ্যাপনায় জীবন আরম্ভ আর অধ্যাপনায় জীবন শেষ ।
কাব্যরচনাঃ প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরাপালক‘!তারপর ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি‘, ‘বনলতা সেন, ‘মহাপৃথিবী‘, ‘সাতটি তারার তিমির‘, ‘জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা‘, ‘রূপসী বাংলা‘, বেলা–অবেলা কালবেলা‘,—তাঁর কাব্য জগতকে করেছে সমৃদ্ধ ।
মৃত্যুঃ ১৯৫৪ সালের ১৪ই অক্টোবর ট্রাম দুর্ঘটনায় কবি আহত হন । ২২শে অক্টোবর রাত্রি ১১ টা ৩৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু ঘটে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে । বাংলা কাব্য–জগৎ বোধ হয় আরও অনেক পাওয়া থেকে হ‘ল বঞ্চিত।
সমাজের উপর রচনার প্রভাবঃ কবি বা শিল্পী–সাহিত্যিক সমাজ সংস্কারক নন, তাই সমাজের উপর তাঁর কোন প্রভাব ছিল না। বরং সমাজের বা যাগের প্রভাব ছিল জীবনানন্দের মধ্যে ।
রচনার বৈশিষ্ট্য ও কাব্য জগতে কবির স্থানঃ জীবনানন্দের ‘ঝরা পালকের’ ‘পিরামিড‘ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, নজরুল প্রভৃতি কবিদের প্রভাব থাকলেও ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি‘ তাঁর নিজস্ব গড়া জগৎ ;—আধূনিক জীবন যেমন দোদুল্যমান, সংশয়াচ্ছন্ন, তার সার্থক প্রতিফলন । জীবনানন্দ রবীন্দ্র–পরবর্তী প্রথম আধনিক কবি। রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন সেনগত, নজরুল— এদের কাব্যে যেমন পরিচ্ছন্ন বিবর্তন, জীবনানন্দে তার পরিবর্তে আছে দোদুল্যমানতা । ‘পিরামিড‘ এ বলেছেন, “কার লাগি, হে সমাধি, তুমি একা বসে আছ আজ”। তারপরই বোধ কবিতায় বল্লেন, “স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়– ভালবাসা নয় /হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জনম লয়”, পৃথিবীর জ্বালা–যন্ত্রণা থেকে সরে এসে স্বপ্নের হাতে নিজেকে ধরা দিতে চেয়েছেন। আবার পূর্বে জন্মের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন— “আবার আসিব ফিরে” “বনলতা সেন”, “সুচেতনা” কবিতায় । “বোধ যাকে নিরাসক্ত করে তুলেছিল, তিনিই বলে উঠলেন, “আমারে দু–দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন”। এই জীবন জটিলতাই কবিকে আধুনিকতা এবং অনন্য–সাধারণতায় উন্নীত করেছে । কাব্যে এক মায়াময়, মোহময়, জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আবার মনের অবচেতনা স্তরে ক্রিয়া–প্রক্রিয়াকে যেভাবে উচ্চকিত করেছেন তা আধুনিকতারই দান ৷
সমস্ত জীবনকে প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ এবং প্রকাশ যে কবি করেন, তিনি প্রকৃতির কবি। প্রকৃতি তাঁর কাছে জড় পদার্থ নয়।—প্রাণ স্পন্দনে স্পন্দিত ।
ইতিহাস, ভূগোল ও তাঁর কাব্যে বিরাট অংশ জুড়ে আছে। ‘বনলতা সেন‘, ‘সুচেতনা‘ প্রভৃতি কবিতায় ইতিহাস, ভূগোল স্পষ্টরেখায় অঙ্কিত । এগুলিপড়ে রবীন্দ্রনাথের ‘কল্পনা‘ কাব্যের কথা মনে পড়লেও চিনতে কষ্ট হয় না জীবনানন্দের স্বতন্ত্র জগৎকে । ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর, ভারত মহাসাগর, ব্যাবিলন, পারস্যকে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, তা তাঁর নতুন সৃষ্টি। আমাদের পিতা বৃদ্ধ কনফুশিয়াসের মতো আমাদের প্রাণ।”
ভাষা শব্দচয়ন, উপমা–সর্বত্রেই তাঁর বিশেষ স্বাতন্ত্র। ‘রমনী‘ ‘নারী‘ না বলে, বলেছেন ‘মেয়েমানুষ‘ বা ‘মানষী‘। আবার ‘দেহ‘ ‘তনলতা‘ ‘দেহবল্লবী‘ না বলে, বলেছেন ‘শরীর‘ । এ–যেন তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার। অনেক অ–কাব্যিক শব্দ তাঁর কবিতায় এনেছে নতুন ব্যঞ্জনা ।— ‘জ্যান্ত‘, ‘ছুঁড়ি‘, ‘নাকের ডাসা‘ ‘বাঁদা’, সরপুটি’, পাখীর ডিমের খোলা‘—তার অপূর্ব‘ প্রয়োগ–ফসল । অশালীন শব্দও তাঁর কাব্যে এক অভাবনীয় রূপ লাভ করেছে।
কবিতায় পয়ার বা অসমমাত্রার বা যাকে বলে ‘বলাকার ছন্দ‘ যা মুক্ত রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে অনন্যবাহক ৷ এর ছন্দ মন্থর ; যেন ইচ্ছে করে ভাঙ্গা–ভাঙ্গা, অসমান, বাঁকানো–চোরানো।—“আমাদের রক্তের ভিতরে / খেলা করে / আমাদের ক্লান্ত করে / ক্লান্ত– ক্লান্ত করে ।–”
চিত্র কল্প রচনায় জীবনানন্দের জুড়ি মেলা ভার। প্রথম–স্তরের কাব্যে নিঃসর্গের আধিপত্য/প্রকৃতির বিষণ্নতা তাঁর শব্দ চয়নে — “বেলা বয়ে যায়, গোধূলির মেঘ সীমানায়/ধুম্র মৌন সাঁঝে/নিত্য নব দিবসের মৃত্যু ঘন্টা বাজে,”-। প্রকৃতি বর্ণনায় দেশ কালে একাকার । আকাশ তাই বর্ণিত হয়েছে—“জ্যোস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের উপর চিতার উজ্জ্বল চামডার / শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ।”
হেমন্তকাল, হিজলগাছ, ধূসরবর্ণ‘—প্রভৃতির প্রতি কবির বিশেষ মন কাজ করত ৷
অনেকের মতে জীবনানন্দ নির্জনতার কবি—নির্জনতা তিনি ভালবাসতেন । কবিতার নামকরণের মধ্যে নির্জনতা এসেছে বার বার। কবিতার ভাবের মধ্যেও এই নির্জনতার দ্যোতনা।
উপসংহারঃ জীবনানন্দ তাই রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। অশান্তয়ুগের এক স্বতন্ত্র কাব্যকার। অশান্তয়ুগের এক স্বতন্ত্র কবি। তাঁর কাব্যের দোদুল্যমানতা, চিত্রকল্প, শব্দচয়ন, ছন্দ – আমাকে দোলা দেয় বার বার । কোথায় যেন আমার মাঝে কি এক বোধ‘ কাজ করে।