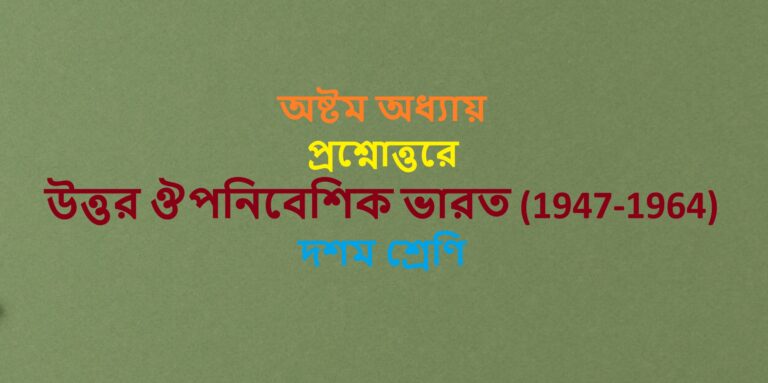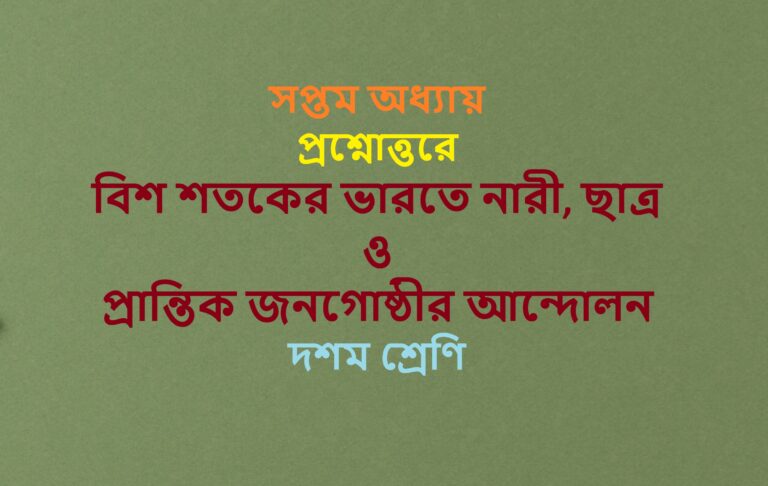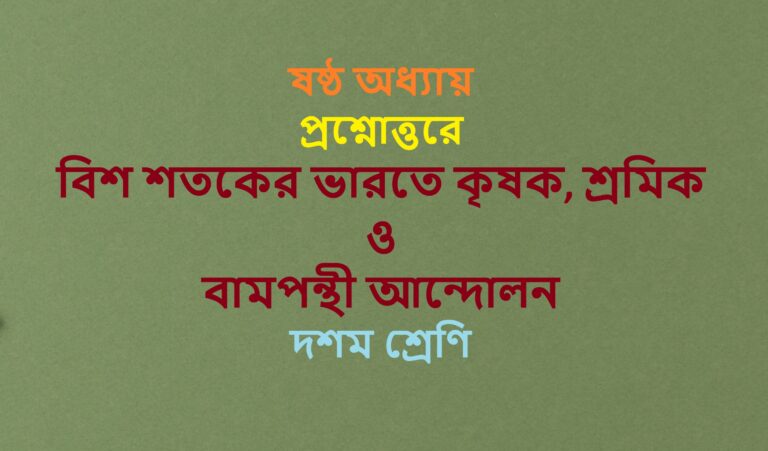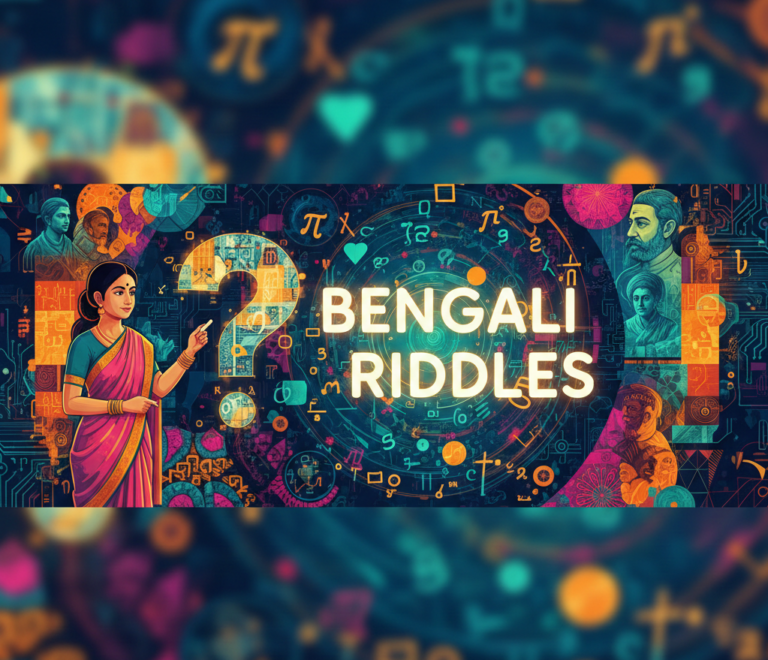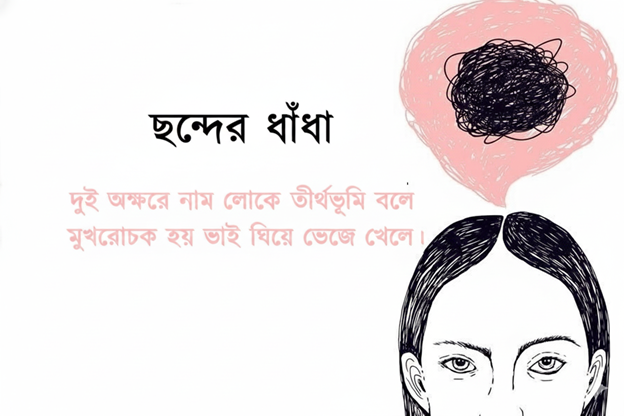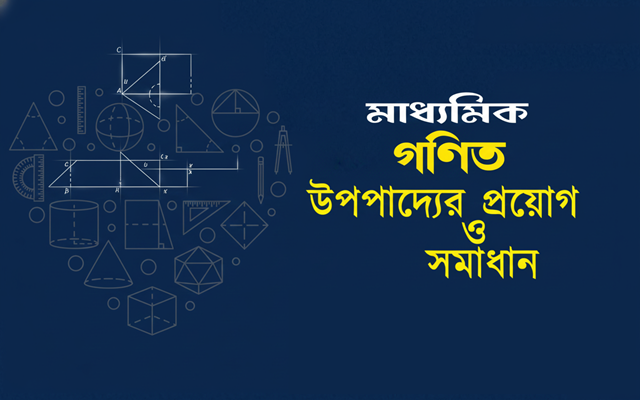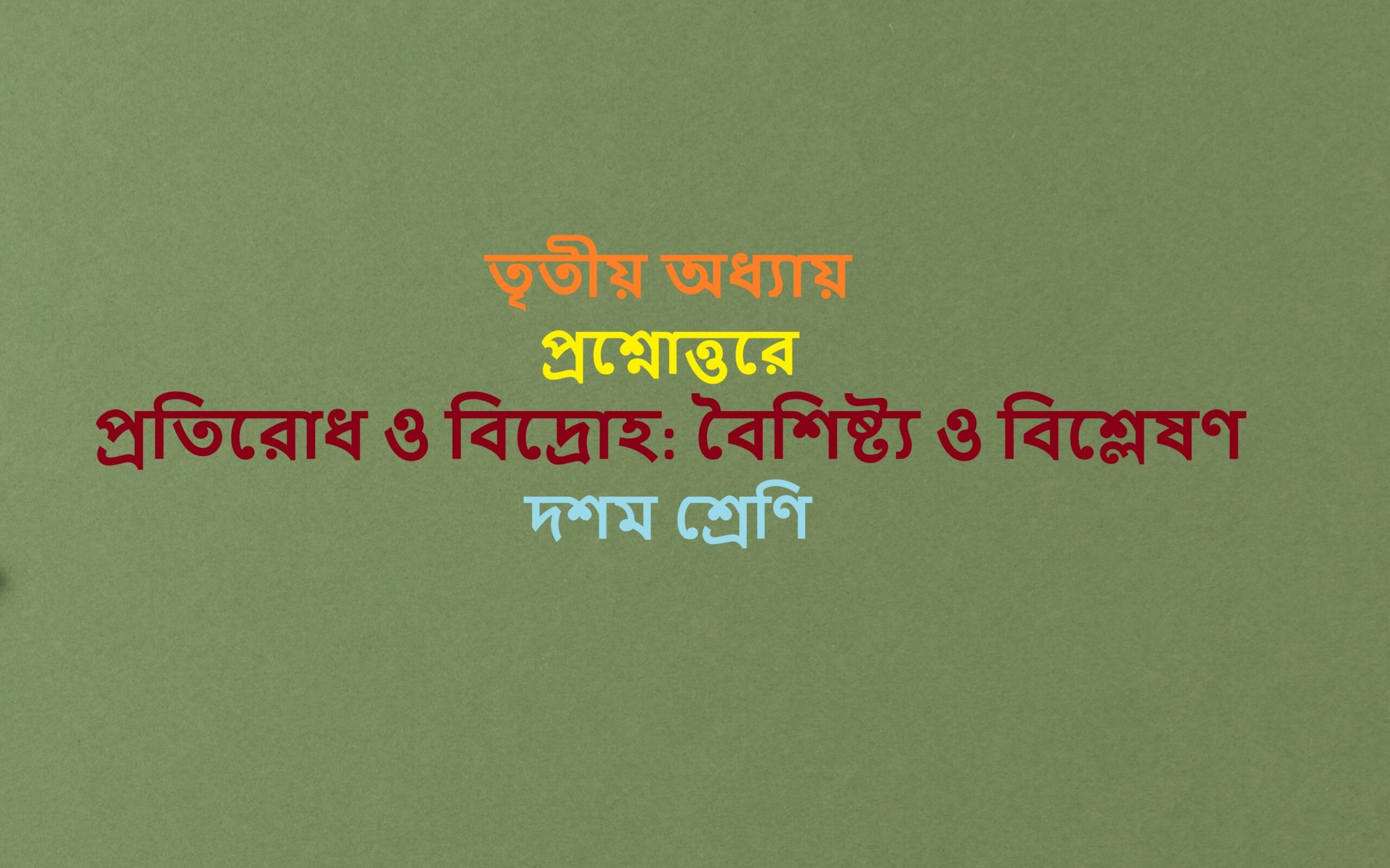
Pratirodh-o-bidroha-Baisistya-o-bislesan
প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ
pratirodh-o-bidroha-baisistya-o-bislesan
অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
উলগুলান বলতে কী বোঝো?
উত্তর উলগুলান বলতে বোঝায় বিরাট তোলপাড় হওয়াকে।
কত সালে নীল কমিশন গঠিত হয় ?
উত্তর 1860 সালে নীল কমিশন গঠিত হয়।
1878 খ্রিস্টাব্দের অরণ্য আইনে অরণ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
উত্তর তিন ভাগে।
ওয়াহাবি কথার অর্থ কী ?
উত্তর নবজাগরণ।
নীল বিদ্রোহের সমর্থনে কোন পত্রিকা দাঁড়িয়েছিল ?
উত্তর হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা।
বাঁশের কেল্লা কে বানিয়েছিলেন?
উত্তর মির নিশার আলি (তিতুমির) ।
কোন সময়কালকে চুয়াড় বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্ব বলা হয় ?
উত্তর 1798-99 খ্রিস্টাব্দকে।
কখন ব্রিটিশ সরকার ‘বনবিভাগ‘ গঠন করে ?
উত্তর 1864 খ্রিস্টাব্দে।
কাকে মেদিনীপুরের লক্ষ্মীবাই বলা হয় ?
উত্তর রানি শিরোমণিকে।
চাইবাসার যুদ্ধ কবে হয়েছিল ?
উত্তর 1820-21 –খ্রিস্টাব্দে।
‘দামিন–ই–কোহ্‘ কথাটির অর্থ কী ?
উত্তর পাহাড়ের প্রান্তদেশ।
‘দিকু‘ কথার অর্থ কী ?
উত্তর বহিরাগত জমিদার ও মহাজনদের দিকু বলা হতো।
কে নিজেকে ‘ধরতি আবা’ বা ‘পৃথিবীর পিতা‘ বলে ঘোষণা করেন?
উত্তর বীরসা মুন্ডা ।
খুৎকাঠিপ্রথা কী ?
উত্তর কৃষিজমিতে মুন্ডাদের যৌথ মালিকানাকে বলা হতো খুৎকাঠি প্রথা ।
কত খ্রিস্টাব্দে ছোটোনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয় ?
উত্তর 1908 খ্রিস্টাব্দে।
ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম কৃষক বিদ্রোহের নাম কী ?
উত্তর সন্ন্যাসী–ফকির বিদ্রোহ।
কোন উপন্যাস থেকে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কথা জানা যায় ?
উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাস থেকে।
কোথায় প্রথম সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ?
উত্তর ঢাকায়।
‘দার–উল–হারব‘ কথাটির অর্থ কী ?
উত্তর শত্রুর দেশ/বিধর্মীদের দেশ।
‘দার–উল–ইসলাম‘ কথাটির অর্থ কী ?
উত্তর ইসলামের দেশ বা ধর্মরাজ্য।
তিতুমিরের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি কে ছিলেন ?
উত্তর মৈনুদ্দিন ও গোলাম মাসুম।
‘ফরাজি‘ কথার অর্থ কী ?
উত্তর ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য ।
দুদু মিঞার আসল নাম কী ?
উত্তর মহম্মদ মহসিন ।
কার সময়ে ফরাজি আন্দোলন সর্বাধিক জনপ্রিয় হয় ?
উত্তর দুদু মিঞার সময়ে।
‘তরিকা–ই–মহম্মদিয়া‘ কথাটির অর্থ কী ?
উত্তর মহম্মদ প্রদর্শিত পথ।
পাগলপন্থী কাদের বলা হতো ?
উত্তর ফকির করমশাহের অনুগামীদের পাগলপন্থী বলা হতো।
নীলচাষ বিষয়ক পঞ্চম ও সপ্তম আইন কবে পাশ হয় ?
উত্তর 1830 খ্রিস্টাব্দে।
কত খ্রিস্টাব্দে ‘নীলচুক্তি আইন‘ রদ করা হয় ?
উত্তর 1868 খ্রিস্টাব্দে।
নীল বিদ্রোহের অবসান কবে হয়েছিল ?
উত্তর 1863 খ্রিস্টাব্দে।
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
ফরাজি আন্দোলন কি ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলন ?
উত্তরঃ বাংলায় সংগঠিত আন্দোলনগুলির মধ্যে ফরাজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনের রূপলাভ করে। হাজি শরিয়তউল্লাহ ফরিদপুর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে সংগঠিত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করে তোলাই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য।
নীলকররা নীলচাষিদের ওপর কীভাবে অত্যাচার করত তা সংক্ষপে আলোচনা করো।
উত্তরঃ নীলচাষে বাধ্য করার জন্য বা উপযুক্ত পরিমাণে নীল আদায়ের জন্য নীলকর সাহেবরা দরিদ্র নীলচাষিদের নীলকুঠিতে আটকে রেখে চাবুক মারত, এমনকী হত্যা করত। নীলকর সাহেবরা নীলচাষিদের গোরুবাছুর লুঠ করত এবং অগ্নিসংযোগ, গৃহে ডাকাতিও করত। এমনকী চাষিদের স্ত্রী–কন্যাকে অপহরণ করে লাঞ্ছিত করতেও নীলকর সাহেবরা পিছপা হতো না ৷
দুদু মিঞা স্মরণীয় কেন ?
উত্তরঃ বাংলায় ফরাজি আন্দোলনের প্রবর্তক হাজি শরিয়তউল্লাহ–এর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহম্মদ মহসিন বা দুদু মিঞা ফরাজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফরাজি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, দক্ষ সংগঠক ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন ধর্মীয়–সামাজিক আন্দোলন থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এই জন্য দুদু মিঞা স্মরণীয়।
নীল বিদ্রোহে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা কীরূপ ছিল ?
উত্তরঃ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার মাধ্যমে নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনি নিয়মিত প্রকাশ করেন এবং তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।
সন্ন্যাসী–ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হলো কেন?
উত্তরঃ ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, মুশা শাহের পরবর্তী যোগ্য নেতার অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, সাম্প্রদায়িক বিভেদ, বিদ্রোহীদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব এবং কোম্পানির আক্রমণে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল।
নীল বিদ্রোহে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা কীরূপ ছিল ?
উত্তরঃ বাংলায় নীল বিদ্রোহে খ্রিস্টান মিশনারিরাই সর্বপ্রথম আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মানসিক শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের চার্চ মিশনারি সোসাইটির তিনজন সদস্য এবং জার্মান মিশনারির বোমভাইটস, জে জি লিঙ্কে সর্বোপরি জেমস লঙ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
চুয়াড় বিদ্রোহের গুরুত্ব কী ?
উত্তরঃ (ক) চুয়াড় বিদ্রোহে জমিদার ও কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল যা সব কৃষক বিদ্রোহে লক্ষ করা যায় না। (খ) এটি ছিল ব্রিটিশ শাসন–শোষণ–অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরক্ষর আদিবাসী চুয়াড়দের প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ। (গ) চুয়াড় বিদ্রোহের ব্যাপকতা লক্ষ করে সরকার ওই অঞ্চলে নিলামে জমি বিলি বন্দোবস্তের নীতি ত্যাগ করে।
দক্ষিণ–পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি কেন গড়ে তোলা হয়েছিল?
উত্তরঃ দক্ষিণ–পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি : ব্রিটিশ সরকার কোল বিদ্রোহের শেষে 1834 খ্রিস্টাব্দে ছোটোনাগপুর বিভাগটিকে বিহার প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ‘দক্ষিণ–পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি‘ নামে এক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল গঠন করে। সরকার ঘোষণা করে যে এখানে ব্রিটিশ আইন বাতিল হবে এবং কোলদের নিজস্ব আইনকানুন কার্যকর করা হবে।
ফরাজি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কী?
উত্তরঃ ব্যর্থতার কারণ : ফরাজি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলি হলো—যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব, সংহতির অভাব এবং ব্রিটিশবিরোধিতার প্রবণতা হ্রাস।
নীল বিদ্রোহে সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষের অবদান গুরুত্বপূর্ণ কেন?
উত্তরঃ সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ বাংলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে গরিব নীলচাষিদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ নিজে দেখে এসে সেই মর্মস্পর্শী কাহিনি হিন্দু প্যাট্রিয়ট সহ অন্যান্য পত্রিকায় তুলে ধরেন। এই জন্য তাঁকে বাংলার প্রথম ‘Field Journalist’ বলা হয়।
খুৎকাঠিপ্রথা কী ?
উত্তরঃ খৎকাঠি কথার অর্থ জমির যৌথ মালিকানা। এই প্রথা অনুযায়ী মুন্ডারা দীর্ঘদিন ধরে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জমির যৌথ মালিকানা ভোগ করত। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের পুরোনো ভূমিব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং সেখানে জমি জরিপ ও ব্যক্তিগত মালিকানার আবির্ভাব হয়।
বেটবেগারি প্রথা কী ?
উত্তরঃ মুন্ডা উপজাতির মানুষদের যে প্রথা অনুযায়ী জমিদার ও মহাজনরা বিনা মজুরিতে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে বাধ্য করত, তাকে বেটবেগারিপ্রথা বলে।
কেনারাম ও বেচারাম কী ?
উত্তরঃ কেনারাম ও বেচারাম হলো দু‘ধরনের ভুয়ো বাটখারা। বহিরাগত ব্যবসায়ীরা যখন সাঁওতালদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনত, তখন প্রকৃত ওজনের চেয়ে বেশি ওজনের বাটখারা ব্যবহার করত। এই বাটখারা কেনারাম নামে পরিচিত ছিল। আবার ওই ব্যবসায়ীরা যখন সাঁওতালদের কাছে লবণ, চিনি প্রভৃতি ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করত, তখন প্রকৃত ওজনের চেয়ে কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করত। এই ধরনের কম ওজনের বাটখারাকে বলা হতো বেচারাম।
ফরাজি খিলাফত কী ?
উত্তরঃ ফরাজি আন্দোলনের নেতা দুদু মিঞা আন্দোলনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে যে ফরাজি প্রশাসন গড়ে তোলেন তাকে বলা হয় ফরাজি খিলাফত । এই শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন তিনি স্বয়ং।
নীল বিদ্রোহের দু‘টি বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তরঃ নীল বিদ্রোহের ভয়াবহতা দেখে সরকার নীলচাষ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল।
নীল বিদ্রোহে একমাত্র বাংলার কৃষকরা প্রথম হরতাল বা ধর্মঘটের পথে পা বাড়ায়।
কোল বিদ্রোহের দু‘টি গুরুত্ব লেখো।
উত্তরঃ কোল বিদ্রোহ অন্য উপজাতিদের বিদ্রোহী হতে উৎসাহিত করেছিল।
কোম্পানি বাধ্য হয়ে দক্ষিণ–পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি গঠন করেছিল।
মুন্ডা বিদ্রোহের দু‘টি গুরুত্ব লেখো। অথবা, মুন্ডা বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য কী?
উত্তরঃ এই বিদ্রোহের পর উপজাতি এলাকায় ভূমি বন্দোবস্ত–এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
এই বিদ্রোহের দ্বারা বেগার শ্রমপ্রথা নিষিদ্ধ হয়।
ব্রিটিশ সরকার কেন অরণ্য আইন চালু করেছিল ?
উত্তরঃ ঔপনিবেশিক অঞ্চলে নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য 1865 খ্রিস্টাব্দে অরণ্য আইন প্রবর্তন করা হয়।
কবে, কার বিরুদ্ধে, কার নেতৃত্বে রংপুরে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল?
উত্তরঃ 1783 খ্রিস্টাব্দে দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নুরুলউদ্দিনের নেতৃত্বে রংপুর বিদ্রোহ হয়েছিল।
ফরাজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ?
উত্তরঃ ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার দূর করা, ইসলামি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং ধর্মসম্মতভাবে মুসলিম সমাজ গঠন করা ছিল ফরাজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য।
তিতুমিরের বারাসত বিদ্রোহের লক্ষ্য কী ছিল ?
উত্তরঃ তৎকালীন সময়ে জমিদার, নীলকর ও কোম্পানির কর্মচারীদের শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও বাড়তি করের বিরুদ্ধে তিতুমির বিদ্রোহী হন বারাসত বিদ্রোহের মাধ্যমে।
সাঁওতাল বিদ্রোহের দু‘টি বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তরঃ এই বিদ্রোহের একটি ঔপনিবেশিকতাবিরোধী চরিত্র ছিল। ও সাঁওতাল ছাড়াও কর্মকার, চর্মকার, তেলি, ডোম, মুসলিম প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ যোগ দিলে তা গণবিদ্রোহে পরিণত হয়।
ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ণয় করো।
উত্তরঃ ‘ওয়াহাব’ কথার অর্থ হলো নবজাগরণ। ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার দূর করা, ইসলামি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মসম্মত মুসলিম সমাজ গঠন করার জন্য ওয়াহাবি আন্দোলন শুরু হলেও বাংলায় এই আন্দোলন অন্তিম পর্বে কিছুটা কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।
তরিকা–ই–মহম্মদিয়া‘ কী ?
উত্তরঃ ‘তরিকা–ই–মহম্মদিয়া‘ শব্দের অর্থ মহানবি মহম্মদ প্রদর্শিত পথ। ইসলাম ধর্মকে শুদ্ধিকরণের জন্য মহম্মদ আব্দুল ওয়াহাব নামক এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে আন্দোলন শুরু করেন তা ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। আর এই আন্দোলনের প্রকৃত নাম ‘তরিকা–ই–মহম্মদিয়া”।
সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ কোথায় কোথায় বিস্তার লাভ করে ?
উত্তরঃ1763-1800 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশ ও বিহারপ্রদেশে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ হয়েছিল। বিশেষ করে ঢাকা, বগুরা, রংপুর, কোচবিহার, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে এই আন্দোলন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল।
নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে কোন নাটকটি রচিত হয় ? এই নাটকটি কে রচনা করেন?
উত্তরঃ নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ‘নীলদর্পণ‘ নাটকটি রচিত হয়। রচনা করেন দীনবন্ধু মিত্র।
‘দামিন–ই কোহ’ কী ?
উত্তরঃ ‘দামিন–ই–কোহ্‘ শব্দের অর্থ হলো পাহাড়ের প্রান্তদেশ। সাঁওতালরা রাজমহলের প্রান্তদেশে বহুকষ্ট ও পরিশ্রমে তাদের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল। সাঁওতালদের এই নতুন অঞ্চলকে ‘দামিন–ই–কোহ’ বলা হতো।
নীলচাষের ক্ষেত্রে ‘দাদনপ্রথা‘ বলতে কী বোঝো?
উত্তরঃ নীলচাষের ক্ষেত্রে দাদন নামে একধরনের অগ্রিম অর্থ জোর করে চাষিকে দিয়ে দেওয়া হতো, যার বিনিময়ে উৎপাদিত নীল নীলকরদেরই বিক্রি করতে বাধ্য করা হতো।
কোম্পানির আমলে দু‘টি ভূমিরাজস্ব নীতি কী ছিল ?
উত্তরঃ 1793 খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং মহলওয়ারি বন্দোবস্ত।
বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর
সাঁওতাল বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ।
অথবা, সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল কেন ?
উত্তরঃ
সূচনাঃ অষ্টাদশ শতক থেকেই কোম্পানির প্রতিনিধিগণ, জমিদার ও মহাজন শ্রেণির শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে একাধিক উপজাতি বিদ্রোহ হয়েছিল। যার মধ্যে অন্যতম ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। সাঁওতাল উপজাতির মানুষেরা বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ধলভূম, ভাগলপুর অঞ্চলে বসবাস করত। তারা দীর্ঘদিন ধরেই সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।
সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট/কারণ
মহাজনি প্রকোপঃ জমিদারদের খাজনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ভয়ে সাঁওতালরা চড়াহারে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে বাধ্য হতো। এই ঋণের দায়ে তাদের জমির ফসল, গোরু–বাছুর, ঘরবাড়ি এমনকী মা–বোনদের ইজ্জত পর্যন্ত হারাতে হতো।
রেলপথ নির্মাণঃ রেলপথ নির্মাণের কাজে সাঁওতাল শ্রমিকদের নিয়ে গিয়ে খুবই কম পারিশ্রমিকে বা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেওয়া হতো।
খ্রিস্টধর্মের প্রচারঃ খ্রিস্টান মিশনারিরা সাঁওতালদের ধর্মকে নীচু করে দেখিয়ে তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করত, যা ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের অপর একটি কারণ।
অতিরিক্ত রাজস্ব আরোপঃ এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বনজঙ্গলের জমিকে চাষযোগ্য করে তুললেও তার ওপর কোম্পানি ও সরকার নিযুক্ত জমিদাররা রাজস্ব চাপাত যা ছিল এই বিদ্রোহের অপর একটি কারণ।
ফলাফল/গুরুত্বঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের ভয়াবহতায় কোম্পানি বাধ্য হয়ে সাঁওতালদের বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, পৃথক সাঁওতাল পরগনা গঠন করে, মহাজনদের শোষণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।
মন্তব্যঃ এই আলোচনায় স্পষ্ট যে সাঁওতাল বিদ্রোহ বাংলার কৃষক আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিস্ফোরণ। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও পরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।
কী উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন প্রণয়ন করা হয় ?
অথবা, কোন আইনের দ্বারা ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় উপজাতিগুলির অরণ্যের অধিকার হরণ করে ?
টীকা লেখো—অরণ্য আইন।
উত্তরঃ
সূচনাঃ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষে কৃষিজমির প্রসার, রাজস্ব খাতে আয়বৃদ্ধি এবং প্রচুর বনজ সম্পদ সংগ্রহ প্রভৃতি কারণে অরণ্যে বসবাসকারী মানুষের সাথে শুরু হয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষোভ–বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের অবসানের জন্য কোম্পানি সুচতুরভাবে 1865 খ্রিস্টাব্দে প্রণয়ন করে ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন।
অরণ্য আইন প্রণয়নের কারনঃ সমকালীন সময়ে কোম্পানির নৌবাহিনী তথা নৌশিল্পের জন্য ও ভারতে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর কাঠ। এই বনজ কাঠের ওপর ব্রিটিশ সরকার নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অরণ্য আইন প্রণয়ন করে।
লর্ড ডালহৌসির উদ্যোগঃ 1855 খ্রিস্টাব্দে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ‘ভারতীয় বনজ সম্পদের সনদ‘ নামে একটি আইন পাশ করে ভারতীয় অরণ্যের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ জারি করেন।
প্রথম ভারতীয় অরণ্য আইনঃ বনবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল ডায়াট্রিক ব্রান্ডিসের রিপোর্ট–এর ভিত্তিতে সরকার 1865 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ‘ভারতীয় অরণ্য আইন‘ পাশ করে।
আইনের বিভিন্ন ভাগঃ 1865 খ্রিস্টাব্দের অরণ্য আইন বাস্তবায়নের জন্য 1878 সালে ঘোষিত হয় ‘দ্বিতীয় অরণ্য আইন‘। এই আইনের দু‘টি দিক— 1. সংরক্ষিত এবং 2. সুরক্ষিত।
ফলাফলঃ এই আইন প্রণয়নের ফলে অরণ্য অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে দু‘টি গোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়—শিকারি এবং জুমচাষিরা। এই আইনে আদিবাসীরা শিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের বনজ সম্পদের অধিকার হরণ করা হয়।
নীল বিদ্রোহে সংবাদপত্রের ভূমিকা আলোচনা করো।
অথবা, নীল বিদ্রোহে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভূমিকা কী ছিল ?
উত্তরঃ
সূচনাঃ ঊনবিংশ শতকে বাংলায় সংগঠিত কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 1859-60 খ্রিস্টাব্দের নীল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ বাংলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষকগণ (নীলচাষি) শুরু করলেও তা বাংলা তথা ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।
মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাগরণঃ নীল বিদ্রোহের ব্যাপকতা সমকালীন বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মনে এক জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। এই বিদ্রোহে প্রথম ব্যাপকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল যা এর পূর্বে অন্য কোনো কৃষক আন্দোলনে দেখা মেলেনি।
লেখকদের ভূমিকাঃ বিভিন্ন লেখক তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে মানুষকে সোচ্চার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। যেমন—দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ‘নীলদর্পণ” নাটকে তৎকালীন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও নিষ্পেষিত নীলচাষিদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত ‘নীলদর্পণ‘ নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাও নীল বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করেছিল।
আইনজীবীদের ভূমিকাঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শম্ভুনাথের মতো খ্যাতনামা আইনজীবীরা নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দেন।
পত্রিকার সম্পাদকদের ভূমিকাঃ নীল বিদ্রোহকে সমর্থন করে যেসকল পত্রিকা ও তার সম্পাদকগণ সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া ঈশ্বরগুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর‘, অক্ষয়কুমার দত্তের ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, মার্শম্যানের ‘সমাচার দর্পণ‘ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল নীল বিদ্রোহের সংবাদ পরিবেশনে।
সীমাবদ্ধতা : নীল বিদ্রোহে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা যথেষ্ট হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা সীমাবদ্ধ ছিলেন। যেমন—কোম্পানির শাসনের প্রতি মোহগ্রস্ত অনেক শিক্ষিত বাঙালি নীল বিদ্রোহকে সরকারবিরোধী বিদ্রোহরূপে দেখতে চাননি। আবার অনেকেই ভাবতেন নীলচাষের ফলে ভারতের গ্রামগুলি সমৃদ্ধ হবে।
সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কারণগুলি বিশ্লেষণ করো
অথবা, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কে কী জানো ?
উত্তর
সূচনাঃ ভারতবর্ষে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে জমিদার ও কোম্পানির বিরুদ্ধে সংঘটিত কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। 1763-1800 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে।
বিদ্রোহের কারণঃ
অতিরিক্ত রাজস্বের চাপঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে সন্ন্যাসী–ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত গরিব শ্রেণির মানুষের ওপর উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য করলে বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত হয়।
তীর্থকর আরোপঃ ধার্মিক সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর অতিরিক্ত তীর্থকর আরোপ করলে তারা কোম্পানিবিরোধী হয়ে ওঠে।
ইজারাদারি শোষণঃ পেশায় কৃষিজীবী সন্ন্যাসী–ফকির সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব বর্তায় ইজারাদারদের ওপর। আর এই ইজারাদারগণ নিজেদের মুনাফালাভের আশায় অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করার জন্য তাঁদের তীব্র শোষণ করত প্রতিনিয়ত যা ছিল এই বিদ্রোহের অপর একটি কারণ।
বিদ্রোহের সূচনাঃ 1763 খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় এই বিদ্রোহের সূচনা হলেও অচিরেই তা দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ফরিদপুর, রংপুর, বগুড়া সহ প্রায় সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।
মূল্যায়নঃ অল্প সময়ে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বিশেষ করে সাংগঠনিক দুর্বলতা, অর্থের অভাব এবং ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, মজনু শাহ, চিরাগ আলি ও মুশা শাহের পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই সন্ন্যাসী–ফকির বিদ্রোহ শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল।
সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রকৃতি / চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
সাঁওতাল বিদ্রোহ কি প্রকৃতই সাঁওতালদের বিদ্রোহ ছিল ?
উত্তরঃ
সূচনাঃ 1855-56 খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল দরিদ্র সাঁওতালদের এক আপসহীন সংগ্রাম। প্রথমাবস্থায় সাঁওতালদের নেতৃত্বে শুরু হলেও এই বিদ্রোহের প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
আদিবাসী বিদ্রোহঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল মূলত বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসী বা উপজাতি সাঁওতালদের বিদ্রোহ। সাঁওতালরাই ছিল এই বিদ্রোহের প্রাণশক্তি।
কৃষকবিদ্রোহঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল মূলত একটি কৃষকবিদ্রোহ। দরিদ্র ও শোষিত সাঁওতাল কৃষকরা জমিদার, মহাজন ও ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।
গণবিদ্রোহঃ কৃষকদের উদ্যোগে এই বিদ্রোহ শুরু হলেও স্থানীয় কামার, কুমোর, তেলি, গোয়ালা, মুসলিম তাঁতি, চামার, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায় ও পেশার মানুষও বিদ্রোহে শামিল হয়। তাই নরহরি কবিরাজ একে সকল সম্প্রদায়ের দরিদ্র জনগণের মুক্তিযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।
ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্রোহঃ কেউ কেউ সাঁওতাল বিদ্রোহে ধর্মের প্রভাব দেখতে পেলেও এই বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ধর্মকেন্দ্রিক ছিল না। বিদ্রোহী সাঁওতালরা ঈশ্বরকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তারা চিৎকার করে বলত, “ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি থাকেন বহু বহুদূরে। আমাদের বাঁচাবার কেউ নেই।”
মন্তব্যঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটা সত্য, বহুমুখী অন্যায়–অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাঁওতাল উপজাতির এই বিদ্রোহ এক আপসহীন সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছিল।
পাবনার কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
উত্তরঃ 1870-এর দশকে বর্তমান বাংলাদেশের পাবনায় কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল তা পাবনা বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
বিদ্রোহের কারণ
রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধিঃ 1859 সালের প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে কিছু কারণ দেখিয়ে ব্রিটিশরা পাবনার কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে দেয় যা তাদের ক্ষুব্ধ করে।
প্রতিকারের চেষ্টার ব্যর্থতাঃ 1870 সালের পরে পাবনার কৃষকরা এই রাজস্বের বোঝা কমানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় যা তাদের বিদ্রোহী করে তোলে।
ঐক্যবদ্ধতাঃ আইনিভাবে রাজস্ব কমানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে জমিদার ঈশানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পাবনার কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কৃষক বিদ্রোহ শুরু করে।
বিদ্রোহের গুরুত্বঃ পাবনার কৃষক বিদ্রোহ বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—এই বিদ্রোহের ফলে কৃষকদের নিয়ে রায়ত সভা গঠিত হয়, বিদ্রোহে বিভিন্ন ধর্মের কৃষক শামিল হওয়ায় এর ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণ হয় এবং সর্বোপরি 1885 সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বলবৎ হয়।
মূল্যায়ন : ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে পাবনার কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অভাব ছিল। নীল বিদ্রোহের তুলনায় পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ছিল আদর্শগতভাবে সীমাবদ্ধ।
রংপুর কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
অথবা, টীকা লেখো : রংপুর বিদ্রোহ।
অথবা, রংপুর বিদ্রোহের কারণ কী ছিল ? এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যা জানো লেখো।
উত্তরঃ
বাংলার কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ। দেবী সিংহ নামে জনৈক ব্যক্তি 1781 খ্রিস্টাব্দে সরকারের কাছ থেকে দিনাজপুর, রংপুর ও একাদ্রপুর পরগনা ইজারা নেন। কিছুদিনের মধ্যেই দেবী সিংহের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলে যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয় তা রংপুর বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
রংপুর বিদ্রোহের কারণ
ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারঃ দেবী সিংহ দিনাজপুর, রংপুর ও একাদ্রপুর পরগনার ইজারা নিয়ে সেখানকার জমিদার ও প্রজাদের ওপর রাজস্বের হার বহুগুণ বৃদ্ধি করেন এবং নানা নতুন কর আরোপ করেন ।
জমিদারি বাজেয়াপ্তঃ সরকারি নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারায় জগদীশ্বরী চৌধুরি, জয়দুর্গা চৌধুরানির জমিদারি সহ অনেকের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হয় ।
রংপুর বিদ্রোহের সূচনাঃ দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরের কাজিরহাট, কাকিনা, ফতেপুর প্রভৃতি স্থানের কৃষকরা 1783 খ্রিস্টাব্দের 18 জানুয়ারি ‘তেপা’ গ্রামে মিলিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই ঘটনা ইতিহাসে রংপুর বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠাঃ বিদ্রোহীরা একটি স্থানীয় স্বাধীন সরকার গঠন করেন। এই সরকারের নবাব বা নেতা হন নুরুলউদ্দিন এবং তাঁর সহকারী নেতা হন দয়ারাম শীল।
বিদ্রোহ দমনঃ খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও বিদ্রোহের ভয়াবহতা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু রংপুরের কালেক্টর গুডল্যান্ড বিদ্রোহ দমনে সুবিশাল ব্রিটিশ বাহিনী পাঠান মোগলহাট ও পাটগ্রামের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে পরাজিত হলে বিদ্রোহ বন্ধ হয়। ব্রিটিশ বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, অসংখ্য বিদ্রোহীকে হত্যা করে।
মুন্ডা বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
অথবা, বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করো।
অথবা, মুন্ডা বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো।
উত্তরঃ
সূচনাঃ আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায় 1899-1900 খ্রিস্টাব্দে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী বিদ্রোহ করেছিল তা মুন্ডা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। মুন্ডা উপজাতি স্বাধীন মুন্ডারাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্রোহ করেছিল।
মুন্ডা বিদ্রোহের কারণঃ
বেগার শ্রমঃ জমিদার ও মহাজনরা মুন্ডাদের ওপর বেত–বেগারি বা জবরদস্তি বেগার খাটার প্রথা চাপিয়ে দেওয়ার। কারণে মুন্ডারা বেগার খাটতে বাধ্য হয়। আর এটাই ছিল মুন্ডা বিদ্রোহের কারণ।
খ্রিস্টধর্মের প্রচারঃ তৎকালীন সময়ে অশিক্ষিত গরিব মুন্ডাদের মধ্যে জোর করে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন পাদরিরা। এই ধর্মান্তরিতকরণ ছিল মুন্ডা বিদ্রোহের কারণ।
খুৎকাঠিপ্রথার অবসান : মুন্ডাদের একটি প্রাচীন প্রথা ছিল খুৎকাঠিপ্রথা। এর অর্থ হলো জমির ওপর যৌথ মালিকানা। কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থায় এই প্রথার অবসান হলে মুন্ডাদের মালিকানাস্বত্ব বিলুপ্ত হতে থাকে যা ছিল মুন্ডা বিদ্রোহের অপর একটি কারণ।
অন্যান্য কারণঃ এ ছাড়া মুন্ডাদের থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার, মুন্ডাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপন্নতা দেখেই বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে শুরু হয় মুন্ডা বিদ্রোহ। অচিরেই তা রাঁচি, বুন্দ,তামার, কারা, বাসিয়া প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।
মুন্ডা বিদ্রোহের গুরুত্ব/ফলাফলঃ মুন্ডা বিদ্রোহের ভয়াবহতায় বাধ্য হয়ে কোম্পানি মুন্ডা শ্রেণির স্বার্থে কিছু নিয়ম চালু করে। যেমন–
ছোটোনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়।
মুন্ডা সম্প্রদায়ের পূর্বের প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা রক্ষা পায়।
মুন্ডা বিদ্রোহ থেকে ভবিষ্যতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রেরণা পাওয়া যায়।
মুন্ডাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।
কোল বিদ্রোহের কারণ ও বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করো।
উত্তরঃ বিহারের ছোটোনাগপুরে কোল জাতির নিবাস ছিল। ব্রিটিশ শাসনে তারা ব্রিটিশ, জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এই বিদ্রোহ কোল বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
কোল বিদ্রোহের কারণগুলি হলো—
রাজস্বঃপূর্বে কোলদের কোনোরকম রাজস্ব প্রদান করতে হতো না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা শুরু হয়। তাতে এদের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করা হয়। বহিরাগত জমিদার ও মহাজনদের হাতে কোম্পানি এখানকার জমির ইজারা দিয়ে দেয়।
উচ্চহারে রাজস্ব আদায়ঃ জমিদাররা রাজস্বের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়াও কোলদের ওপর অন্যান্য করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় যা প্রদান করতে গিয়ে কোলরা নিঃস্ব হয়ে যায় ৷
অত্যাচারঃ ইজারাদাররা রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রভূত অত্যাচার চালায়। তারা কোলদের জমি থেকে উৎখাত করতে থাকে। কোল রমণীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চলতে থাকে। তাদের লাঞ্ছিত করা হয়। নানা অজুহাতে কোলদের বন্দি করা হয়।
চিরাচরিত ঐতিহ্যের অবক্ষয়ঃ কোলদের চিরপ্রাচীন আইন ও বিচারপদ্ধতি কোম্পানি ধ্বংস করে দিয়ে নিজেদের আইন তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে কোলদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।
বিস্তারঃ কোল বিদ্রোহ সিংভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ জেলার সর্বত্র বিস্তারলাভ করে। বিদ্রোহীরা ইংরেজ, জমিদার ও মহাজনদের বাড়িতে আক্রমণ করে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। বহুলোক বিদ্রোহীদের হাতে মারা যায়। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বুদ্ধু ভগত, জোয়া ভগত, সিংরাই, ঝিন্দরাই মানকি, সুই মুন্ডা প্রমুখ।
করে।
বিদ্রোহের ফলে কোম্পানি কোলদের জন্য পৃথক দক্ষিণ–পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল গঠন তাদের জমি ফিরিয়ে দেয় । কোলদের আইন, বিচারব্যবস্থা তাদের বাসভূমিতে পুনরায় স্থাপিত হয়।
চুয়াড় কথার অর্থ কী ? চুয়াড় বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।
অথবা, চুয়াড় বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল/গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উত্তরঃ
সূচনাঃ চুয়াড় কথার অর্থ হলো : উপজাতি কৃষক সম্প্রদায়‘। চুয়াড় বলতে বাঁকুড়া মেদিনীপুর, ধলভূম, ও মানভূমের ভূমিজ অর্থাৎ কৃষিজ আদিম অধিবাসীদেরকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ইংরেজ শাসনকালে এই অঞ্চলের অধিকাংশ জমি কেড়ে নিয়ে উচ্চমূল্যে ইজারা দেওয়া শুরু হলে এখানে চুয়াড় বিদ্রোহের সূচনা হয় ।
চুয়াড় বিদ্রোহের কারণ
উচ্চহারে খাজনা ধার্যঃ চুয়াড় সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিনা খাজনার জমি ভোগ করত। কিন্তু কোম্পানি তাদের এই অধিকার খর্ব করলে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
জীবিকার সমস্যাঃ ব্রিটিশ কোম্পানি চুয়াড়দের অধিকাংশ জমি কেড়ে নিলে চুয়াড় সম্প্রদায়ের মানুষেরা জীবন–জীবিকার সমস্যায় ভোগে।
জমিদারদের অসন্তোষঃ উচ্চহারে কর ধার্য করলে অনেক জমিদার তাদের জমিদারি হারায়। ফলে জমিদাররাও চুয়াড়দের সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়।
অতিরিক্ত নির্যাতনঃ কোম্পানির কর্মচারীরা চুয়াড় সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর যে কঠোর অত্যাচার চালাত তা ছিল চুয়াড় বিদ্রোহের অপর একটি কারণ।
বিদ্রোহের সূচনাঃ উপরিউক্ত কারণে চুয়াড় সম্প্রদায়ের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান ধলভূমের জমিদার জগন্নাথ ধল 1768 খ্রিস্টাব্দে চুয়াড়দের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহের মাধ্যমে 1798-99 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পর্বে চুয়াড়রা আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে দুর্জন সিং–এর নেতৃত্বে।
চুয়াড় বিদ্রোহের ফলাফল
চাষের জমি ফেরতঃ এই বিদ্রোহের চাপে পড়ে কোম্পানি চুয়াড়দের জমি ফেরত দিয়ে বাধ্য হয়।
ঐক্যবদ্ধতাঃ এই বিদ্রোহে জমিদার ও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ রূপ লক্ষ করা যায় বিদ্রোহের জন্য সম্ভব হয়েছিল।
রাজস্বের পরিমাণ হ্রাসঃ চুয়াড় বিদ্রোহের চাপে পড়ে কোম্পানি বাধ্য হয়েছিল রাজস্বের পরিমাণ কমিয়ে দিতে।
পৃথক জঙ্গলমহল গঠনঃ চুয়াড় বিদ্রোহের ফলে কোম্পানি বাধ্য হয়ে চুয়াড়দের বসতি অঞ্চল নিয়ে পৃথক ‘জঙ্গলমহল‘ গঠন করেছিল।
টীকা লেখোঃ তরিকা–ই–মহম্মদিয়া।
উত্তরঃ
ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত নাম হলো তরিকা–ই–মহম্মদিয়া। তরিকা–ই–মহম্মদিয়া কথার অর্থ হলো মহম্মদ প্রদর্শিত পথ। মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব প্রবর্তিত ধর্মীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন ছিল তরিকা–ই–মহম্মদিয়া। অষ্টাদশ–উনিশ শতকে আরবদেশ তথা ভারতীয় মুসলিম সমাজে যে পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন শুরু হয় তা ‘তরিকা–ই–মহম্মদিয়া‘ নামে পরিচিত। এই ভাবধারার মূলকথা হলো ইসলামকে অতীতের পবিত্রতায় ফিরিয়ে দেওয়া,অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা।
তরিকা–ই–মহম্মদিয়ার উদ্দেশ্যঃ তরিকা–ই–মহম্মদিয়া আন্দোলনের মূলউদ্দেশ্য হলো মহম্মদ প্রদর্শিত পথ প্রতিষ্ঠা করা, ইসলাম ধর্মের মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারগুলির বিলোপ ঘটানো, এ ছাড়া ভারতবর্ষকে শত্রুমুক্ত করা।
আরবদেশে আন্দোলনঃ অষ্টাদশ শতকে আবদুল ওয়াহাব নামে জনৈক ব্যক্তি আরবদেশে ‘তরিকা–ই–মহম্মদিয়া‘ নামক মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর নামানুসারে সাধারণভাবে এটি ‘ওয়াহাবি আন্দোলন‘ নামেই বেশি পরিচিত।
ভারতে আন্দোলনঃ দিল্লির মুসলিম সন্ত শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং তাঁর পুত্র আজিজ ভারতে ‘তরিকা–ই–মহম্মদিয়া‘ অর্থাৎ ওয়াহাবি আন্দোলনের ভাবধারা প্রচার করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইসলামের শুদ্ধিকরণ ঘটিয়ে সমাজকে পবিত্র করা।
বাংলায় আন্দোলনঃ উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজেও শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে ‘তরিকা–ই–মহম্মদিয়া’র ভাবধারা প্রচারিত হয়। বাংলায় এই ভাবধারার প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নেন তিতুমির বা মির নিশার আলি। তাঁর অনুগামীরা প্রচার করেন যে অমুসলিমদের অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনে ভারত ‘দার–উল–হারব‘ অর্থাৎ বিধর্মীর দেশে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশকে ‘দার–উল–ইসলাম‘ অর্থাৎ পবিত্র ইসলামের দেশে পরিণত করতে হবে।
রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর
ফরাজি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
অথবা, ফরাজি আন্দোলন কতটা সফল হয়েছিল বলে তুমি মনে করো?
অথবা, ফরাজি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।
অথবা, টীকা লেখো—ফরাজি আন্দোলন।
অথবা, ফরাজি আন্দোলনের কারণ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তরঃ
সূচনাঃ ফরাজি একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হলো ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য‘। অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য যে সংস্কারকামী আন্দোলনের সূচনা করে তা–ই ফরাজি আন্দোলন নামে পরিচিত।
ফরাজি আন্দোলনের কারণ
ধর্মীয় সংস্কারঃ ইসলাম ধর্মের শুদ্ধতা রক্ষা করে ধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করা বিশ্বদরবারে এই ধর্মের প্রচারের জন্য শুরু হয়েছিল ফরাজি আন্দোলন।
দার–উল–ইসলামে পরিণত করাঃ মুসলিম সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করে বাংলাদেশকে ‘দার–উল–হারব’বা বিধর্মীদের দেশ থেকে ‘দার–উল–ইসলাম‘ বা ইসলামের দেশে পরিণত করার জন্যও হাজি শরিয়ত উল্লাহ এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন।
রাজনৈতিক কারণঃ ধর্মীয় উদ্দেশ্যের সাথে সাথে আন্দোলনের রাজনৈতিক কারণও ছিল। দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের রক্ষা করতে আন্দোলনকারীরা অত্যাচারী ইংরেজ, জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল।
ফরাজি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যঃ
প্রথমত, এই আন্দোলন ছিল ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের আন্দোলন, যার কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল পূর্ববাংলার ফরিদপুর অঞ্চলে।
দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন পরিচালনার ভার যেহেতু প্রথম থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের বাংল হাতে ছিল তাই নিম্নবর্ণের হিন্দু বাদে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই আন্দোলন নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।
তৃতীয়ত, এই আন্দোলনের দ্বারা হাজি শরিয়ত উল্লাহ–এর অনুগামীতে পরিণত হয়েছিল জমিদারদের হাতে উৎখাত হওয়া প্রজা, বেকার ও কারিগর শ্রেণির মানুষজন ।
চতুর্থত, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়াও স্থানীয় জমিদার, নীলকর ও ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছিল এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য
ফরাজি আন্দোলনের গুরুত্ব
প্রথমত, শুধুমাত্র মুসলিম শ্রেণির মানুষেরাই নয়, হিন্দু কৃষকরাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।
দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন ব্যভিচারী বিদেশি শাসকের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির স্পৃহাকে জাগিয়ে তোলে। ফরাজি আন্দোলনকে এই কারণে স্বাধীনতা আন্দোলন বললেও কোনো অত্যুক্তি হয় না।
তৃতীয়ত, ফরাজি আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করতে না পারলেও বাংলা থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নে প্রেরণা জুগিয়েছিল।
চতুর্থত, কিছু ইতিহাসবিদের মতে, এই আন্দোলনে শ্রেণিসংগ্রামের ঝলক পাওয়া যায়। শক্তিশালী ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণির সংগ্রাম এই মতকে প্রতিষ্ঠা করে।
ফরাজি আন্দোলনের প্রকৃতি
কৃষক বিদ্রোহঃ ফরাজি আন্দোলনের শেষ পর্বে এর প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কারণ দলে দলে কৃষক জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে আন্দোলনে যোগদান করে। ফলে ধর্মীয় কারণে শুরু হওয়া আন্দোলন কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়।
ধর্মীয় আন্দোলনঃ ‘ফরাজি’ কথার অর্থ ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য। আন্দোলনে । এই জনগণ ধর্মীয় কারণে একত্রিত হয়েছিল এ কথা বলা যায়। তাই ফরাজি আন্দোলন ছিল ধর্মীয় পুনরুত্থানের আন্দোলন।
সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাঃ ফরাজি আন্দোলন আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে। তাই অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেছেন—“এই আন্দোলন প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও শেষ পর্বে কৃষকদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিল।”
নীল বিদ্রোহের কারণ, ফলাফল, গুরুত্ব লেখো।
অথবা, নীল বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
অথবা, নীল বিদ্রোহের কারণ ও বৈশিষ্ট্য লেখো।
অথবা, নীল বিদ্রোহের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তর
সূচনাঃ মহাবিদ্রোহের পরবর্তীতে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল য়ের বাংলার নীল বিদ্রোহ। নীলকর সাহেবদের সীমাহীন অত্যাচারের প্রতিবাদে নদিয়ার চৌগাছা গ্রামে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের হাত ধরে 1859-1860 খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয় নীল বিদ্রোহ ।
নীল বিদ্রোহের কারণঃ
নীলচাষে বাধ্য করাঃ বাংলা এবং বিহারের বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের খাদ্যশস্য বা অন্যান্য ফসল চাষ বন্ধ করে নীলকর সাহেবরা জোর করে তাদের নীলচাষ করতে বাধ্য করত। ফলে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
চাষিদের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিঃ জোর করে নীলচাষ করানোর সাথে সাথে উৎপাদিত নীল কৃষকদের কমদামে বিক্রি করতেও বাধ্য করত নীলকর সাহেবরা যা ছিল বিদ্রোহের অপর একটি কারণ।
দাদনপ্রথাঃ গরিব চাষিদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নীলকর সাহেবরা অগ্রিম অর্থ হিসেবে দাদন নিতে বাধ্য করত কৃষকদের। সাথে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতেও তারা বাধ্য করত। এই চুক্তিপত্রের দ্বারা কৃষকদের আমৃত্যু নীলচাষে বাধ্য করা হতো। চাষিদের অবস্থা হতো কে ভূমিদাসের মতো ।
দমনমূলক পঞ্চম আইনঃ 1830 খ্রিস্টাব্দে বেন্টিঙ্ক কর্তৃক বলবৎ করা পঞ্চম আইন অনুসারে নীলকর সাহেবদের সাথে চুক্তিভঙ্গ ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হতো। এই হিংসাত্মক ও দমনমূলক আইনের প্রতি কৃষকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
উপরিউক্ত কারণে1859-60 খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় নীল বিদ্রোহ।
নীল বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য
সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতিঃ এই বিদ্রোহ বিশেষ কোনো একটি ধর্ম–সম্প্রদায় নয়, হিন্দু–মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত কৃষক নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শামিল হয়।
জমিদারদের অংশগ্রহণঃ বাংলার কিছু জমিদার এই বিদ্রোহে কৃষকদের সাথে যোগদান করে নীলচাষের বিরোধিতা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রানাঘাটের শ্রীগোপাল পালচৌধুরী চণ্ডীপুরের শ্রীহরি রায়, নড়াইলের রামরতন রায় উল্লেখযোগ্য।
সংবাদপত্রের ভূমিকাঃ কৃষকদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে যেসকল সংবাদপত্র সোচ্চার হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রধান ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’, ‘গ্রামবাৰ্ত্তা প্রকাশিকা‘, ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, ‘সমাচার দর্পণ’।
মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকাঃ উপরিউক্ত সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীলচাষিদের দুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে নীল বিদ্রোহকে সমর্থন করে।
নীল বিদ্রোহের ফলাফল/গুরুত্বঃ
নীল কমিশন গঠনঃ নীল বিদ্রোহের চাপে পড়ে বাংলার ছোটোলাট জে.পি. গ্রান্ট 1860 সালে নীল কমিশন গঠন করেন। এতে স্থির হয় নীলকররা জোর করে কাউকে নীলচাষ করাতে পারবে না।
জাতীয় চেতনার উন্মেষঃ নীল বিদ্রোহে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের মিলিত অংশগ্রহণ পরোক্ষভাবে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।
সংঘবদ্ধ হবার গুরুত্বঃ নীল বিদ্রোহে সকল শ্রেণি ও ধর্মের মানুষের সংঘবদ্ধতা প্রমাণ করেছিল যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সাফল্য এনে দিতে পারে। শিশিরকুমার ঘোষ তাই বলেছেন—“এই নীল বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছিল।”