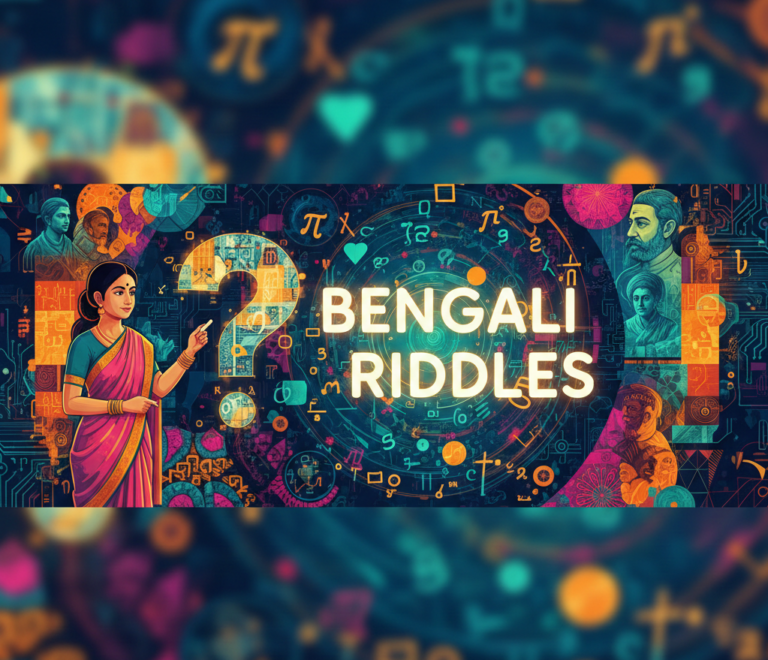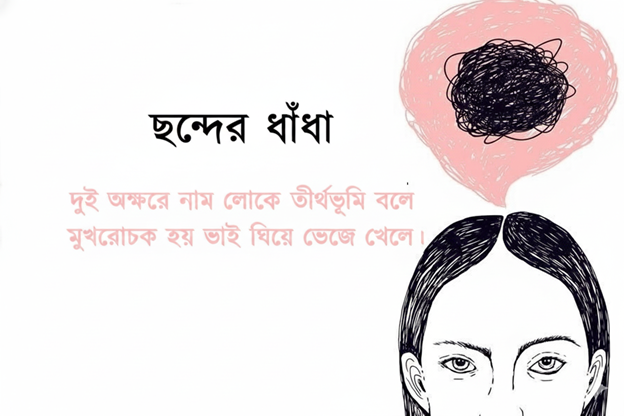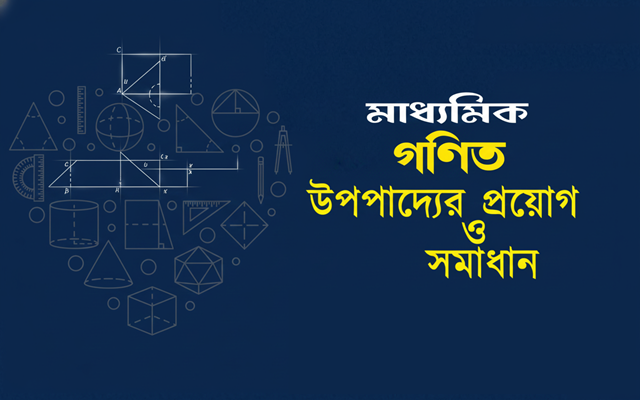অর্থনীতি - সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের বিশেষ অনুশীলনী - পর্ব ১
অর্থনীতি – সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের বিশেষ অনুশীলনী – পর্ব ১
Economics Short Questions and Answers- Part – 1
প্রশ্ন ১। স্বল্পোন্নত দেশ কাকে বলে?
উত্তর। স্বল্পোন্নত দেশ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন একটি দেশ, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে মূলধন সৃষ্টির হার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কম, মাথাপিছু জাতীয় আয় কম এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনুন্নত।
প্রশ্ন ২। উন্নয়নশীল দেশ কাকে বলে?
উত্তর। স্বল্পোন্নত দেশ যখন উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে তখন তাকে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ।উন্নয়নশীল দেশ এক অর্থে উন্নয়নের পথে অগ্রসরমান একটি স্বল্পোন্নত দেশ, অর্থাৎ এমন একটি দেশ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে মূলধন সৃষ্টির হার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কম থাকে। তবে উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে সেই দেশের অনগ্রসরতার মাত্রা কমতে থাকে।
প্রশ্ন ৩। উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশের প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য কী কী?
উত্তর।(১)উন্নয়নশীল দেশগুলি মূলত কৃষিপ্রধান, (২) উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মূলধন সৃষ্টির হার অপেক্ষাকৃত কম, (৩) উন্নয়নশীল দেশে দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Dual Economy) পরিলক্ষিত হয়, (৪) গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা (Disguised Unemployment) পরিলক্ষিত হয়।
প্রশ্ন ৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নের কী কী লক্ষণ আছে ?
উত্তর।অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষণগুলি হল—(ক) সমৃদ্ধির হার (rate of growth) বেশি, (খ) জনপ্রতি প্রকৃত আয় (per capita real income) বাড়তে থাকে, (গ) মূলধন সরবরাহের প্রাচুর্য ও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি, (ঘ) শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদন শক্তি বেশি, (ঙ) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, (চ) শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বা মানবিক মূলধনে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং (ছ) উন্নত আর্থিক পরিকাঠামো।
প্রশ্ন ৫। দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অর্থ কী ?
উত্তর।দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি ক্ষেত্র হচ্ছে বড় বড় শহরে অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো যেখানে বড় বড় ব্যাংক, ব্যবসা-বাণিজ্য, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান (দেশি অথবা বিদেশি) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ক্ষেত্রকে বলা হয় উন্নত বা পুঁজিবাদী ক্ষেত্র (Capitalist Sector) ; অপর ক্ষেত্রটি হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে দেশের অধিকাংশ লোক কোনও রকমে জীবনধারণ করে। এই ক্ষেত্রকে বলা হয় জীবনধারণের (Subsistence Sector) ক্ষেত্র। স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই দুটি ক্ষেত্র দেখা যায়।
Latest Economy MCQ Objective Question and Answer
প্রশ্ন ৬। ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী?
উত্তর। ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—(১) ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ, (২) ভারতে গ্রামীণ বেকার সমস্যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, (৩) ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো দ্বিক্ষেত্র বিশিষ্ট, (৪) প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকার সমস্যা, (৫) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি, (৬) ভারতের জাতীয় আয় এবং জনপ্রতি প্রকৃত আয় খুব কম,(৭) দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, (৮) জাতীয় আয় বণ্টনের বৈষম্য, (৯) মুদ্রাস্ফীতি ও বহির্বাণিজ্যের ঘাটতিতে জর্জরিত এবং (১০) স্বল্প হারে মূলধনসৃষ্টি।
প্রশ্ন ৭। ভারতের জাতীয় আয়ে ক্ষেত্রগত পরিবর্তন কীভাবে হচ্ছে ?
উত্তর।ভারতের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক অবদানের অনুপাত ক্রমশ বিশেষভাবে কমছে, মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদানের অনুপাতও কিছু কমছে ; অপরদিকে তৃতীয় ক্ষেত্রের (সেবাস্রোত) অবদানের অনুপাত ক্রমশ বাড়ছে।
প্রশ্ন ৮। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক হার কত ?
উত্তর। ২০১১ সালে সেন্সাস-কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বেড়েছে ১৭.৬৪ শতাংশ।
প্রশ্ন ৯। ভারতে বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় জনসংখ্যা কত ?
উত্তর। ২০১১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২৫ জন ।
প্রশ্ন ১০। ২০১১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা কত ?
উত্তর। ২০০১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা (২০১১ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত) ১২১ কোটি ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪২২।
প্রশ্ন ১১। ভারতে বর্তমানে পুরুষ ও মহিলার গড় আয়ু কত?
উত্তর। ভারতে পুরুষ ও মহিলার গড় আয়ু হল যথাক্রমে ৬৩.৬৭ বছর এবং ৬৬.৯১ বছর।
প্রশ্ন ১২। ভারতে বর্তমানে সাক্ষরতার হার কত ?
উত্তর। ২০১১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল ৭৪.০৪ শতাংশ।
প্রশ্ন ১৩। ভারতে সাক্ষরতার হার কোন্ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি এবং কত?
উত্তর। ভারতে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি কেরালায় এবং সেটা হল ৯০.৯২ শতাংশ।
প্রশ্ন ১৪। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন কতটা বেড়েছিল?
উত্তর। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন ৩.৪ শতাংশ বেড়েছিল।
প্রশ্ন ১৫। সর্বশেষ হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় আয় কীভাবে বেড়েছে?
উত্তর। সর্বশেষ হিসাবে ২০১০-১১ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের ১৪.২ শতাংশ সৃষ্ট হয়েছিল প্রাথমিক ক্ষেত্রে, ২২.৪ শতাংশ সৃষ্ট হয়েছিল মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এবং ৬৩.৪ শতাংশ সৃষ্ট হয়েছিল পরিষেবা ক্ষেত্র বা তৃতীয় (সেবাস্রোত) ক্ষেত্রে।
প্রশ্ন ১৬। ভারতে মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন কত ?
উত্তর। ২০০৯-১০ সালে মাথাপিছু নিট উৎপাদন হল ১৯৯৯-২০০০ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ৩৩৭৩১ টাকা।
প্রশ্ন ১৭। দারিদ্র্য সীমা পরিমাপ করার কয়েকটি পদ্ধতির নামোল্লেখ কর ।
উত্তর। দারিদ্র্য সীমা পরিমাপ করার কয়েকটি পদ্ধতি হল, (১) মাথা গণনার মাধ্যমে পরিমাপ (Head Count Measure)।(২) মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ পরিমাপ এবং এক্ষেত্রে বিচার করা হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জীবনধারণের জন্য কতটা ক্যালরি, প্রোটিন ও ভিটামিন পেয়ে থাকে; এটাকে প্ৰাণীগত দৃষ্টিভঙ্গি (Biological Approach) বলা হয়। (৩) আয়পন্থা (Income Method) প্রয়োগ করে দেখা সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাবার মত আয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আছে কিনা, এবং (৪) আপেক্ষিক বঞ্চনা (relative deprivation) পদ্ধতি প্রয়োগ।
প্রশ্ন ১৮। সপ্তম পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের অনুপাত কতটা কমিয়ে আনার কর্মসূচি ছিল?
উত্তর।সপ্তম পরিকল্পনার শেষে (১৯৮৯-৯০ সালে) দারিদ্র্যের অনুপাত ২৫.৮ শতাংশে কমিয়ে আনার কর্মসূচি ছিল।
Economics Short Questions and Answers- Part 1 by Team Make My Notes
প্রশ্ন ১৯। নেহরু রোজগার যোজনার অর্থ কী ?
উত্তর।নেহরু রোজগার যোজনা ১৯৮৯ সালে প্রবর্তিত হয়। এই প্রকল্প থেকে শহরাঞ্চলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কারবার গঠনের জন্য ঋণ দেওয়া হয় এবং মজুরির বিনিময়ে যাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় অথবা গরিবদের জন্য সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প প্রবর্তিত হয় সেজন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। শহরাঞ্চলের গরিব ও বেকারদের জন্য এই প্রকল্প প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে এই প্রকল্পটি ‘স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনার’ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।
প্রশ্ন ২০। জওহর রোজগার যোজনার অর্থ কী?
উত্তর। ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে গ্রামীণ দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য জওহর রোজগার যোজনা প্রবর্তিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই যোজনার নাম হয় জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা। বর্তমানে এই যোজনা স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগারের সঙ্গে মিশে গেছে।
প্রশ্ন ২১। ভারতে নতুন কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী ?
উত্তর।ভারতে নতুন কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) নিবিড় কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ এবং এজন্য উচ্চফলনশীল বীজ রোপণ, পর্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ, কৃষকদের কাছে স্বল্প দামে কীটনাশক ওষুধ সরবরাহ করা এবং যাতে জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদিত হয় তা সুনিশ্চিত করা, (২) আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষির যন্ত্রীকরণ, (৩) মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ, (৪) কৃষি উৎপাদনের জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ, (৫) কৃষকদের উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন, এবং (৬) সরকারি এজেন্সি কর্তৃক কৃষিজাত সামগ্রী ক্রয় করার ক্ষেত্রে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করার মত দাম প্রদান করা।
প্রশ্ন ২২। ভারতে সবুজ বিপ্লব বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর।ভারতে সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য হল, ষাটের দশকের শেষ পর্যায় এবং সত্তরের দশক থেকে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনের আশাতীত বৃদ্ধি এবং নতুন কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সামগ্রিকভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা একটি বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা বলেই এটাকে ‘সবুজ বিপ্লব’বলা হয়।
প্রশ্ন ২৩। ভারতে কৃষকদের জন্য সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগত ঋণের বিভিন্ন উৎস কী কী?
উত্তর।ভারতে কৃষকদের জন্য সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগত ঋণের উৎসগুলি হল—(ক) স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও সিডিউল্ড বেসরকারি ব্যাংক, (খ) কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাংক, (গ) আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, (ঘ) জমি উন্নয়ন ব্যাংক এবং (ঙ) সমবায় ঋণদান সমিতি।
প্রশ্ন ২৪। ‘অপারেশন বর্গা’ কথাটির অর্থ কী?
উত্তর।অপারেশন বর্গা হল, বর্গাকার বা ভাগচাষিদের নাম রেজিষ্ট্রি করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে অপারেশন বর্গার মাধ্যমে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বর্গাদারদের রেকর্ড থাকুক আর নাই থাকুক, যে জমিতে চাষ করবে আইন তাকে বর্গাদার হিসাবে কাগজপত্রে স্বীকার করে নেবে। জোতদার তাকে বর্গাদার স্বীকার না করলে আইন-আদালতের জন্য খরচ তাকেই বহন করতে হবে। তাছাড়া ফসল পাবার পর জোতদারকে বর্গাদারের নাম, ফসলের পরিমাণ, জমির দাগ নম্বর, তারিখ প্রভৃতি নিয়ে একটি রসিদ দিতে হবে। রসিদ না দেওয়া বেআইনি হবে এবং সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ বলে অনুমিত হয়েছিল।
প্রশ্ন ২৫। ভারতে কৃষিঋণের কারণগুলি কী কী ?
উত্তর।কৃষি- -ঋণের কারণগুলি হল—(১) কৃষকদের দারিদ্র্য, (২) গ্রামীণ মহাজনদের কাছে পুরুষানুক্রমে ঋণ, (৩) ব্যয়াধিক্যের চাপ, (৪) উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ পুরোপুরি না পাওয়া এবং মহাজনদের কাছে পণ্যের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ ও ঋণের উপর সুদ দেওয়া, (৫) বছরের কয়েকমাস বেকার থাকার দরুন ঋণের উপর নির্ভর করা।
প্রশ্ন ২৬। ভারতে দারিদ্র্যের মূল কারণগুলি কী কী ?
উত্তর।দারিদ্র্যের মূল কারণগুলি হল—(১) অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও সেই সঙ্গে স্বল্প আয় ও মূলধনের স্বল্পতা হেতু দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, (২) বেকার সমস্যার তীব্রতা, (৩) অর্ধবেকারত্ব ও উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি, (৪) মুদ্রাস্ফীতির-তীব্রতা হেতু ক্রয়শক্তি হ্রাস, (৫) কৃষি-শ্রমিকদের অত্যন্ত স্বল্প মজুরি এবং (৬) আয়ের বৈষম্য।
প্রশ্ন ২৭। জমির মালিক ও প্রজা-চাষিদের মধ্যে সম্পর্ক কী?
উত্তর।জমির মালিক নিজের জমিতে চাষ না করে প্রজা-চাষির (tenant farmer) মাধ্যমে জমি চাষ করাতে পারে। যখন প্রজা-চাষি জমির মালিককে এজন্য খাজনা প্রদান করে তখন তাদের বলা হয় রায়ত। কিন্তু প্রজা-চাষিরা ভাগচাষি হিসাবে কাজ করতে পারে। ভাগচাষি হিসাবে যারা বর্গা গ্রহণ করে থাকে তারা জোতদারের জমিতে চাষ করে এবং চাষের খরচ বাবদ জোতদারের কাছ থেকে টাকাও আদায় করে এবং তার বিনিময়ে উৎপাদনের একটি অংশ জোতদারের হাতে অর্পণ করে।
প্রশ্ন ২৮। আবাদযোগ্য জমি কাকে বলে ? অথবা, ‘অর্থনৈতিক জোত’ কাকে বলে ?
উত্তর। আবাদযোগ্য জমির সংজ্ঞা হল, আবাদযোগ্য জমি = মালিকানাধীন জমি + ইজারা নেওয়া জমি – ইজারা দেওয়া জমি।
প্রশ্ন ২৯। সমবায় কৃষিব্যবস্থা কাকে বলে ?
উত্তর।সমবায় কৃষিব্যবস্থা বলতে বোঝায় ‘যৌথ ব্যবস্থাপনায় জমির একত্রীকরণ’। সমবায় কৃষি ব্যবস্থায় জমির মালিকানা কৃষকদের থাকে,—তবে বিভিন্ন জমিখণ্ডকে একটিমাত্র কেন্দ্রের অধীনে কৃষিকাজের জন্য সংগঠিত করা হয় এবং সমবায়ের ভিত্তিতে ফসলের উৎপাদন ও বণ্টন করা হয়।
প্রশ্ন ৩০। মিশ্র অর্থনীতির কাঠামো বলতে কী বোঝায়?
উত্তর। মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোয় একটি থাকে সরকারি ক্ষেত্র এবং অপরটি থাকে বেসরকারি ক্ষেত্র।সরকারি ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকানায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, এই দুটি সহাবস্থানের মাধ্যমে মিশ্র অর্থনীতির কাঠামো গঠিত হয়।
প্রশ্ন ৩১। ভারতে প্রথম শিল্পনীতি কোন্ সালে ঘোষিত হয় ?
উত্তর। ভারতের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয় ১৯৪৮ সালে।
প্রশ্ন ৩২। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে কীভাবে বিভক্ত করা হয়েছিল?
উত্তর।১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণিতে ছিল ১৭টি শিল্প (যেমন অস্ত্র, গোলাবারুদ, আণবিক শক্তি, লোহা ও ইস্পাত, রেলওয়ে পরিবহন, জাহাজ শিল্প প্রভৃতি) যেগুলির ভবিষ্যত উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিল ১২টি শিল্প যেগুলি ক্রমে ক্রমে রাষ্টায়ত্তে আনার কথা বলা হয়েছিল। অবশিষ্ট শিল্পগুলিকে রাখা হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণিতে।
প্রশ্ন ৩৩। যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্র বলতে কী বোঝ?
উত্তর। ১৯৭৩ সালের শিল্প-লাইসেন্স নীতিতে যৌথ উদ্যোগের (Joint sector) ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছিল। যৌথক্ষেত্রে রাজ্য সরকার মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে।
প্রশ্ন ৩৪। ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিকে উদার শিল্পনীতি বলা হয় কেন?
উত্তর। ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিকে উদার শিল্পনীতি বলা হয় নিম্নলিখিত কারণে—(১) এই শিল্পনীতিতে একচেটিয়া ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বতম সীমার বিলোপ সাধন করা হয়েছে, (২) শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, (৩) জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় ১৮টি শিল্প বাদে সব শিল্পকে লাইসেন্সমুক্ত করা হয়েছে, (৪) বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা ৪০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫১ শতাংশ করা হয়েছে, (৫) বিদেশি প্রযুক্তিকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং (৬) মূলধন দ্রব্য আমদানি নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা হয়েছে।
প্রশ্ন ৩৫। রিপো রেট কাকে বলে ?
উত্তর। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যখন রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে স্বল্পকালীন ঋণ গ্রহণ করে তখন যে সুদের হারে সেই ঋণ নেওয়া হয় তাকে বলা হয় রিপো রেট (Repo Rate) ।
প্রশ্ন ৩৬। রুগ্ন শিল্পের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর। একটি শিল্পোদ্যোগকে তখনই রুগ্ন শিল্প বলা যায় যখন শিল্পটি পর পর কয়েক বছর যাবৎ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে এবং লোকসানের বোঝা আর বইতে পারছে না।
প্রশ্ন ৩৭। শিল্পক্ষেত্রে বিদায়নীতি বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। যেসব শিল্পোদ্যোগ রুগ্ন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে সেগুলিকে যদি লাভজনক সংস্থায় পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব না হয় তবে সেগুলিকে বন্ধ করে দিতে হবে এবং এজন্য এই সংস্থাগুলিতে যারা কর্মহীন হবে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দিষ্ট সময়ে অবসরের আগেই বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দিয়ে দিতে হবে। এটাই হল শিল্পক্ষেত্রে বিদায় নীতি।
প্রশ্ন ৩৮। ভারতের পাঁচটি উন্নয়ন ব্যাংকের নামোল্লেখ কর।
উত্তর। (১) কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাংক (NABARD)। (২) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (IDBI)।(৩) ভারতের শিল্প ঋণ সরবরাহ করপোরেশন (IFCI)। (৪) ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (SIDBI)। (৫) রপ্তানি-আমদানি ব্যাংক (EXIM BANK)।
প্রশ্ন ৩৯। রিভার্স রিপো রেট কাকে বলে ?
উত্তর। যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে আগেকার নেওয়া স্বল্পকালীন ঋণ ফেরত দেয় তখন সুদের হারকে বলা হয় রিভার্স রিপো রেট (Reverse Repo Rate)।
প্রশ্ন ৪০। ‘এক্সিম স্ক্রিপ’ কাকে বলে ?
উত্তর। ভারত সরকারের পূর্বতন আমদানি নীতিতে আমদানি লাইসেন্সকে বলা হত আর.ই.পি. লাইসেন্স বা Replenishment Licence, -কোন্ শিল্প কতটা রপ্তানি করেছে তার ভিত্তিতে আগে পাঁচ শতাংশ থেকে কুড়ি শতাংশের মধ্যে এই লাইসেন্সকে বেধে রাখা হত। ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে বলা হয়েছিল যে, সবক্ষেত্রেই এই লাইসেন্স একই হারে দেওয়া হবে এবং তার নাম রাখা হয়েছিল ‘এক্সিম স্ক্রিপ’ (Exim Scrip)। যেসব রপ্তানি ক্ষেত্রে আমদানির পরিমাণ কম, তাদের হাতে বেশি এক্সিম স্ক্রিপ থাকবে এবং তারা এটা নিয়ে অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে। সেই বাণিজ্যে ক্রমে ব্যাংক এবং অর্থলগ্নি সংস্থাগুলিও অংশগ্রহণ করতে পারবে। বর্তমানে ভারতীয় টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় (চলতি অ্যাকাউন্টে) সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরযোগ্য হওয়ায় এক্সিম স্ক্রিপ উঠে গেছে।
প্রশ্ন ৪১। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা কী ?
উত্তর।(১) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, (২) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, (৩) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, (৪) জাতীয় উৎপাদনের সুষ্ঠু বণ্টন, (৫) মূলধন সৃষ্টির হার বাড়ানো, (৬) কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ, (৭) বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন এবং (৮) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খুবই প্রয়োজন আছে।
প্রশ্ন ৪২। ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কিসের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরু আরোপ করা হয়েছিল ?
উত্তর। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কৃষি ও খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।
প্রশ্ন ৪৩। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কী কী ?
উত্তর। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল— (১) জাতীয় আরের বৃদ্ধি করা, (২) কৃষি ও শিল্পের সুখন উন্নয়ন করা, (৩) কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করা, (৪) দারিদ্র্য দূর করা (৫) জীবনমান উন্নয়ন করা এবং (৬) আর ও ঋণের বৈষম্য দূর করা যাতে দেশের অর্থনৈতিক শক্তির সমান ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন হয়।
প্রশ্ন ৪৪। প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকার কাকে বলে?
উত্তর। যদি এমন কখনও দেখা যায় যে একটি খামার থেকে বুজ বা শ্রমিক সরিয়ে আনলেও এবং মূলধন কাঠামো ও শ্রমিকের দক্ষতা অপরিবর্তিত থাকলেও সেই খামারের উৎপাদন মোটেই কমছে না, তবে বুঝতে হবে যে দুজন বা একজন শ্রমিকের খামারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে মোটেই কোন ভূমিকা নেই তখন এই জবা একজন শ্রমিককে আমরা প্রভাবে বেকার বা হাবেশী বেকার বলতে পার।
প্রশ্ন ৪৫। ভারতের বেকার সমস্যা সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য তিনটি উৎস কী ?
উত্তর। উৎসগুলি হল—(১) দশ বছর পর পর লোকগণনা, (২) জাতীয় নমুনা-সমীক্ষা এবং (৩) কর্ম-বিনিময় রেজিস্টার এবং কাজের সুযোগ সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ কর্মসূচি
প্রশ্ন ৪৬। মরশুমি বেকার অবস্থা কাকে বলে ?
উত্তর। অনেক সময় দেখা যায়, কোন কাজ শ্রমিকদের বছরের প্রায় কয়েকমাস করতে হয় না, যেমন কৃষিক্ষেত্র থেকে ফসল তোলার আগে কৃষি-শ্রমিকদের বছরে প্রায় তিনমাস কোন কাজ থাকে না, এই ধরনের বেকার অবস্থাকে মরশুমি বেকার অবস্থা বলা হয়।
প্রশ্ন ৪৭। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন এজেন্সি বলতে কী বোঝ?
উত্তর। এই প্রকল্পে দ্রুত অথচ সক্ষম কৃষকদের আর্থিক সাহায্যসহ উৎপাদনের উপাদান সংগ্রাহ করা এবং বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিয়ে নিবিড় চাষ করার কথা বলা হয়েছে।
প্রশ্ন ৪৮। প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষি শ্রমিক এজেন্সি কী?
উত্তর। এই কর্মসূচি অনুযায়ী প্রাপ্তিক কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকদের সংস্থাগত হন (institutional credit) অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, সমবায় সমিতি প্রভৃতি থেকে ঋণ প্রদান করে কহিতে উন্নতি কর চেষ্টা করা হয় যাতে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাজের সুযোগও বাড়ে।
প্রশ্ন ৪৯। শহর অঞ্চলে বেকার সমস্যা মোকাবিলার জন্য কী কী প্রকল্প প্রবর্তিত হয়েছে?
উত্তর। এক্ষেত্রে তিনটি প্রকল্প প্রণতিত হয়েছে—(১) শহর অঞ্চলের গরিবদের জন্য -নিয়োজিত কর্মসংস্থান (The Self Employment Programme for the Urban Poor or SEPLP) প্রবন্ধ; (২) শহর অঞ্চলের শিক্ষিত যুবকদের জন্য নিয়োজিত কর্ম (Scheme for Self Employment to Educated Urban Youth or SEEUY) এবং (৩)নেহেরু রোজগার যোজনা (Nehru Rozgar Yojana)। ১৯৯৭ সালে ডিসেম্বরে এই সব কটি প্রকল্প একত্রিত করে স্বর্ণজয়ন্তী শহর রোজগার প্রকল্প প্রবর্তিত হয়েছে।
প্রশ্ন ৫০। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির প্রধান কারণ কী ?
উত্তর। রপ্তানি অনুপাতে আমদানির অত্যধিক বৃদ্ধিই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির প্রধান কারণ ।
প্রশ্ন ৫১। ভারতে মুদ্রার সর্বশেষ অবমূল্যায়ন কবে এবং কত হয়েছে?
উত্তর। ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই ও ৩রা জুলাই এই দুদিনে ভারতীয় মুদ্রার ২০ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়।
প্রশ্ন ৫২। ভারত সাধারণত কী কী জিনিস বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে?
উত্তর। ভারত সাধারণত খাদ্যসামগ্রী, পেট্রোলিয়াম, কাঁচামাল, তুলো, ভোজ্য তেল ও ধাতব সামগ্রী, রাসায়নিক সামগ্রী, সার, মুক্তো, দামি পাথর, ওষুধ, সিনথেটিক কাপড়, অ-ধাতব খনিজ সামগ্রী, পোশাক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ঘড়ি, চোখ চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রভৃতি ৮০০ রকমের জিনিস আমদানি করে থাকে।
প্রশ্ন ৫৩। ভারতের প্রধান রপ্তানি সামগ্রীগুলি কী কী?
উত্তর। ভারতের প্রধান রপ্তানি সামগ্রীগুলি হল, ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী, রত্ন ও জুয়েলারি, পাট ও চটজাত দ্রব্য, চা, চিনি, সুতিবস্ত্র, সফটওয়্যার, কফি ও চামড়া।
প্রশ্ন ৫৪। ভারতের বৈদেশিক ঋণের উৎস কী কী?
উত্তর। ভারতের বৈদেশিক ঋণের উৎসগুলি হল, (১) আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি ;(২) রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি ; (৩) ভারত সাহায্য সংস্থা ; (৪) বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্র ; (৫) বৈদেশিক কোম্পানি; (৬) বৈদেশিক ব্যাংক ; (৭) বৈদেশিক সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা ; (৮) এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এবং (৯) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।
প্রশ্ন ৫৫। শর্তসাপেক্ষ বৈদেশিক ঋণ বলতে কী বোঝ?
উত্তর। শর্তসাপেক্ষ বৈদেশিক ঋণ একটি নির্দিষ্ট শর্তাধীনে (Tied) আবদ্ধ থাকে ; সাধারণত এই ঋণ হল প্রকল্পভিত্তিক।
প্রশ্ন ৫৬। আর্থিক ঘাটতি, বাজেট ঘাটতি এবং ঘাটতি অর্থসংস্থানের মধ্যে পার্থক্য কী ?
উত্তর। (১) আর্থিক ঘাটতি (Fiscal Deficit) = মোট সরকারি ব্যয় – (রাজস্ব প্রাপ্তি + ঋণ পরিশোধ বাবদ আদায় + সম্পদ বিক্রয় থেকে প্রাপ্তি)। (২) বাজেট ঘাটতি (Budgetary Deficit) = মোট সরকারি ব্যয় – মোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ট্রেজারি বিলের নিট বিক্রি বাদে)।(৩) ঘাটতি অর্থসংস্থান (Deficit Financing or Monetized Deficit) = বাজেট ঘাটতি দূর করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত ক্রেডিটের নিট বৃদ্ধি।
প্রশ্ন ৫৭। ভারতের নতুন অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য কী?
উত্তর।ভারতের নতুন অর্থনৈতিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল, অর্থনৈতিক কাঠামোর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বেড়াপাশ থেকে দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত করে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। এই নীতির অপর একটি উদ্দেশ্য হল, বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারত যাতে ■ প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
প্রশ্ন ৫৮। কাঠামোগত সামঞ্জস্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য কী?
উত্তর।কাঠামোগত সামঞ্জস্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং দেশের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের পণ্যসামগ্রীর বাজার আরও সম্প্রসারিত করতে পারে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ করে উৎপাদন শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।
প্রশ্ন ৫৯। জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিল কী ?
উত্তর। শিল্পক্ষেত্রে সরকারের বিদায়নীতির ফলে যারা কর্মচ্যুত হবেন অথবা কর্মকাল শেষ হবার আগেই অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, তাদের পুনর্বাসনের জন্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিল গঠিত হয়েছে।
প্রশ্ন ৬০। বাজার অর্থনীতি বলতে কী বোঝ ?
উত্তর। বাজার অর্থনীতি বলতে বোঝায় সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজারে চাহিদা ও বাজারের জোগানের অবাধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ ও ব্যবসায়িক নীতি নির্ধারণ। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাজার অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত সব ইউনিট সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করার এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণ করার সুযোগ পায় ।
প্রশ্ন ৬১। ভারতে রাজস্বের জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন্ করের উপর বেশি নির্ভর করা হয় ?
উত্তর। বর্তমানে ভারতে রাজস্বের জন্য প্রত্যক্ষ করের উপর বেশি নির্ভর করা হয়।
প্রশ্ন ৬২। ভারতের কয়েকটি প্রত্যক্ষ করের নামোল্লেখ কর ।
উত্তর। ভারতের কয়েকটি প্রত্যক্ষ কর হল, ব্যক্তিগত আয়কর, কোম্পানি কর, সম্পদ কর, বৃত্তি কর (রাজ্য সরকার কর্তৃক ধার্য করা হয়) এবং মূলধন মুনাফা কর।
প্রশ্ন ৬৩। ভারতের কয়েকটি পরোক্ষ করের নামোল্লেখ কর।
উত্তর। ভারতের কয়েকটি পরোক্ষ কর হল, বাণিজ্য শুল্ক, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, পরিষেবা কর, GST প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৬৪। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন কীভাবে হয়?
উত্তর। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি একটি ফিনান্স কমিশন নিয়োগ করেন এবং এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করা হয়।
প্রশ্ন ৬৫। সম্পদ করের ক্ষেত্রে করযোগ্য সম্পদ কত?
উত্তর। সম্পদ করের ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ টাকার সম্পদের উপর কর ধার্য করা হয়।
প্রশ্ন ৬৬। আয়করের ক্ষেত্রে ছাড়ের পরিমাণ কত ?
উত্তর। ২০১১-১২ সালের বাজেটের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে ছাড়ের পরিমাণ হল আবা পুরুষদের ক্ষেত্রে (প্রবীণ নাগরিক ব্যতীত) বার্ষিক ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, মহিলাদের ক্ষেত্রে বার্ষিক ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং প্রবীণ নাগরিকদের (senior citizens) ক্ষেত্রে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ৮০ বছর বয়স অথবা তার ঊর্ধ্বে খুব প্রবীণ নাগরিকদের (very senior citizens) ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়ের সীমা করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা।
প্রশ্ন ৬৭। রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রা প্রচলনের নিয়ম কী ?
উত্তর। রিজার্ভ ব্যাংককে মুদ্রা প্রচলন করার জন্য ২০০ কোটি টাকার রিজার্ভ রাখতে হয়,–এই ২০০ কোটি টাকার জন্য ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের সোনা এবং অবশিষ্ট ৮৫ কোটি টাকার সোনা অথবা বৈদেশিক মুদ্রা থাকবে।
প্রশ্ন ৬৮। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনটি?
উত্তর। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া।
প্রশ্ন ৬৯। ভারতে মোট কয়টি সরকারি ব্যাংক আছে?
উত্তর। বর্তমানে ভারতে সরকারি ব্যাংকের মোট সংখ্যা হল ২৭ ।
প্রশ্ন ৭০। ভারতের মুদ্রা সরবরাহে M, বলতে কী বোঝায়?
উত্তর। M, বলতে বোঝায় জনসাধারণের হাতে মোট অর্থের জোগান এবং ব্যাংকের দাবি | আমানত (Current and demand deposits)।
প্রশ্ন ৭১। মুদ্রা সরবরাহে M, বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। M, বলতে বোঝায় সামগ্রিক মুদ্রা বা আর্থিক সম্পদ (Aggregate Monetary Resources)। এগুলি হল,—(১) জনসাধারণের হাতে মুদ্রা, (২) ব্যাংকের হাতে দাবি আমানত, (৩) ব্যাংকের হাতে মেয়াদি আমানত, এবং (৪) রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে অন্যান্য আমানত।
প্রশ্ন ৭২। M, বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। M, বলতে বোঝায় M, + পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে জনসাধারণের জমানো টাকা।
প্রশ্ন ৭৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে বর্তমানে বিধিবদ্ধ নগদ রিজার্ভের কত অনুপাত রাখতে বেশ হয়?
উত্তর। বর্তমানে ব্যাংকগুলির অতিরিক্ত বর্ধিত আমানতের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নগদ রিজার্ভের অনুপাত বর্তমানে ২৪ শতাংশ।
প্রশ্ন ৭৪। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে বর্তমানে নগদ রিজার্ভের কত অনুপাত রাখতে হয় ?
উত্তর। ৬ শতাংশ (২০১০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে)।
প্রশ্ন ৭৫। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বর্তমান ব্যাংক রেট কত ?
উত্তর। ৬ শতাংশ।
প্রশ্ন ৭৬। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতির উদ্দেশ্য কী ?
উত্তর। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতির উদ্দেশ্য হল স্থিতিশীলতার সঙ্গে উন্নয়ন (Growth with stability) অর্জন করা ।
প্রশ্ন ৭৭। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কী ?
উত্তর।ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার একটি হল নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা (regulatory role) এবং অপরটি হল উন্নয়নমুখী ভূমিকা (Promotional role)।
প্রশ্ন ৭৮। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বলতে কী বোঝায়?
উত্তর। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বলতে বোঝায় পরিবহন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাস্তাঘাট, আবাসন ব্যবস্থা, জলসেচের ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প, গ্যাস সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা—যেগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে খুব জরুরি।
প্রশ্ন ৭৯। ভূমি সংস্কার কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্ত ?
উত্তর। ভূমি সংস্কার অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত (necessary condition), কিন্তু এটাই যথেষ্ট শর্ত ( sufficient condition) নয়।
প্রশ্ন ৮০। ঘাটতি ব্যয় কাকে বলে?
উত্তর। বাজেটের ঘাটতি মেটাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত নিট ব্যাংক ঋণ।
প্রশ্ন ৮১। ভারত সরকার বেশি রাজস্ব আদায় করে কোন্ দুটি কর থেকে?
উত্তর। (১) ব্যক্তিগত আয়কর এবং (২) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক থেকে।
প্রশ্ন ৮২। ভারতে ভূমি সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য কী ?
উত্তর। ভারতে ভূমি সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য হল, কৃষির উৎপাদন দক্ষতা (Productive efficiency) বাড়ানো এবং সামাজিক ন্যায় (Social justice) প্রতিষ্ঠা করা।
প্রশ্ন ৮৩। ভারতে কোন্ রাজ্যের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি?
উত্তর। ভারতে বর্তমানে গোয়া রাজ্যে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি।
প্রশ্ন ৮৪। ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান কত শতাংশ?
উত্তর। ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ২০০৯-১০ সালে ছিল ১৪.২ শতাংশ।
প্রশ্ন ৮৫। ‘খারিফ শস্য’ বলতে কী বোঝ ?
উত্তর। খারিফ শস্য বলতে বোঝায় মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর-নভেম্বর মাসের ভিতর চাল, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, আখ প্রভৃতি যেসব শস্য উৎপাদিত হয় সেগুলিকে।
প্রশ্ন ৮৬। কৃষি শ্রমিক কাকে বলে ?
উত্তর৷ জমির উপর মালিকানাহীন যেসব ব্যক্তি দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে জোতদারদের জমিতে কৃষিকাজ করে তাদের বলা হয় কৃষি শ্রমিক বা খেতমজুর।
প্রশ্ন ৮৭। রবিশস্য কাকে বলে ?
উত্তর।যেসব শস্য নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বপন করা হয় এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে জমি থেকে তোলা হয় তাদের বলা হয় রবিশস্য,–যেমন গম, ছোলা, সরষে, বার্লি, তিল প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৮৮। ভারতে জমির উপবিভাজনের কুফল কী কী ?
উত্তর।জমির উপবিভাজনের ফলে কৃষিক্ষেত্রের—(১) উৎপাদন শক্তি কমে যায়, (২) উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়, (৩) খণ্ডিত জমিগুলির আল বাঁধার জন্য কিছু জমি নষ্ট হয় এবং (৪) আর্থিক সমস্যা জটিল হয়।
প্রশ্ন ৮৯। ভারতে ব্যাংক জাতীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল ?
উত্তর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যাংক ঋণ যাতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রবাহিত হয়, ব্যাংক ব্যবস্থা যাতে দেশের সর্বত্র সম্প্রসারিত হয় এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বেকার যুবক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—তারা সবাই যাতে ব্যাংক ঋণের সুযোগ পায় এবং ব্যাংকগুলি যাতে নিজেদের মুনাফা সর্বাধিক না করে সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে নিজেদের কাজকর্ম পরিচালিত করে— ব্যাংক জাতীয়করণের এটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।
প্রশ্ন ৯০। কালো টাকা বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। হিসাব-বহির্ভূত যে টাকা আয়করের হিসাবে দেখানো হয় না, তাকেই বলা হয় কালো টাকা।
প্রশ্ন ৯১। ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক কখন স্থাপিত হয়?
উত্তর।১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক কাজ আরম্ভ করে। গোড়ায় এই ব্যাংক ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের সহযোগী হিসাবে কাজ করত। ১৯৭৬ সালে এই ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে আলাদা করা হয়।
প্রশ্ন ৯২। বেসরকারি শিল্পঋণ প্রদান করার জন্য ভারতের প্রথম উন্নয়ন ব্যাংক কোনটি এবং কত সালে এটা স্থাপিত হয় ?
উত্তর।বেসরকারি শিল্পে ঋণ প্রদান করার জন্য প্রথম উন্নয়ন ব্যাংক হল ভারতের শিল্প-ঋণ সরবরাহ করপোরেশন ; ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে স্থাপিত হয়।
প্রশ্ন ৯৩। ভারতে মুদ্রাস্ফীতির অন্তত চারটি কারণ উল্লেখ কর।
উত্তর।ভারতের মুদ্রাস্ফীতির চারটি অন্যতম কারণ হল—(১) বিপুল পরিমাণ ঘাটতি অর্থসংস্থানের দরুন মুদ্রা সরবরাহের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি, (২) প্রচুর পরিমাণ কালো টাকার প্রচলন, (৩) প্রশাসনিক নির্দেশে প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির মূল্যবৃদ্ধি, (৪) আমদানি খরচের বৃদ্ধি
প্রশ্ন ৯৪। সমান্তরাল অর্থনীতি বলতে কী বোঝ ?
উত্তর।হিসাব-বহির্ভূত যে টাকা আয়করের হিসাবে দেখানো হয় না তাকে বলা হয় কালো টাকা। জনসাধারণের আয় বেড়ে গেলে যদি কালো টাকার পরিমাণও বেড়ে যায় তবে সেটা বর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি করে এবং দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। দেশের ভিতর আয় উপার্জনকারীদের (যারা কর ফাঁকি দেন না) লেনদেনের পাশাপাশি কালো টাকার অধিকারীদের যে লেনদেন চলে, তাকে বলা হয় সমান্তরাল অর্থনীতি।
প্রশ্ন ৯৫। ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ কত ?
উত্তর।ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Survey) অনুযায়ী ২০১০ সালের ৩১শে মার্চ ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩৯৫৮১ কোটি টাকা।
প্রশ্ন ৯৬। বেসরকারি ক্ষেত্রে শিল্পগুলির দীর্ঘকালীন মূলধনের উৎস কী কী ?
উত্তর।বেসরকারি ক্ষেত্রে শিল্পগুলির দীর্ঘকালীন মূলধনের উৎসগুলি হল—(১) শেয়ার বিক্রয়, (২) ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বিক্রয়, (৩) জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ, (৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ, (৫) উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ এবং (৬) সরকারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ।
প্রশ্ন ৯৭। ভারতের সরকারি উদ্যোগগুলির লাভ কম হবার কারণ কী ?
উত্তর।ভারতের সরকারি উদ্যোগগুলির লাভ কম হবার কারণগুলি হল—উৎপাদন শক্তির সদ্ব্যবহার করতে না পারা, উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি, বিনিয়োগ আধিক্য, দুর্নীতি, ক্ষেত্রবিশেষে পরিচালনায় অদক্ষতা।
প্রশ্ন ৯৮। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা কী ?
উত্তর।সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচিকে (IRDP) পুনর্গঠন করে ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY) প্রবর্তিত হয়। গ্রামের গরিবদের স্ব-নিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে আয় বাড়ানোর জন্য ব্যাংক ঋণ ও ভরতুকির মাধ্যমে তাদের সম্পদ বাড়ানো এবং তাদের দারিদ্র্য সীমার উপরে নিয়ে আসা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচির ব্যয়ভার ৭৫ : ২৫ অনুপাতে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি বহন করে।
প্রশ্ন ৯৯। স্বর্ণজয়ন্তী শহরি রোজগার যোজনা (SJSRY) কী ?
উত্তর।শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য মোচনের জন্য শহর অঞ্চলে স্ব-নিয়োগ কর্মসূচি এবং মজুরিভিত্তিক কর্মনিয়োগের কর্মসূচি হল স্বর্ণজয়ন্তী শহরি রোজগার যোজনার প্রধান দুটি উপাদান। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে এই যোজনা প্রবর্তিত হয়।
প্রশ্ন ১০০। সবুজ বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ?
উত্তর।সবুজ বিপ্লবের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হল—(১) কৃষি-ব্যবস্থাকে বাজারমুখী করা, (২) উন্নত ধরনের উৎপাদন কৌশল প্রবর্তন করা, এবং (৩) নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগে উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেওয়া।
প্রশ্ন ১০১। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হয় এরকম দুটি করের নাম লেখ ৷
উত্তর। (১) ব্যক্তিগত আয়কর ও (২) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক।
প্রশ্ন ১০২। ঘাটতি বাজেট কাকে বলে ?
উত্তর। ঘাটতি বাজেট = মোট সরকারি ব্যয় – মোট সরকারি প্রাপ্তি (ট্রেজারি বিলের নিট বিক্রয় বাদে)।
প্রশ্ন ১০৩। ‘জোতের খণ্ডিকরণ’ বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর । যখন কৃষিজাত উত্তরাধিকারদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়, তখন ‘জোতের খণ্ডিকরণ’ হয়।
প্রশ্ন ১০৪। গুরুত্বপূর্ণ দুটি দারিদ্র্যবিরোধী কর্মসূচির নাম উল্লেখ কর।
উত্তর। (১) সর্বনিম্ন প্রয়োজন কর্মসূচি (Minimum Needs Programme), (২) জওহর রোজগার যোজনা।
প্রশ্ন ১০৫। ভারতে দারিদ্র্যসীমার নীচে আনুমানিক কত লোক বাস করে?
উত্তর। ২০১০-১১ সালে আনুমানিক ২৫ শতাংশ।
প্রশ্ন ১০৬। ব্যক্তিগত আয়কর ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি প্রত্যক্ষ করের নাম লেখ।
উত্তর। (১) কর্পোরেশন কর এবং (২) সম্পদ কর।
প্রশ্ন ১০৭। কর্পোরেশন কর’ বলতে কী বোঝ?
উত্তর। বিভিন্ন যৌথমূলধনি কোম্পানির আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয় সেটাই হল কর্পোরেশন কর।
প্রশ্ন ১০৮। নাবার্ডের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের নাম লেখ।
উত্তর। (১) কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ঋণ দেওয়া, এবং (২) জমি উন্নয়ন ব্যাংক, সিডিউল্ড বাণিজ্যিক ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক ও রাজ্য সমবায় ব্যাংককে পুনঃঋণের (refinance) নিশ্চয়তা প্রদান করা।
প্রশ্ন ১০৯। ‘সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর। সামাজিক নিরাপত্তা বলতে বোঝায়, এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে শ্রমিকদের বেকার অবস্থা, দুর্ঘটনা,বার্ধক্যজনিত কর্মক্ষমতার অভাব, অসুস্থতা এবং অন্যান্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা থাকে।
প্রশ্ন ১১০। শ্রমিক আন্দোলনের দুটি দুর্বলতা উল্লেখ কর।
উত্তর।(১) রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থে পরিচালিত হওয়া, (২) একই শিল্পে অনেকগুলি শ্রমিক সংঘ থাকায় পারস্পরিক রেষারেষি ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বাধার সৃষ্টি হওয়া।
প্রশ্ন ১১১। ‘আবশ্যিক সালিসি’ বলতে কী বোঝ?
উত্তর। শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাইরে থেকে আবশ্যিক মধ্যস্থতা অথবা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক (মালিক, শ্রমিক ও সরকার) করে আবশ্যিকভাবে সালিসি করা।
প্রশ্ন ১১২। বায়ু দূষণের দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ কর।
উত্তর। (১)মোটর গাড়ি বা বাস ও মিনিবাসের ইঞ্জিন থেকে অনবরত নিঃসৃত ডিজেল ও পেট্রোলের ধোঁয়া এবং (২) কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস।
প্রশ্ন ১১৩। ‘বদ্ধস্ফীতি’ কী ?
উত্তর।একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি এবং অপরদিকে শিল্পোৎপাদনে মন্দা (Stagnation), এই দুইয়ের সংমিশ্রণ হল বদ্ধস্ফীতি।
প্রশ্ন ১১৪। ভারতে শিল্পরুগ্নতার দুটি কারণ উল্লেখ কর।
উত্তর। (১) শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের জন্য চাহিদার হ্রাস হেতু শিল্পের বছরের পর বছর লোকসান। (২) শিল্প-বিরোধ হেতু উৎপাদন কাজ ব্যাহত হওয়া।
প্রশ্ন ১১৫। কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিকল্পনা-বহির্ভূত দুটি ব্যয়ের উদাহরণ দাও।
উত্তর। (১) সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ অর্থব্যয়, (২) ভরতুকি বাবদ ব্যয়।
প্রশ্ন ১১৬। ভারতের জাতীয় আয়ের আনুমানিক কত শতাংশ শিল্পের অবদান ?
উত্তর। ২০১০-১১ সালে ২২.৪ শতাংশ।
প্রশ্ন ১১৭। ভারতে মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অংশ কত?
উত্তর। ২০০৯-১০ সালে ভারতে মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অংশ হল ৫৮.৬ শতাংশ।
প্রশ্ন ১১৮। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা কী?
উত্তর। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার লক্ষ্য হল দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় ও এতনের সম্পদের অনুপাতে মুলধন গঠনের হার ও উন্নয়ন হারের স্বল্পতা, নীচুমানের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং বেকার সমস্য
প্রশ্ন ১১৯। স্থূল জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর। কোন নির্দিষ্ট বছরে নিদিষ্ট মূল্যস্তরের ভিত্তিতে দেশে উৎপাদিত মোট চূড়ান্ত সামগ্রী (Final Products) এবং মোট সেবাস্রোত বা পরিষেবার মূল্য হল স্কুল জাতীয় উৎপাদন।
প্রশ্ন ১২০। মাথাপিছু আয় কী?
উত্তর। কোন বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই বছরের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তা-ই হল মাথাপিছু আয়।
প্রশ্ন ১২১। উন্নয়ন হার বলতে কী বোঝ?
উত্তর। এক বছরের তুলনায় পরের বছর জাতীয় আয় যত শতাংশ বৃদ্ধি পায় ততটা হল উন্নয়ন হার
প্রশ্ন ১২২। আয় বণ্টনের বৈষম্য বলতে কী বোঝায়?
উত্তর। দেশে জাতীয় আয় বন্টনে একশ্রেণির লোক লাভবান বা ধনী হয় এবং অপর এক শ্রেণির লোক লাভবান হয় না ও কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এ ধরনের আয়ের কণ্টন হল আয় পল্টনের বৈষম্য।
প্রশ্ন ১২৩। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত গঠন কী ?
উত্তর। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত গঠন হল প্রাথমিক ক্ষেত্র (কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উৎপাদন), মাধ্যমিক ক্ষেত্র (শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন) এবং তৃতীয় ক্ষেত্র বা সেবাস্রোত ক্ষেত্র (পরিষেবা ক্ষেত্রে উৎপাদন)।
প্রশ্ন ১২৪। দারিদ্র্য রেখার সংজ্ঞা দাও।
উত্তর। দারিদ্র্যরেখা বলতে এমন একটি সীমারেখা ধরা হয় যার নীচে আয় থাকলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ক্যালরি, প্রোটিন ও ভিটামিনসম্মত খাদ্যসামগ্রী ভোগ করা সম্ভব হয় না।
প্রশ্ন ১২৫। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কী?
উত্তর। প্রতি দশকে আগের দশকের তুলনায় জনসংখ্যা যত শতাংশ বাড়ে ততটা হল জনসংখ্যার হার। যদি একে দশ দিয়ে ভাগ করা হয় তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার নিরূপিত হয়। প্রশ্ন ১২৬। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত? উত্তর। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হল ১৭.৬৪ শতাংশ।
প্রশ্ন ১২৭। জনসংখ্যার বসতি ঘনত্বের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর। প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় জনসংখ্যার বণ্টনকে বলা হয় বসতি ঘনত্ব।
প্রশ্ন ১২৮। স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। প্রতি এক হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যাকে বলা হয় স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত।
প্রশ্ন ১২৯।ভারতে সর্বশেষ লোকগণনায় (২০১১) স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত কত ছিল?
উত্তর। ২০১১ সালে প্রতি এক হাজার পুরুষের অনুপাতে মহিলার সংখ্যা ছিল ৯৪৩ জন।
প্রশ্ন ১৩০। পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। জন্মহার বৃদ্ধির পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণকে বলা হয় পরিবার পরিকল্পনা।
প্রশ্ন ১৩১। পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর।পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং পরিবারের সদস্যদের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো হল পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা।
প্রশ্ন ১৩২। ভূমিসংস্কার বলতে কী বোঝ?
উত্তর।ভূমিসংস্কার বলতে বোঝায় জমিতে মালিকানা ব্যবস্থার সংস্কার এবং সেই সঙ্গে যদি জমির উপর কৃষকদের মালিকানা না থাকে তবে জমির পুনর্বণ্টন করে তাদের মালিকানা প্রদান করা, প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, মধ্য স্বত্বাধিকারের বিলোপ করা এবং ভাগচাষিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।
প্রশ্ন ১৩৩। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি উচ্ছেদ কখন হয়েছিল ?
উত্তর। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ আইনের মাধ্যমে।
প্রশ্ন ১৩৪। জমির উপর ঊর্ধ্বতম সীমা কী ?
উত্তর। ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে একজন জমিদার বা জোতদার কতটা জমির উপর মালিকানা ভোগ করে তার একটি ঊর্ধ্বতম সীমা ধার্য করে দেওয়া হয়। এই ঊর্ধ্বতম সীমার উপর বাড়তি জমি সরকারের হাতে তুলে দিতে হয়।
প্রশ্ন ১৩৫। মধ্যস্বত্বাধিকারের বিলোপ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর। মধ্যস্বত্বাধিকারের বিলোপ কথাটার অর্থ হল প্রজাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা বা প্রজাস্বত্বের সংস্কার করা, যাতে সরকার ও প্রজাদের মধ্যে মধ্যস্বত্বাধিকারী হিসাবে কিছু সুবিধাভোগী লোক না থাকতে পারে।
প্রশ্ন ১৩৬। সমবায় খামার কাকে বলে ?
উত্তর।যখন কৃষকরা বিভিন্ন জমি একত্রিত করে যৌথ পরিচালনায় সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ করে তখন তাকে বলা হয় সমবায় খামার।
প্রশ্ন ১৩৭। সবুজ বিপ্লব কী ?
উত্তর।নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনের আশাতীত পরিমাণ বৃদ্ধি হল সবুজ বিপ্লব।
প্রশ্ন ১৩৮। উচ্চফলনশীল বীজ কী?
উত্তর। যে বীজ একর প্রতি জমিতে ভাল ফলন দেয় তাকে বলা হয় উচ্চফলনশীল বীজ প্রশ্ন
১৩৯। বাণিজ্যিক ব্যাংক জাতীয়করণ কখন হয়েছিল?
উত্তর। ১৯৫৫ সালে ইম্পেরিয়্যাল ব্যাংক জাতীয়করণ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয় । পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়।
প্রশ্ন ১৪০। গ্রামীণ ঋণের প্রধান উৎসগুলির নাম লেখ।
উত্তর।(১) গ্রাম্য মহাজন, (২) আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, (৩) কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাংক (NABARD) এবং (৪) গ্রামীণ সমবায় ঋণদান সমিতি।
প্রশ্ন ১৪১। কুটির শিল্পের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর।যখন শুধু একই পরিবারভুক্ত সদস্যরা সীমিত মূলধনের সাহায্যে কোন শিল্প পরিচালনা করে তখন তাকে বলা হয় কুটির শিল্প।
প্রশ্ন ১৪২। শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয় এরকম দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম লেখ।
উত্তর। (১) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (IDBI) এবং (২) ভারতের শিল্পঋণ সরবরাহ কর্পোরেশন (IFCI)।
প্রশ্ন ১৪৩। অর্থনৈতিক কেন্দ্রায়ন বলতে কী বোঝ ?
উত্তর। যখন দেশের অর্থনৈতিক শক্তি মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠী বা কয়েকজন শিল্পপতির অধিকারে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক কেন্দ্রায়ন।
প্রশ্ন ১৪৪। ভারতের শিল্পনীতি প্রথম কখন ঘোষিত হয়েছিল?
উত্তর। ১৯৪৮ সালে।
প্রশ্ন ১৪৫। ভারতে উদারীকরণ বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। ভারতে অর্থনৈতিক উদারীকরণ বলতে বোঝায় সরকারি ক্ষেত্রের সংকোচন, শিল্প বেসরকারিকরণ, শিল্প লাইসেন্সের যতটা সম্ভব অবসান, আমদানি শুল্কের ব্যাপক হ্রাস, বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আমন্ত্রণ ।
প্রশ্ন ১৪৬। শ্রমিক সংঘের সংজ্ঞা দাও ।
উত্তর।শ্রমিকরা যখন নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় করার জন্য ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংঘবদ্ধ হয় তখন তাদের সংঘকে বলা হয় শ্রমিক সংঘ।
প্রশ্ন ১৪৭। শ্রমিক সংঘের সংগ্রামী কাজ কী ?
উত্তর। দাবিদাওয়া আদায় ও অধিকার অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করা ও ধর্মঘট করা হল শ্রমিক সংঘের সংগ্রামী কাজ।
প্রশ্ন ১৪৮। শ্রমিক সংঘের সৌভ্রাতৃত্বমূলক কাজ কী ?
উত্তর। শ্রমিক সংঘ যখন তার অন্তর্ভুক্ত সদস্য ও শ্রমিক বন্ধুদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করে তখন সেটা হল সৌভ্রাত্রমূলক কাজ।
প্রশ্ন ১৪৯। শিল্প-বিরোধ বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। যখন মালিকপক্ষ ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, তখন তাকে বলে শিল্পবিরোধ।
প্রশ্ন ১৫০। শিল্প-বিরোধের নিষ্পত্তির পন্থাগুলি কী ?
উত্তর। (১) যৌথ দরকষাকষি, (২) সালিশি আলোচনা, (৩) আপস ব্যবস্থা, (৪) বাধ্যতামূলক বিচার ব্যবস্থা।
প্রশ্ন ১৫১। বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন বলতে কী বোঝায়?
উত্তর। আমদানি ও রপ্তানি হল বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন।
প্রশ্ন ১৫২। বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিপথ বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিপথ বলতে বোঝায় কোন্ কোন্ দেশে কী পরিমাণ রপ্তানি হচ্ছে এবং কোন্ কোন্ দেশ থেকে কী পরিমাণ আমদানি হচ্ছে।
প্রশ্ন ১৫৩। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী ?
উত্তর। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া।
প্রশ্ন ১৫৪। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কখন স্থাপিত হয়েছিল ?
উত্তর। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল (রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৪ অনুযায়ী) এবং ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল কাজ আরম্ভ করেছিল।
প্রশ্ন ১৫৫। রপ্তানি উন্নয়ন কী ?
উত্তর। রপ্তানি উন্নয়ন বলতে বোঝায় রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা।
প্রশ্ন ১৫৬। আমদানি নিয়ন্ত্রণ কী?
উত্তর। আমদানির পরিমাণ কমাবার জন্য আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা ও কোটার মাধ্যমে আমদানি সীমিত করে দেওয়া।
প্রশ্ন ১৫৭। মূল্যস্তর বৃদ্ধির ধারা কী ?
উত্তর। যখন দেশে মুদ্রাস্ফীতি হয় তখন বিভিন্ন ভোগসামগ্রীর জন্য চাহিদা তার জোগান অপেক্ষা বেশি থাকায় অথবা উৎপাদন-ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্তর বৃদ্ধির ধারা পরিলক্ষিত হয়।
প্রশ্ন ১৫৮। শিল্পক্ষেত্রে যৌথ ক্ষেত্র কী ?
উত্তর। যখন শিল্পক্ষেত্রে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে কোন শিল্প পরিচালিত
হয় তখন তাকে বলা হয় যৌথ ক্ষেত্ৰ ।
প্রশ্ন ১৫৯। ঘাটতি অর্থসংস্থান কী?
উত্তর।বাজেটে রাজস্ব অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ধরলে যে ঘাটতির সৃষ্টি হয় সেই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে নেওয়া নিট ক্রেডিট বা ঋণ।
প্রশ্ন ১৬০। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বলতে তুমি কী বোঝ ?
উত্তর।পরিকল্পিতভাবে দেশের উন্নয়ন হার বৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুষম ও ন্যায়সংগত বণ্টন হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।
প্রশ্ন ১৬১। ভারতে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কখন আরম্ভ হয়েছিল ?
উত্তর। ১৯৫১ সালে।
প্রশ্ন ১৬২। ভারতে এ পর্যন্ত কতগুলি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে?
উত্তর। ভারতে এ পর্যন্ত এগারোটি পাঁচসালা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।
প্রশ্ন ১৬৩। বাৎসরিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর। একটি আর্থিক বছরের জন্য পরিকল্পনা কর্মসূচি এবং তারজন্য ব্যয়বরাদ্দ হল বাৎসরিক পরিকল্পনা।
প্রশ্ন ১৬৪। ভারতীয় অর্থনীতিতে ‘দারিদ্র্য’ ধারণাটি বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর।১৯৭৯ সালে প্রকাশিত ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি Task Force-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু ২৪৩৩ ক্যালরি এবং শহরাঞ্চলে ২০৯৫ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু মাসিক ভোগজনিত ব্যয়ের মধ্যবর্তী বিন্দুকে (mid-point of a monthly per capita expenditure) দারিদ্র্য রেখা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর ভিত্তিতে ১৯৭৯- ৮০ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে গ্রামবাসীর যদি মাসে ৭৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলের অধিবাসীর যদি মাসে ৮৮ টাকা খরচ করার মতো ক্ষমতা না থাকে, তবে সে দরিদ্র্য।
প্রশ্ন ১৬৫। দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি কী?
উত্তর। দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি হল গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে যথাক্রমে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন পরিবেশ প্রকল্পের মাধ্যমে ও স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং গরিব জনসাধারণের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আবাসনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
প্রশ্ন ১৬৬। জমির উপবিভাজন ও অসংবদ্ধতা বলতে কী বোঝ?
উত্তর। যখন একটি জমি বিভিন্ন শরিকের মধ্যে ভাগাভাগি করা হয় তখন তাকে বলা হয় জমির উপবিভাজন (subdivision of landholding) এবং যখন গ্রামের ভিতর অথবা একাধিক গ্রামে কোনও কৃষকের জমি ছড়ানো অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলা হয় জমির অসংবদ্ধতা (fragmentation of lands)।
প্রশ্ন ১৬৭। বৈদেশিক মূলধন ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
উত্তর। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে যদি বিদেশ থেকে মূলধন আসে তবে সেটা বৈদেশিক মূলধন। কিন্তু যখন কোন দেশ লেনদেন ব্যালান্স ঘাটতি দূর করার জন্য অথবা কোন প্রকল্প তৈরির অর্থসরবরাহের জন্য বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তখন সেটা হল বৈদেশিক সাহায্য। বৈদেশিক সাহায্য অনুদান হিসাবেও আসতে পারে।
প্রশ্ন ১৬৮। তুমি কি মনে কর যে ভারত একটি অনগ্রসর দেশ ?
উত্তর। ভারত সাধারণভাবে একটি অনগ্রসর দেশ বটে, তবে অন্যান্য বহু অনগ্রসর দেশের তুলনায় ভারতের অনগ্রসরতা অনেক কম। ভারতকে একটি উন্নয়নশীল দেশ বলা যেতে পারে।
প্রশ্ন ১৬৯। অনগ্রসর দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ?
উত্তর। (ক) অনগ্রসর দেশগুলিতে দারিদ্র্যের তীব্রতা বেশি এবং মূলধন সৃষ্টির হার অপেক্ষাকৃত কম ; (খ) এই দেশগুলি মূলত কৃষিপ্ৰধান ; (গ) এই দেশগুলিতে বেকার সমস্যা তীব্র এবং গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয় ; (ঘ) এই দেশগুলিতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম এবং আয় বণ্টনে বৈষম্য থাকে ; (ঙ) অধিকাংশ অনগ্রসর দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি ; (চ) অধিকাংশ অনগ্রসর দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যেও বরাবর ঘাটতি দেখা যায়।
প্রশ্ন ১৭০। তুমি কি মনে কর যে ভারতে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ছে ?
উত্তর। ভারতে চলতি মূল্যের ভিত্তিতে মাথাপিছু আর্থিক আয় বাড়ছে; তবে সেই হারে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ছে না।
প্রশ্ন ১৭১। ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপ করার চারটি সমস্যার উল্লেখ কর।
উত্তর। ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের চারটি সমস্যা- (ক) ভারতে জনসাধারণের একটি বড় অংশকে আয়কর দিতে হয় না বলে জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না ; (খ) অনেকক্ষেত্রে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি আয়-ব্যয় এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব ঠিকমতো রাখে না অথবা হিসাবে কারচুপি করে ; সেক্ষেত্রে সঠিক আয়ের পরিমাপ করতে সমস্যার সৃষ্টি হয় ; (গ) যদি উৎপাদনব্যবস্থা পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে এবং উৎপাদনকারী যদি উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকাংশ ভোগ করে তবে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়;(ঘ) আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক শ্রমিক, বিশেষ করে কৃষি শ্রমিক আছে যাদের অর্থের মাধ্যমে মজুরি দেওয়া হয় না ;এ ধরনের অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্রে (non-monetized sector) জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
প্রশ্ন ১৭২। জাতীয় আয়ের বর্তমান ক্ষেত্রগত কাঠামো সম্পর্কে একটি ধারণা দাও ।
উত্তর। ভারতে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত কাঠামো ২০১০-১১ সালে ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) ১৪.২ শতাংশ প্রাথমিক ক্ষেত্রে, ২২.৪ শতাংশ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এবং ৬৩.৪ শতাংশ তৃতীয় ক্ষেত্রে বা পরিষেবা ক্ষেত্রে। ভারতের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ক্রমেই কমছে। মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং তৃতীয় ক্ষেত্রের অবদান দ্রুত বাড়ছে।
প্রশ্ন ১৭৩। ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলি কী কী ?
উত্তর।ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলি হল—(ক) প্রাপ্ত আয় পদ্ধতি, (খ) উৎপাদনের ও পণ্যের সংযোজিত মূল্যের (Value added) পরিসংখ্যান পদ্ধতি এবং (গ) সমীক্ষার মাধ্যমে ব্যয় সঞ্চয় পদ্ধতি।
প্রশ্ন ১৭৪। দারিদ্র্য বলতে কী বোঝ ?
উত্তর। দারিদ্র্য বলতে বোঝায় আয় এত কম যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরি ও ভিটামিনসম্পন্ন খাদ্য ক্রয় করা সংশ্লিষ্ট লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণভাবে দারিদ্র্যকে ‘আপেক্ষিক বঞ্চনা’ এবং স্বত্বাধিকার (entitlements) অর্জন করার ক্ষমতার অভাব হিসাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।
প্রশ্ন ১৭৫। দারিদ্র্যরেখা কী ?
উত্তর। দারিদ্র্যরেখা বলতে বোঝায়, আয় এবং প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও ভিটামিনসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের সামর্থ্যের ভিত্তিতে এমন একটি রেখা যার নীচে অবস্থিত লোকেরা গরিব, কারণ তাদের আয় কম ও তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও ভিটামিনসম্পন্ন খাদ্য ক্রয় করা সম্ভব নয়। এই রেখার উপর যারা আছে তাদের দারিদ্র্য বলে চিহ্নিত করা যায় না।
প্রশ্ন ১৭৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৬১ থেকে ১৯৭০, ১৯৭১ থেকে ১৯৮১, ১৯৮১ থেকে ১৯৯১, ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ এবং ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কী ছিল ?
উত্তর।১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৪.৮ শতাংশ। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৪.৭৫ শতাংশ, ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৩.৫ শতাংশ। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এবং ২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২১.৩৪ শতাংশ এবং ১৭.৬৪ শতাংশ।
প্রশ্ন ১৭৭। ভারতে পরিবার পরিকল্পনার কী উদ্দেশ্য।
উত্তর। ভারতে পরিবার পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং জনসংখ্যা সীমিত করা।তাছাড়া পরিবার কল্যাণের জন্য এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্ত্রীলোক ও পুরুষদের সচেতনতা | বাড়িয়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।
প্রশ্ন ১৭৮। প্রজাস্বত্ব সংস্কার বলতে তুমি কী বোঝ ?
উত্তর জমির মধ্যস্বত্বাধিকার দূর করে প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা ও তাদের জমির মালিকানা জমি ভোগের অধিকার দেওয়া হল প্রজাস্বত্ব সংস্কার।
প্রশ্ন ১৭৯। ভারতে জোতের ক্ষুদ্রাকারের চারটি কারণ উল্লেখ কর।
উত্তর।ভারতে কৃষিজোতের ক্ষুদ্র আকার হবার কারণ হল—(১) কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ ও উত্তরাধিকার আইনের ফলে জমির উপবিভাজন, (২) যৌথ পরিবার প্রথায় ভাঙ্গন হবার দরুন জমির উপবিভাজন, (৩) কুটির শিল্পের অবনতি হবার সঙ্গে জমির উপর চাপ বাড়ছে এবং বড় জোতগুলি ভেঙে ছোট জোত তৈরি হচ্ছে অথবা বড় জোতের কিছু অংশ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ও ছোট জোতে পরিণত হচ্ছে, (৪) গ্রামীণ ঋণের বোঝা ও মহাজনদের কাছে ঋণ পরিশোধের চাপে অনেক কৃষক খণ্ড খণ্ড করে জোতের কিছু অংশ বিক্রি করে।
প্রশ্ন ১৮০। NABARD কখন এবং কেন সৃষ্টি হয়েছিল ?
উত্তর। কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাংক বা NABARD কাজ আরম্ভ করে ১৯৮২ সালের ১২ই জুলাই ।এই ব্যাংক হল কৃষিক্ষেত্রে অর্থ অথবা ঋণ সরবরাহের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংকের প্রধান কাজ হল ব্যাংকগুলিকে পুনঃঋণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কারিগর, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত কাজের জন্য ঋণ সরবরাহ করা। এই ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার ঋণ দিয়ে থাকে। সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের প্রধান উৎস হল এই ব্যাংক।
প্রশ্ন ১৮১। শিল্প লাইসেন্স নীতি বলতে কী বোঝ?
উত্তর। শিল্পগুলি যাতে শুধু মুনাফা অর্জনের জন্য যথেচ্ছভাবে নিজেদের সম্প্রসারণ করতে না পারে এবং দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ উপেক্ষা করে আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থা চালাতে অথবা অভ্যন্তরীণ ব্যবসা চালাতে না পারে সেজন্য তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার শিল্প লাইসেন্স নীতি প্রবর্তন করে থাকে।
প্রশ্ন ১৮২। শিল্প-বিরোধ বলতে তুমি কী বোঝ ?
উত্তর। শিল্প-বিরোধ বলতে বোঝায় শিল্পে মালিক ও শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ। মজুরি হার নির্ধারণ, শ্রমিকদের ছুটি, অবসর ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মনিয়োগ, শ্রমিক ছাঁটাই প্রভৃতি ক্ষেত্রে দাবি-দাওয়া নিয়ে যখন শিল্প-মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় শিল্প-বিরোধ।
প্রশ্ন ১৮৩। ভারতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ কী কী ?
উত্তর। ভারতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণগুলি হল—(১) সরকারের অতিরিক্ত বাজেট ঘাটতির জন্য অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ এবং তার ফলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ও ভোগ্যপণ্যের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি –অথচ চাহিদা অনুযায়ী জোগানের স্বল্পতা, (২) মজুরি বৃদ্ধি ও আমদানি খরচের বৃদ্ধি হেতু উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, (৩) কালো টাকার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় একশ্রেণির লোকের হাতে, বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের হাতে, অতিরিক্ত ক্রয়শক্তি থাকায় ভোগসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি, (৪) সরকার-নির্দেশিত শিল্পক্ষেত্রে কাঁচামালের আপেক্ষিক জোগান কম হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং (৭) পরিবহন খরচের মূল্যের (Administered price) বৃদ্ধি—সাধারণত ভরতুকি কমাবার ক্ষেত্রে এটা হয়, (৫) বৃদ্ধি; এটা মূল্যস্তরে প্রতিফলিত হয়।
প্রশ্ন ১৮৪। পাঁচসালা পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ?
উত্তর। সরকার যখন পাঁচ বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট আর্থিক সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং সেই পাঁচ বছরের মধ্যেই পরিকল্পিতভাবে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদন লক্ষ্য পূরণ করার চেষ্টা করে, তখন তাকে বলা হয় পাঁচসালা পরিকল্পনা। এই পরিকল্পিত কর্মসূচিতে আর্থিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে উৎপাদন লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ও তা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়।
প্রশ্ন ১৮৫। পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তত দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ কর।
উত্তর। পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তত দুটি উদ্দেশ্য হল—(১) দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং (২) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরশীলতা (self-reliance) অর্জন করা।
প্রশ্ন ১৮৬। ঘাটতি অর্থসংস্থান কাকে বলে ?
উত্তর। বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি (ট্রেজারি বিলের নিট বিক্রি বাদে) থেকে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে বাজেট ঘাটতির সৃষ্টি হয়,—এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য যখন সরকারকে অর্থসংস্থান করতে হয় তখন তাকে বলা হয় ঘাটতি অর্থসংস্থান। এই অর্থসংস্থানের জন্য সরকার প্রধানত রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে,—অর্থাৎ নোট ছেপে মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে বাজেট ঘাটতির অর্থসংস্থান করে থাকে। অবশ্য সরকার সাধারণভাবে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে এবং জনসাধারণের কাছে সিকিউরিটি বা বন্ড বিক্রি করেও ঘাটতি অর্থসংস্থান করতে পারে। সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণ করার জন্য নিট ব্যাংক ক্রেডিট হল ‘ঘাটতি অর্থসংস্থান’।
প্রশ্ন ১৮৭। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক মূলধনের মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে তা পরিশোধ করার দায়- দায়িত্ব থাকে না যেহেতু এটা ঋণ নয় ; কিন্তু বৈদেশিক মূলধন যদি ঋণ হিসাবে গৃহীত হয়, তবে সেটা পরিশোধ করার দায়-দায়িত্ব থাকে। বৈদেশিক মূলধন অনুদান হিসাবেও আসতে পারে, সেক্ষেত্রে এটা পরিশোধ করার প্রশ্ন আসে না।
প্রশ্ন ১৮৮। প্রজাস্বত্ব সংস্কার বলতে কী বোঝ?
উত্তর। প্রজাস্বত্ব সংস্কার হল জমিতে প্রজাদের (tenants) স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাতে সরকার ও প্রজার মধ্যে মধ্যস্বত্বাধিকারী হিসাবে কিছু সুবিধাভোগী লোক না থাকতে পারে।