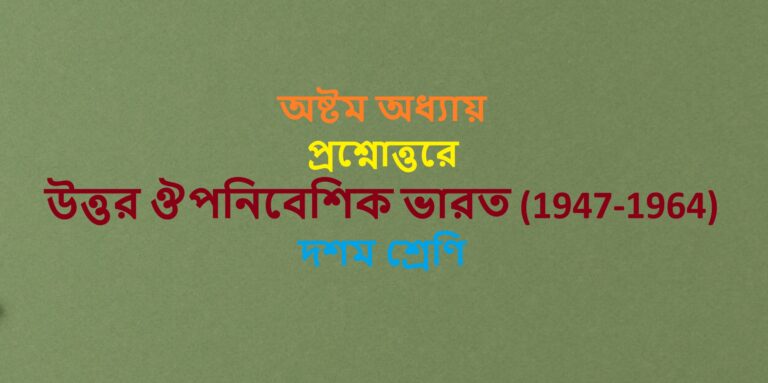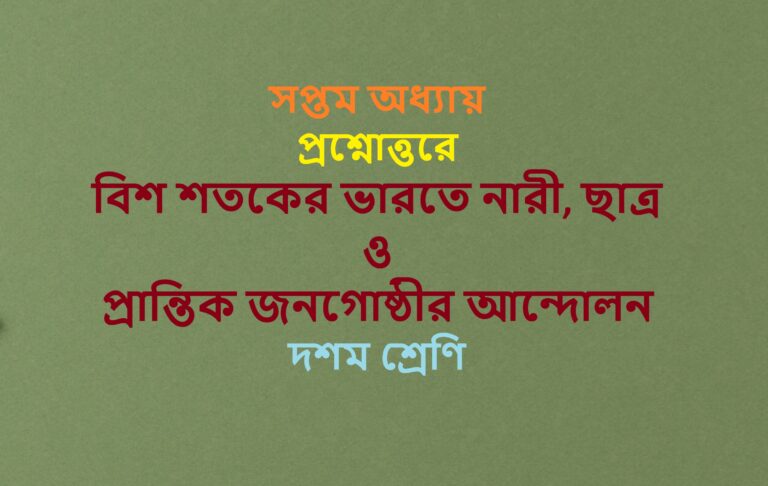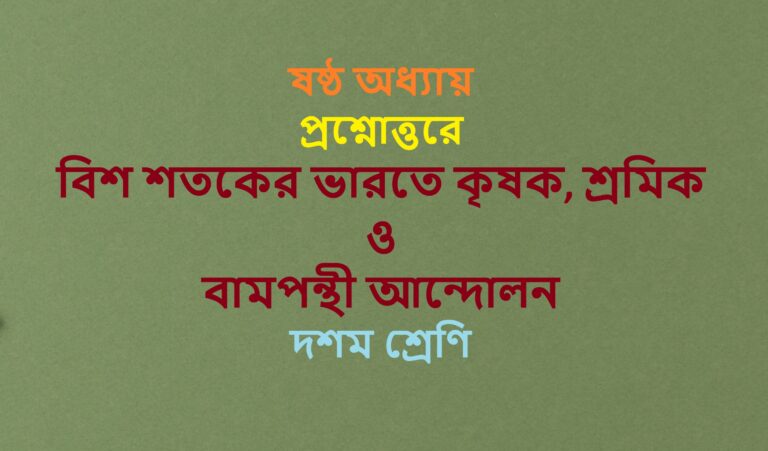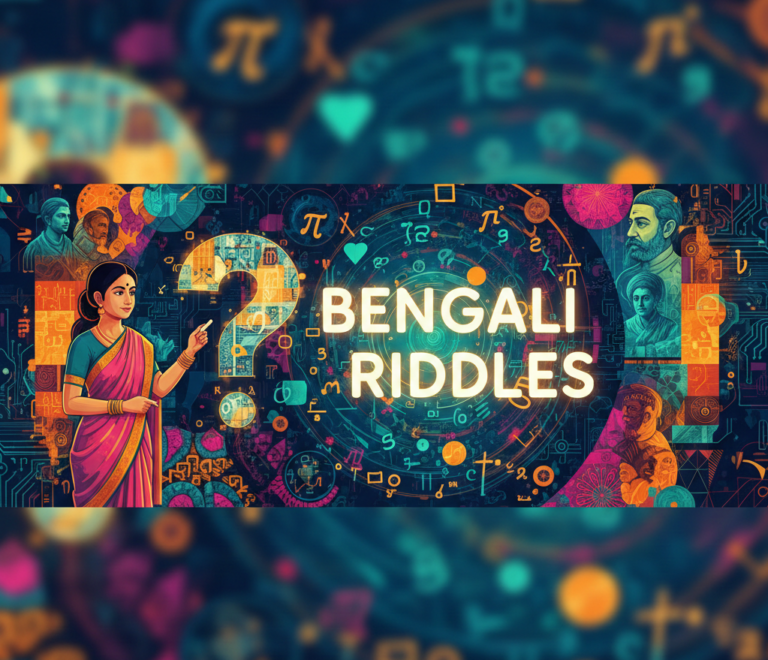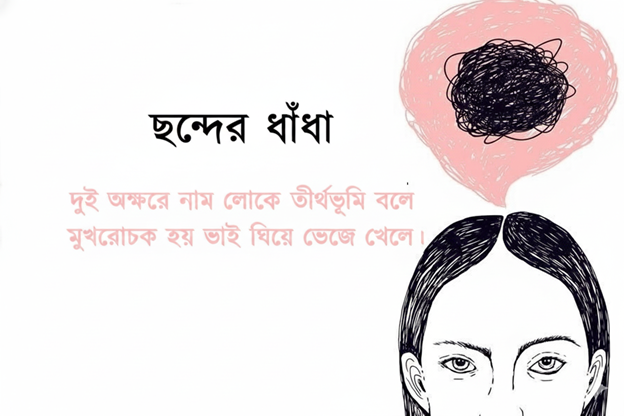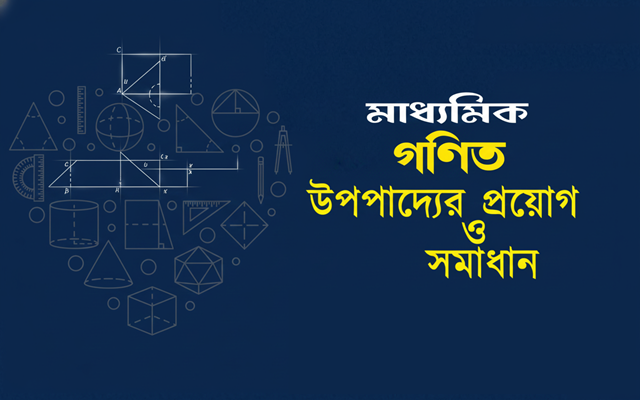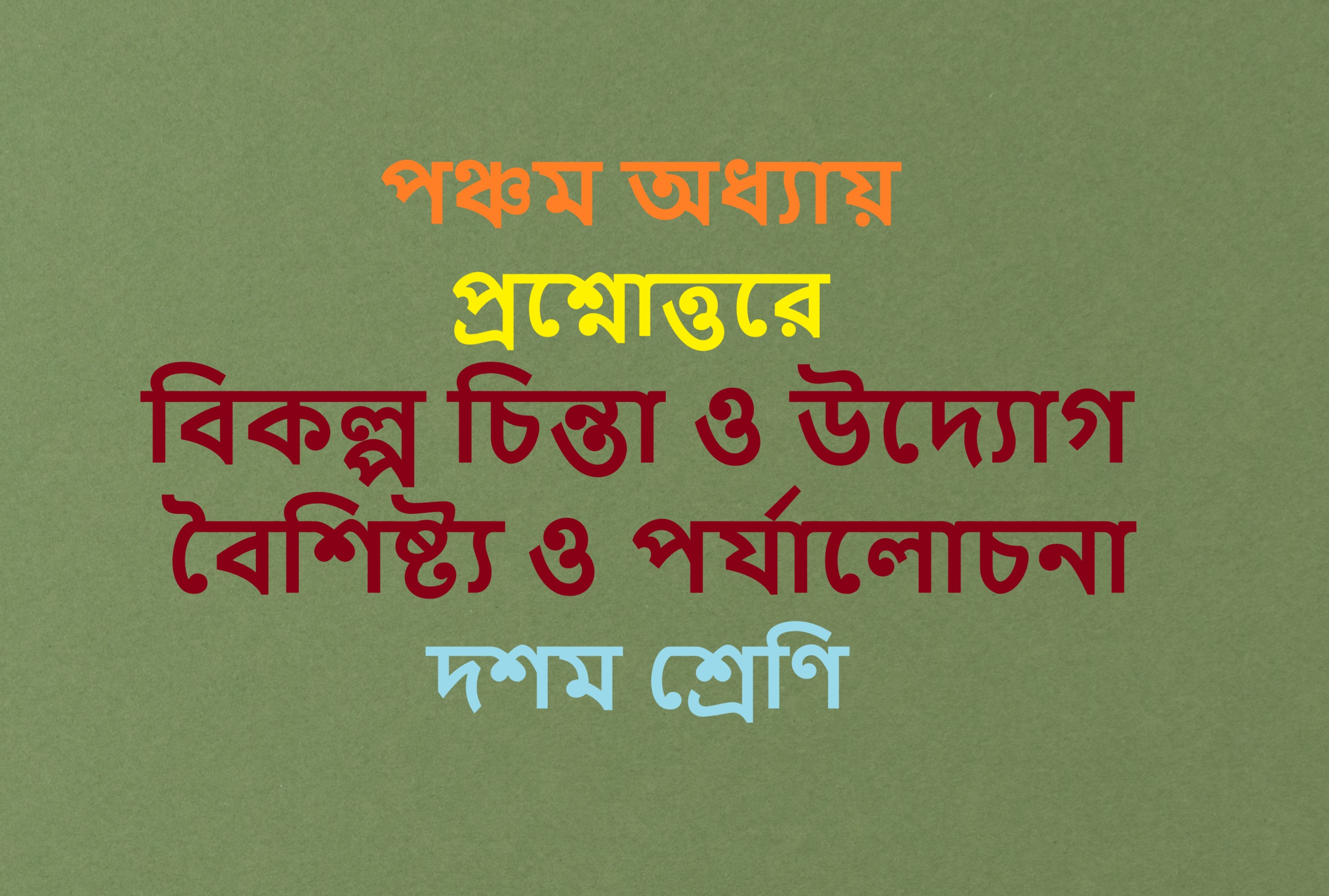
Bikalpa-cinta-o-udyog-Baisistya-o-paryalocana
বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা
Bikalpa-cinta-o-udyog-Baisistya-o-paryalocana
অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম চিত্রিত গ্রন্থের নাম কী ?
উত্তর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’।
কে বর্ণপরিচয় রচনা করেন ?
উত্তর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট–এর প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন?
উত্তর প্রমথনাথ বসু ।
‘সংবাদ প্রভাকর‘-এর সম্পাদকের নাম কী ?
উত্তর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
‘A Grammar of the Bengal Language’ কার লেখা ?
উত্তর ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড–এর লেখা।
কত খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হয় ?
উত্তর 1800 খ্রিস্টাব্দে।
‘প্রতাপাদিত্য চরিত্র‘ কে রচনা করেন?
উত্তর রামরাম বসু ।
ভারতে প্রথম কোথায় ছাপাখানা শুরু হয় ?
উত্তর গোয়ায়।
ছাপাখানার জনক কাকে বলা হয়?
উত্তর জোহানেস গুটেনবার্গকে।
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম কী ?
উত্তর ‘সমাচার দর্পণ‘।
বাংলা ছাপাখানার অগ্রপথিক কাকে বলা হয় ?
উত্তর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে।
ভারতে ‘হাফটোন’ প্রিন্টিং কে প্রবর্তন করেন?
উত্তর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
‘গোলদিঘির গোলামখানা‘ কাকে বলা হয় ?
উত্তর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে।
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
উনিশ শতকের শিক্ষার বিকাশে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স–এর ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর ড. মহেন্দ্রলাল সরকার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানকে সাধারণ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার মান উন্নত করা।
বিশ্বভারতী‘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল ?
উত্তর প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘বিশ্বভারতী’ গড়ে তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে ‘বিশ্বভারতী’ গড়ে উঠুক। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার পরিণত রূপ হলো ‘বিশ্বভারতী‘র প্রতিষ্ঠা।
বাংলা ছাপাখানার বিকাশে পঞ্চানন কর্মকারের ভূমিকা কী ছিল ?
উত্তর পঞ্চানন কর্মকার ধাতুর ওপর নকশা খোদাই–এর জীবিকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ছেনি দিয়ে কাটা বাংলা হরফ তৈরি করেন । এই হরফেই ‘হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ‘ মুদ্রিত হয়।
বাংলার মুদ্রণের ইতিহাসে বটতলা প্রকাশনার গুরুত্ব কী ?
উত্তর উনিশ শতকে কলকাতার চোরাবাগান, শোভাবাজার, দর্জিপাড়া, জোড়াসাঁকো প্রভৃতি স্থানে যেসব প্রকাশনা চলত তা বটতলা প্রকাশনা নামে পরিচিত। দেশি পেপারের ব্যবহার এবং স্বদেশি কারিগরির মুন্সিয়ানা দ্বারা বটতলা প্রকাশনী থেকে খুবই সস্তায় বই প্রকাশিত হতো। সমসাময়িক বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনা তুলে ধরা হতো। বিভিন্ন রসাত্মক কথাযুক্ত বই ছাপা ছিল এখানকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
চার্লস উইলকিন্স কে ছিলেন?
উত্তর চার্লস উইলকিন্স ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে রাইটার হিসেবে যোগদান করেছিলেন। বাংলা মুভেবল টাইপ বা বিচল হরফের আবিষ্কর্তা হিসেবে চার্লস উইলকিসের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত।
বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ছাপাখানা বিকাশের ভূমিকা কতটা ?
উত্তর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় স্থাপিত একাধিক ছাপাখানা সমগ্র বাংলায় শিক্ষাপ্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এইসব ছাপাখানায় স্কুল ও কলেজের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ছাপা হতো। বাংলায় ছাপাখানার বিকাশ কিছু মুক্তচিন্তকের উত্থানে অবদান রাখে যাঁরা সাময়িক ও সংবাদপত্রে তাদের মতামত লিখতেন।
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল কেন?
উত্তর ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। বিভিন্ন দিক থেকে এর সীমাবদ্ধতা ছিল, যেমন—এই শিক্ষা ছিল ইংরেজি ভাষায়, তাই সকল ভারতীয়ের কাছে এই শিক্ষাগ্রহণ একপ্রকার ভীতির সঞ্চার করেছিল। এই শিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করা হয়। এই শিক্ষা মানুষের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে।
বাংলা ছাপাখানা বিকাশে লাইনোটাইপ প্রবর্তনের গুরুত্ব কী ?
উত্তর বাংলায় মুদ্রণশিল্পের প্রসারে পঞ্চানন কর্মকারের নাম স্মরণীয়। তিনি ছাপাশিল্পে বাংলা হরফের প্রচলনের পরে সুরেশচন্দ্র মজুমদার লাইনোটাইপ নামে আরও উন্নত বেঙ্গলি হরফ তৈরি করেন। ফলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সর্বোপরি বাংলা জনমানসে তথা ছাপাখানা শিল্পে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে।
বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ছাপাখানার বিকাশের ভূমিকা কতটা?
উত্তর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় স্থাপিত একাধিক ছাপাখানা সমগ্র বাংলায় শিক্ষাপ্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এইসব ছাপাখানায় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছাপা হতো। বাংলায় ছাপাখানার বিকাশ কিছু মুক্তচিন্তকের উত্থানে অবদান রাখে যাঁরা সাময়িক ও সংবাদপত্রে তাঁদের মতামত লিখতেন।
ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার স্মরণীয় কেন ?
উত্তর তিনি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স‘-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 1876 সালে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পরামর্শে সরকার মেয়েদের বিবাহের বয়স ন্যূনপক্ষে 16 বছর নির্ধারণ করেছিল।
পঞ্চানন কর্মকার কেন বিখ্যাত ?
উত্তর পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরির ক্ষেত্রে চার্লস উইলকিন্স–এর সহযোগী। ইস্পাতের পাতের ওপর বাংলা অক্ষর এঁকে ছাচ কেটে ধাতুনির্মিত অক্ষরকে লেখার কাজে তিনি এক উইলকিন্সকে সাহায্য করেন। তাঁর তৈরি মুদ্রাক্ষর হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণে ও কর্নওয়ালিশ কোডের বাংলা সংস্করণে ব্যবহার করা হয়।
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ কী ছিল ?
উত্তর রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিক শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেন। চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষাকে আবদ্ধ না রেখে খোলা আকাশের নীচে বা গাছতলে শিক্ষাদান ও ব্রহ্মচর্য পালন এই শিক্ষাদর্শনের বৈশিষ্ট্য ছিল। শিক্ষার স্বাভাবিক বিকাশ রবীন্দ্রনাথের কর শিক্ষাদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল।
ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের সম্পর্ক কী ছিল?
উত্তর ছাপাখানা উদ্ভবের আগে শিক্ষাব্যবস্থা মূলত হাতে লেখা পুথি বা মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ছাপা বইয়ের সহজলভ্যতার ফলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞান অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পরিবেশনের কাজ শুরু হয়।
ওষুধ শিল্পের জনক কাকে বলা হয় ? তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর ওষুধ শিল্পের জনক বলা হয় বিখ্যাত রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেন।
কারা শ্রীরামপুর ত্রয়ী‘ নামে পরিচিত ছিলেন ?
উত্তর শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড ‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী‘ নামে পরিচিত ছিলেন।
কবে, কোথায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় ?
উত্তর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 1906 খ্রিস্টাব্দের 12 মার্চ 92 জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়।
কার উদ্যোগে, কবে ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট‘ প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তর আইনজীবী ও শিক্ষাদরদি তারকনাথ পালিত 1906 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট‘ প্রতিষ্ঠা করেন।
শ্রীনিকেতন কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
উত্তর গ্রামীণ সমাজকে স্বনির্ভর করতে ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন কালীমোহন ঘোষ।
প্রসেস প্রিন্টিং কী ?
উত্তর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছাপাখানার বিশেষ কৃতিত্ব হলো প্রসেস প্রিন্টিং। এটি হলো একধরনের উন্নত মুদ্রণ কৌশল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর ইউ রায় অ্যান্ড সন্স নামে ছাপাখানায় নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে এই উন্নত কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন।
বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসারে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স‘-এর ভূমিকা কী ছিল ?
উত্তর বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসারে এর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, দান উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণায় সহায়তা করা এবং ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার স্পৃহা জাগিয়ে তোলা ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।
ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রটি কে আবিষ্কার করেন? যন্ত্রটির কাজ কী ?
উত্তর ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন জগদীশচন্দ্র বসু।
এই যন্ত্র অতিসামান্য বৃদ্ধিকে একশো গুণ বড়ো করে দেখাতে পারে।
‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম‘ কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1901 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম‘ প্রতিষ্ঠা করেন।
কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ‘ কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ‘কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ‘ 1914 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন।
হিকির ছাপাখানা বিখ্যাত কেন?
উত্তর জেমস অগাস্টাস হিকি বাংলার রাজধানী কলকাতায় 1777 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানায় সংবাদপত্র ছাপা ও প্রকাশনার কাজ করা হতো। এছাড়াও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বিল ছাপা হতো।
‘বসু বিজ্ঞান মন্দির‘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল ?
উত্তর জগদীশচন্দ্রের মতে, এটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও জ্ঞানের প্রসার, বিজ্ঞানের সুফল সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া এবং বিজ্ঞানের প্রগতি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি।
ভারতে সর্বপ্রথম কবে, কারা, কোথায় আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ?
উত্তর ভারতে সর্বপ্রথম 1556 খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজরা গোয়ায় আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।
বাংলার প্রথম সংবাদপত্র কোনটি? এর প্রকাশক কে ছিলেন?
উত্তর বাংলার প্রথম সংবাদপত্রটি ছিল ‘বেঙ্গল গেজেট’। এই সংবাদপত্রের প্রকাশক ছিলেন জেমস অগাস্টাস হিকি।
বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর
বাংলার ছাপাখানা বিকাশে U. Ray & Sons-এর অবদান কতখানি ছিল ?
অথবা, বাংলার মুদ্রণশিল্পের প্রসারে U. Ray & Sons-এর ভূমিকা লেখো।
উত্তর
সূচনাঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তথা বিশ শতকের প্রথম দশকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশুসাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর আর–এক বড়ো পরিচয় হলো তিনি বইপ্রকাশনা সংস্থারও প্রধান ছিলেন।
OU. Ray & Sons-এর বৈশিষ্ট্যঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সাহিত্যসাধনার পাশাপাশি মুদ্রাকর হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বই ছাপার জন্য 1895 খ্রিস্টাব্দে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম U. Ray & Sons.
প্রসেসবিদ্যাঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন হাফটোন ব্লক ব্যবহারের পথিকৃৎ। তিনি কাঠের ব্লক তৈরি করে ‘ছেলেদের রামায়ণ‘ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। হাফটোন ব্লকের সাথে রঙিন ব্লকও তিনি তৈরি করেন যা প্রসেসবিদ্যার উন্নতি ঘটায়। ফলে মুদ্রণজগতে বিরাট পরিবর্তন আসে।
কারিগরি প্রতিভাঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর উদ্ভাবনী ভাবনা ও কারিগরি দক্ষতার বিষয়টি যেমন দেশে খ্যাতিলাভ করে তেমনি বিদেশেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে তিনি যেসকল পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা হলো 60 স্প্রিন টিন্ট প্রসেস পদ, ডায়োটাইপ স্প্রিন হ্যাডজস্টার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। এগুলি ছিল তাঁর অসীম প্রতিভার উদাহরণ।
পুনর্গঠনঃ উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায় ফোটোগ্রাফি এবং প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে যান। শিক্ষাগ্রহণের শেষে তিনি দেশে ফিরে এসে পারিবারিক ছাপাখানার আমূল পরিবর্তন করেন। এরপর গড়ফা রোডে U. Ray & Sons-এর পুনর্গঠন করেন।
প্রকাশনাঃ বাংলার ছাপাখানা শিল্পের বিকাশে তথা শিক্ষার প্রসারে এই ছাপাখানার অবদান অনস্বীকার্য। বাণিজ্যিক বিভিন্ন কাজের সাথে সাথে নিজস্ব প্রকাশনার কাজও করে চলে এই সংস্থা। এখান থেকেই প্রকাশিত হয় ‘ছেলেদের মহাভারত’, ‘টুনটুনির বই’, ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন‘ প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ ।
মূল্যায়নঃ কেবলমাত্র ব্যবসায়িক মুনাফার উদ্দেশ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেননি। ছাপার প্রযুক্তি ও রঙিন ছবির ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক অবদান রাখেন, সাথে সাহিত্যসাধনাও চালিয়ে যান। নিজের লেখা গ্রন্থগুলিও প্রকাশ করেন এখান থেকে। ছাপার পদ্ধতিগুলিতে তাঁর বিভিন্ন কৃতিত্বের জন্য ‘Ray Screen Adjuster’ পদ্ধতির কথাও জানা
যায়।
কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বাংলায় ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের কী ভূমিকা ছিল?
অথবা, বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশে B.T.I.-এর অবদান লেখো । অথবা, টীকা লেখো – B.T.I
সূচনাঃ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশি উদ্যোগে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের যে উদ্যোগ শুরু হয়, সেই উদ্যোগের প্রতি বাঙালিদের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং তার বিস্তারে অনন্য ভূমিকা নিয়েছিল ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট‘।
প্রতিষ্ঠাঃ তারকনাথ পালিত–এর প্রচেষ্টায় 1906 খ্রিস্টাব্দের 25 জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় “বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট‘। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে তারকনাথ পালিত প্রায় 4 লক্ষ টাকা উৎসর্গ করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে।
উদ্দেশ্যঃ প্রাচ্য রীতি ও আদর্শের ওপর ভর করে শিক্ষাদানে উদ্যোগী হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। এখানে যন্ত্রবিজ্ঞান, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ফলিত রসায়ন, ভূবিদ্যা, শিল্পপ্রযুক্তির সাথে কলা বিভাগেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূললক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করা।
সমন্বয়সাধনঃ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রথমে কারিগরি শিক্ষাদান দিয়ে শুরু হলেও খুব অল্পসময়ে ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট‘ এবং ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ’ একত্রে মিশে যায়। 1928 খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নাম হয় ‘কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি‘।
মূল্যায়নঃ ঔপনিবেশিক শাসনকালে যাঁরা জাতীয় শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল BTI. 1925 সালের মধ্যে এখান থেকে বছরে গড়ে প্রায় একশো জন করে সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হন যাঁরা দেশের কারিগরি শিক্ষার বিকাশে নিয়োজিত হয়েছিলেন।
ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।
উত্তর
সূচনাঃ যেকোনো সময়ে যেকোনো দেশের শিক্ষার অগ্রগতি ঘটাতে যেমন উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন হয় পাঠ্যপুস্তক। আর এই পাঠ্যপুস্তক জোগান দেবার জন্য প্রয়োজন ছাপাখানা। উনিশ শতকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত বহু ছাপাখানা শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।
বই ও শিক্ষার নিবিড় সম্পর্কঃ ছাপা বই–এর সমাহার একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে, ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীর কাছে প্রয়োজন মেটায় শিক্ষার উপাদানের। তাই বলা যায়, ছাপা বই এবং শিক্ষার বিস্তার পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।
সহজলভ্যতাঃ অল্প সময়ে ও অল্প খরচে বইয়ের জোগান পেতে ছাপা বই–এর বিকল্প নেই। তাই ছাপা বইয়ের সহজলভ্যতা শিক্ষাবিস্তারে সহায়ক।
লেখার স্পষ্টতাঃ যেকোনো লেখা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য ছাপা বই–এর বিকল্প নেই। পরিষ্কার ও স্পষ্ট লেখা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে।
শিক্ষার বিস্তারঃ ছাপা বই উনিশ শতকে ব্যাপক হারে বিস্তারলাভ করলে সারাদেশে একই ধরনের শিক্ষার বিস্তারে তা সহায়ক হয়ে ওঠে যা সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সমতা এনেছিল।
মূল্যায়ন : ঊনবিংশ শতকে গড়ে ওঠা ‘শ্রীরামপুর মিশন প্রেস’, ‘ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি সহ বহু প্রতিষ্ঠানে ছাপানো বই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। একারণে বলা যায়, ছাপা বই–এর সাথে শিক্ষাবিস্তারের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।
বাংলায় মুদ্রণশিল্পের বিকাশে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের কীরূপ অবদান ছিল?
উত্তর
সূচনাঃ বাংলায় ছাপাখানা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাকেন্দ্রিক বইব্যাবসার সূত্রপাত ঘটে। প্রথম বাঙালি মুদ্রাকর ও বইবিক্রেতা ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। 1818 খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ব্যবসায়িক লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন বাঙ্গাল গেজেট প্রেস।
কম্পোজিটার হিসেবে গঙ্গাকিশোরের অবদানঃ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের প্রেসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য একজন কম্পোজিটার হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তীতে মিশনারিদের সাথে পারস্পরিক মতানৈক্যর কারণে তিনি শ্রীরামপুর মিশন ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন।
গঙ্গাকিশোরের অবদানঃ বাংলার মুদ্রণশিল্পে একজন কম্পোজিটার হিসেবে গঙ্গাকিশোরের অবদান কম নয়। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ ছিল প্রথম ছবিওয়ালা বাংলা বই ।
মুদ্রাকরঃ তিনি অনেকগুলি গ্রন্থরচনা করেন, পুস্তকব্যাবসার সাথে নিজে জড়িত থেকে বাংলায় মুদ্রণ ব্যাবসাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যান। মুদ্রণ ও প্রকাশনায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।
মূল্যায়নঃ দীর্ঘ জীবন কলকাতায় অতিবাহিত করার পর গঙ্গাকিশোর নিজ গ্রামে ফিরে যান এবং সেখান থেকেই তিনি মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যান। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি একাধারে মুদ্রণ ব্যবসায়ী, প্রকাশক, পুস্তক ব্যবসায়ী ও সর্বোপরি একজন গ্রন্থকার এবং সাংবাদিক।
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কীভাবে একটি অগ্রণী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো ?
অথবা, বাংলার মুদ্রণশিল্পে শ্রীরামপুর ছাপাখানার অবদান উল্লেখ করো।
অথবা, বই ছাপানোর ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান আলোচনা করো।
উত্তরঃ জেসুইট মিশনারি কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে 1800 খ্রিস্টাব্দে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন যা সেইসময় এশিয়ার সর্ববৃহৎ ছাপাখানারূপে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। এই ছাপাখানার দ্বারা বাংলার মুদ্রণশিল্পে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়।
অনুবাদ সাহিত্যঃ শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে ভারতীয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল অনূদিত হয়ে ছাপা হতে থাকে।
পাঠ্যপুস্তকঃ এই ছাপাখানা থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক, অন্যান্য বিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যপুস্তক প্রভূত পরিমাণে ছাপা হতে থাকে।
পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রঃ শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে রামরাম বসুর ‘প্রতাপাদিত্য চরিত্র‘ এবং মার্শম্যান সম্পাদিত ‘দিগ্দর্শন‘ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।
শিক্ষায় ভূমিকাঃ শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা থেকে প্রচুর পাঠ্যপুস্তক ছাপা হতে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীদের হাতে খুব সহজে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে যেতে থাকে। দরিদ্র শিক্ষার্থীরাও শিক্ষালাভের সুযোগ পায় ।
বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার বিকাশে ড. মহেন্দ্রলাল সরকারের কীরূপ ভূমিকা ছিল ?
অথবা, টীকা লেখো : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স‘।
অথবা, IACS-এর প্রতিষ্ঠা এবং বাংলায় আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করো।
অথবা, কীভাবে IACS প্রতিষ্ঠিত হয় তা ব্যাখ্যা করো।
উত্তর
সূচনাঃ উনিশ শতকের ভারতে সরকারি উদ্যোগে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ঘটলেও তা ছিল অপ্রতুল। তাই বাঙালি তথা ভারতীয়রা নিজ উদ্যোগে বিজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রসর হয়। এই ধরনেরই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ড. মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণার স্বার্থে 1876 সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘Indian Association for the Cultivation of Science.”
প্রতিষ্ঠানঃ ড. মহেন্দ্রলাল সরকার লন্ডনের ‘রয়্যাল ইনস্টিটিউট‘ এবং ‘ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স‘-এর অনুকরণে একটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্ৰ প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেন। অবশেষে ফাদার ইউজিন লাফোঁ–এর সহযোগিতায় 1876 খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বৌবাজারে প্রতিষ্ঠা করেন IACS.
উদ্দেশ্যঃ এই গবেষণা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমত, বিজ্ঞানের প্রসারসাধন ও প্রকৃত গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞান গবেষণার পরিধির বিস্তার ঘটানো। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে গবেষণা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।
গবেষণাঃ এই প্রতিষ্ঠানটিতে দেশবিদেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।
গবেষণাপত্রঃ বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণামূলক কাজগুলি প্রকাশের জন্য এই প্রতিষ্ঠান থেকে “ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স‘ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।
যুক্তিবাদের প্রসারঃ ড. সরকার ছিলেন প্রকৃত অর্থেই বিজ্ঞানপ্রেমী। বাঙালিকে অন্ধবিশ্বাসের বদলে যুক্তিবাদের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি।
মন্তব্যঃ IACS প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান জনপ্রিয় হয়েছিল। বিখ্যাত গবেষক জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সি.ভি. রমন, মেঘনাদ সাহা, কে এস কৃষ্ণান ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ।
বাংলায় মুদ্রণের ব্যবসায়িক উদ্যোগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
উত্তর
ভূমিকাঃ ছপাখানা প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরে বাংলায় শিক্ষাপ্রসারের কারণে মুদ্রণশিল্পের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এজন্য বাংলায় নতুন নতুন ছাপাখানা গড়ে উঠল। একশ্রেণির শিক্ষিত বাঙালি মুদ্রণশিল্পকে পেশা হিসেবে বাছতে উদ্যোগী হয়।
ছাপাখানার ব্যবসায়িক উদ্যোগ
অনারেবল কোম্পানিজ প্রেসঃ 1781 সালে উইলকিনস কলকাতায় অনারেবল কোম্পানিজ প্রেস গড়ে তোলেন। এটি ছিল কলকাতার সবথেকে ব্যস্ত ছাপাখানা।
শ্রীরামপুর মিশন প্রেসঃ 1800 সালে শ্রীরামপুরে কেরি, মার্শ ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপন করেন। এটি ছিল এশিয়ার বৃহত্তম ছাপাখানা ৷
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যঃ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথম বাঙালি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা। প্রথম সচিত্র বাংলা বই ‘অন্নদামঙ্গল’ তিনি প্রকাশ করেন।
ইস্টার্নহোপ প্রেসঃ 1840 সালে ঈশ্বরীপ্রসাদ বসু এটি স্থাপন করেন। এখান থেকে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা‘ ছাপা হতো ।
গুপ্ত প্রেসঃ 1861 সালে দুর্গাচরণ গুপ্ত প্রতিষ্ঠা করেন গুপ্ত প্রেস। এখানে ছাপা পঞ্জিকা আজও সকলের ঘরে ঘরে সমাদৃত।
বি. পি. এমস প্রেসঃ বরদাপ্রসাদ মজুমদার গড়ে তোলেন এই ছাপাখানা । তিনি জমিদারি ছেড়ে দিয়ে ‘নোটবই’–এর ব্যাবসা শুরু করেন। এ ছাড়াও মুদ্রণশিল্পে অন্য বাঙালিদের মধ্যে বেণীমাধব দে, মথুরানাথ তর্করত্ন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।
ছাপাখানা বাংলার শিক্ষাবিস্তারে কীরূপ পরিবর্তন এনেছিল ?
উত্তর
সূচনাঃ ছাপাখানার প্রচলনের ফলে শিক্ষার বিস্তার ক্রমশ সহজ থেকে সহজতর হয়ে উঠেছিল একথা বলা যায়। চলমান হরফের প্রচলন ও মুদ্রণবিপ্লব সারাবিশ্বের জ্ঞানচর্চাকে উচ্চশ্রেণির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসারিত করেছিল। ভারত তথা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ সর্বোপরি গণশিক্ষার প্রসারে ছাপাখানা ও স্থাপ বই–এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
শিক্ষার বিস্তারে ছাপাখানার ভূমিকা
শিক্ষার প্রসারেঃ কেবলমাত্র বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে মুদ্রির সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর প্রচুর ছাপা বই বাজারে আসে। ছাপা বইপত্রগুলি পুস্তকের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিক্ষাদান উচ্চবিত্তদের মধ্যে দাম সস্তা হওয়ায় সেগুলি আপামর মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়। রেভারেন্ড জেমস লঙ–এর মতে, মুদ্রণ ও শিক্ষার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
শ্রীরামপুর ছাপাখানার ভূমিকাঃ এদেশের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা ছিল শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারি উইলিয়াম কেরি কর্তৃক 1800 খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপন। এখান থেকে বাংলা, হিন্দি, অসমিয়া, ওড়িয়া, মারাঠি, সংস্কৃত সহ 16 ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত সহ বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ, হিতোপদেশ, বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রভৃতি এখান থেকে ছাপা হয় ।
কলকাতার ছাপাখানার ভূমিকাঃ কলকাতায় 1801-32 সালের মধ্যে বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে 40টি ভাষায় 2 লক্ষেরও বেশি বই ছাপা হয়। এইসময় থেকে শ্রীরামপুর ছাপাখানার মার্শম্যান সম্পাদিত মাসিক ‘দিগ্দর্শন‘ এবং সাপ্তাহিক ‘সমাচার দর্পণ’; কলকাতা থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘বেঙ্গল গেজেট‘ সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশের ফলে
জনশিক্ষার প্রসার ঘটে।
মূল্যায়নঃছাপাখানা শিশুশিক্ষার অগ্রগতিতেও সহায়তা করেছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার–এর ‘শিশুশিক্ষা’, বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’, রামসুন্দর বসাকের ‘বাল্যশিক্ষা’, প্রাণলাল চক্রবর্তীর ‘অঙ্কবোধ’, গোবিন্দপ্রসাদ দাসের ‘ব্যাকরণ সার’, আনন্দকিশোর সেনের ‘অর্থের সার্থকতা’ বাল্য ও শিশুশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সর্বোপরি বলা যায়, ছাপাখানা একদিকে যেমন শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক সহায়ক ছিল, তেমনি শিল্প তথা ব্যাবসারও উন্নতি ঘটিয়েছিল।
‘বসু বিজ্ঞান মন্দির‘ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো ।
অথবা, টীকা লেখো— ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির‘।
উত্তর
সূচনাঃ পরাধীন ভারতে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষে তথা বাংলায় বিজ্ঞানের গবেষণা তথা বিজ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশের উদ্দেশ্যে যেসকল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির‘ বা ‘বোস ইনস্টিটিউট‘ যা ছিল সমকালীন বিশ্বের একটি প্রথম সারির বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান।
প্রেক্ষাপটঃ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে ছিলেন অতিজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির‘ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন।
বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা ও সার্বিক চর্চার জন্য 1917 খ্রিস্টাব্দের 30 নভেম্বর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ বা ‘বোস ইনস্টিটিউট‘। এই প্রতিষ্ঠানের উদবোধন অনুষ্ঠানে ‘দ্য ভয়েস অব লাইফ‘ শিরোনামে স্বাগত ভাষণে জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠানটিকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।
উদ্দেশ্যঃ এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন—এটির উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও জ্ঞানের প্রসার ঘটানো। তিনি চাইতেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আবিষ্কারের সুফল যেন সকল শ্রেণির মানুষ পায় ।
মূল্যায়নঃ ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির‘ ভারতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশ্বমানের গবেষণার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে বলেছেন, “আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যেসকল অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যেকোনোটির জন্যে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।”
টীকা লেখো-‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ‘।
অথবা, ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ–এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব লেখো।
উত্তর
সূচনাঃ 1905 খ্রিস্টাব্দের 16 অক্টোবর লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হলে সমগ্র বাংলাজুড়ে শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের অঙ্গ বয়কটের প্রস্তাব অনুসারে বিদেশি শিক্ষাগ্রহণে ছাত্রসমাজ বিরত থাকতে শুরু করে। এর পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে স্বদেশি শিক্ষাপ্রসারের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।’
উদ্দেশ্যঃ ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ‘ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি শিক্ষানীতির ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করে দেশীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যার প্রসার ঘটিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের আদর্শ জাগ্রত করা এবং নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
মনীষীদের অংশগ্রহণঃজাতীয় শিক্ষা পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার কাজে বিভিন্ন মনীষী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ বসু, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ।
গুরুত্বঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম গুরুত্ব ছিল এর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়—‘বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ’ এবং ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট‘। এ ছাড়া বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। পরিষদের উদ্যোগেই 1908 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 25টি মাধ্যমিক এবং 300টিরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
মূল্যায়নঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা ছিল স্বদেশি আন্দোলনের বৃহৎ গঠনমূলক প্রচেষ্টা। ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদই বাংলা তথা ভারতে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থাকে বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।
কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ সম্পর্কে টীকা লেখো।
অথবা, বিজ্ঞানচর্চায় কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ভূমিকা কী ছিল ?
অথবা, বিজ্ঞানশিক্ষার বিকাশে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের উৎকর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করো।
উত্তর
সূচনাঃ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকালে ভারতীয়রা বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করায় বিকল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে একদিকে গড়ে উঠেছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এবং অন্যদিকে স্বদেশি বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ। 1914 খ্রিস্টাব্দের 27 মার্চ শিক্ষাদরদি দুই ব্যক্তিত্ব তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বিজ্ঞান কলেজ। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ।
উদ্দেশ্যঃ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উনিশ শতকের বাংলায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা এবং বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটানো। আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ভূমিকা ছিল এইরকমঃ
খ্যাতনামা শিক্ষার্থীঃ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের তৎকালীন কিছু শিক্ষার্থী এই কলেজে বিজ্ঞানসাধনা করে খ্যাতিলাভ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।
খ্যাতনামা শিক্ষকঃ তৎকালীন সময়ে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদান করেন বহু খ্যাতনামা শিক্ষক ও বিজ্ঞানী, যেমন–আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটারমন, শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ। এই খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ হয়ে ওঠে বিশ্বমানের শিক্ষাকেন্দ্র।
মূল্যায়নঃ পরে ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও দেশ গঠনে এই কলেজের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।
রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর
বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। অথবা, বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার সূচনাপর্ব বিশ্লেষণ করো।
অথবা, বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো । অথবা, বাংলায় বিজ্ঞানচর্চায় কোন কোন বাঙালি, কীভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তা আলোচনা করো।
উত্তর
সূচনাঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় শিক্ষাপ্রসারের যে জোয়ার এসেছিল তার প্রভাব লক্ষ করা যায় বিভিন্ন দিকে। এইসময় আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিকাশ লক্ষ করা যায়। দেশীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক অনুপ্রবেশে বাংলা তথা ভারতে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তার উত্তাল হিল্লোলে বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা বিকশিত হয়ে ওঠে।
কারিগরি শিক্ষার বিকাশে মনীষীদের ভূমিকাঃ উনিশ শতকে বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে যেসকল মনীষী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাধাগোবিন্দ কর, মহেন্দ্রলাল সরকার, নীলরতন সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানঃ বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
নিয়েছিল, যেমন—
সরকারি উদ্যোগঃ ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন, কলকাতা মাদ্রাসা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেছিল।
IACS: মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রচেষ্টায় 1876 খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে ‘Indian Association for the Cultivation of Science.’ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলির গবেষণা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই গবেষণাগারের অন্যতম ফলাফল ছিল বিজ্ঞানী C.V. Raman কর্তৃক ‘রামন প্রভাব‘-এর আবিষ্কার ।
কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ : 1914 খ্রিস্টাব্দে তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ‘। স্নাতকোত্তর স্তরে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ বিশেষ পঠনপাঠন সহ উচ্চতর গবেষণার সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।
বসু বিজ্ঞান মন্দিরঃ 1917 খ্রিস্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানের গবেষণা ও বিজ্ঞানচর্চার জন্য গড়ে তোলেন ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির‘। পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণায় এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।
BTI : 1906 সালে কলকাতায় ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট‘ নামে একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যা 1955 খ্রিস্টাব্দে ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে’ পরিণত হয়।
মূল্যায়নঃ উপরিউক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে উনিশ শতকে বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশে যেমন একদিকে বিভিন্ন মনীষী গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন, ঠিক তেমনি বাংলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাচিন্তা ও শান্তিনিকেতন ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীর আদর্শ ও উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করো।
অথবা, বিশ্বভারতী সম্পর্কে টীকা লেখো।
উত্তর
সূচনাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্জনে ধর্মীয় চর্চার উদ্দেশ্যে (MP 2020) ভুবনডাঙায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি এর নাম দেন শান্তিনিকেতন। পরবর্তীতে 1921 খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানেই প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী যা বিশ্বজাতির মহামিলনের ক্ষেত্রে পরিণত হয় ।
ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ 1901 খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার আদর্শঃ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা–তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন——যত্র বিশ্বম ভবত্যেকণীড়ম‘ অর্থাৎ যেখানে বিশ্ব একটি নীড়ে পরিণত হবে। এই আদর্শের ভিত্তিতে 1921 খ্রিস্টাব্দের 23 ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়।
শিক্ষাপদ্ধতিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির প্রাথমিক প্রয়োগ হয় ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল আশ্রমিক গুরুকুল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকত না।
বিশ্বভারতীর উদ্যোগ: বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ) শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতীর বিভিন্ন শাখা বা অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলি হলো পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, এ ছাড়াও ছিল কলাভবন ও সংগীতভবন। ) শ্রীনিকেতন—শান্তিনিকেতনের পাশে অবস্থিত যেখানে কৃষি, পল্লি সংগঠন ভবন ও শিল্পভবনের দ্বারা গ্রামোন্নয়ন ও কিশোর–যুবকদের উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সংগঠিত হতো। ০ পঠনপাঠনে বিশ্বভারতীর উদ্যোগ: রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে চিন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে এসে বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এখানে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল গৈরিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলামিক ও পাশ্চাত্যের
জ্ঞান সংবলিত পাঠ্য।
মন্তব্য: রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করতে • চেয়েছিলেন। 1951 খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদালাভ করে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রথম উপাচার্য হন। তাঁর আদর্শ ও উদ্যোগ আজও অম্লান।
হ্যালহেডের ‘এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ‘ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? বাংলা ছাপাখানার বিকাশে চার্লস উইলকিনস–এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর
সূচনাঃ বাংলা ভাষার বিকাশে একটি স্মরণীয় নাম হলো হ্যালহেড। বাংলা ভাষায় গদ্যরূপ নির্মাণে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছিল ‘A Grammar of the Bengal Language’ | 1778 সালে ব্রিটিশ কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে তিনি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছিলেন, যা ছিল বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ বই। অন্যদিকে বাংলা সচল হরফের আবিষ্কার করায় চার্লস উইলকিনস ছিলেন বাংলা মুদ্রণজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।
বাংলা ছাপাখানার জগতে এই গ্রন্থের ভূমিকা
প্রথমতঃ ‘এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ‘ গ্রন্থটি মূলত ইংরেজি ভাষায় লেখা হলেও এতে বহু অক্ষর, বাক্যাংশ, শ্লোক সহ পদ্যাংশ ছাপা হয়েছিল বাংলা হরফে। এই গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠার চারভাগের একভাগ অংশে উদাহরণরূপে বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল। আর এভাবেই বাংলা মুদ্রণ তথা ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল।
দ্বিতীয়তঃ হ্যালহেড রচিত এই বইটিতে বাংলা মুদ্রণে কাঠের ব্লকের পরিবর্তে সর্বপ্রথম সচল হরফ বা এককথায় বলতে গেলে ‘মুভএবল হরফ‘-এর ব্যবহার করা হয়েছিল। আর এই পদ্ধতি বাংলা ছাপাখানার জগতে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল।
বাংলা ছাপাখানার বিকাশে চার্লস উইলকিনস–এর ভূমিকা
বাংলা হরফ নির্মাণঃ উইলকিনস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে 1770 খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। বাংলা মুদ্রণশিল্পের জনক হলেন চার্লস উইলকিনস, তিনি বিলেত থেকে বাংলা অক্ষর তৈরির কৌশল রপ্ত করেন। উইলকিনস প্রথম ধাতুনির্মিত সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফ–এর সৃষ্টিকর্তা। এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেন পঞ্চানন কর্মকার।
হেস্টিংসের নির্দেশঃ কোম্পানি সরকার রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে হ্যালহেড রচিত বাংলা ব্যাকরণটি ছাপানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করলে, তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সিভিলিয়ান এবং বিশিষ্ট বাংলা ও পণ্ডিত চার্লস উইলকিনসকে দায়িত্ব দেন। উইলকিনস–এর তত্ত্বাবধানে বাংলা হরফের আবিষ্কার বাঙালির নবজাগরণের প্রথম সূত্রপাত বলা যেতে পারে।
উইলকিনস–এর গ্রন্থপ্রকাশঃ 1778 খ্রিস্টাব্দে উইলকিনস কোম্পানির ছাপাখানার শিক্ষার্থী প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। চার্লস উইলকিনস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকার–এর সাহায্যে ছেনি কাটা বাংলা হরফ তৈরি করে অ্যানড্রুজের ছাপাখানা থেকে 1778 সালে ‘এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ‘ প্রকাশ করেন। উইলকিনস–এর দক্ষতা ও নিপুণতায় বাংলা ভাষায় প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়।
মূল্যায়নঃ একাধারে বাংলার শিক্ষার বিস্তার ও বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিকাশে তাই হ্যালহেড এবং চার্লস উইলকিনস–এর নাম ভারতীয়দের কাছে চিরস্মরণীয়।
মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। অথবা, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর
সূচনাঃ 1935 খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে মেকলে মিনিট–এর মাধ্যমে ভারতের ব্রিটিশশাসিত অঞ্চলে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী করেন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও রীতিনীতির বাস্তবে কোনো মিল না থাকায় ত বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। এই সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এই শিক্ষাব্যবস্থার একজন তীব্র সমালোচক ছিলেন।
ঔপনিবেশিক শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিঃ
যান্ত্রিকতাঃ রবীন্দ্রনাথের মতে তৎকালীন ভারতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রাণের যোগ ছিল না
তাঁর মতে এই ধরনের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নিষ্ক্রিয় যন্ত্রে পরিণত করে।
একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষাঃ রবীন্দ্রনাথের মতে এটা ছিল একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালা ব্যাপার দেশের সব শিক্ষারীতিকে এক ছাঁচে শক্ত করে জমিয়ে দেওয়া হবে, যাতে দেশবাসীর বুদ্ধিবৃত্তি ওপর সম্পূর্ণ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।
জাতীয়তাবিরোধীঃ এই শিক্ষা জাতীয়তাবিরোধী। কারণ এটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শে অনুসরণ ও ধার করা বিদ্যার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এখানে যা শিখানো হয় তাতে বুলিপড়া গতানুগতিক দল সৃষ্টি হয় এবং তারা হয় বিদেশের বুলি মুখস্থ করা খাঁচার পাখি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শান্তিনিকেতনঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপরিউক্তভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি শিক্ষাদর্শনের পরিকল্পনা করেছেন এবং তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিংহের কাছ থেকে যে 20 বিঘা জমি কিনেছিলেন সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ তিনি বলতেন, শিক্ষক শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞান | বিতরণ করবেন আর শিক্ষার্থী শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে তিনি গুরু ও শিষ্যের | মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।
প্রথমত, তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের ওপর জোর দিয়েছিলেন। | সেখানে তিনি বিভিন্ন উৎসব পালন করার ব্যবস্থাও করেন। তিনি বলতেন যে এসবের মাধ্যমে | শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে।
দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন যে পূর্ব ও পশ্চিম–এর চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা = করে তাকে বিশ্বজাতির মিলনভূমিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বভারতীতে বিশ্বধর্ম
প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার সমন্বয়ঃ তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষা বিষয়ে হাতেকলমে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে শিক্ষা হবে মুক্ত প্রকৃতির কোলে ও মুক্ত আকাশের নীচে। চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তিনি খোপওয়ালা বড়ো বাক্স বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতির কাছে থেকে এবং আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশু ও কিশোরদের বড়ো হতে সাহায্য করা।
এজন্যই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আশেপাশের গ্রামগুলির যোগাযোগ ছিল। সেখানে গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি ও সকলের মিলনক্ষেত্র হিসেবে পৌষমেলার আয়োজন করা তা হয়। এই মেলায় আশেপাশের গ্রামের মানুষজন তাদের ঘরোয়া সামগ্রী যেমন—মাটির হাঁড়ি, বেতের তৈরি ধামা, কুলা, লোহার তৈরি কড়াই, হাতা প্রভৃতি বিক্রি করে। তা ছাড়া জমিতে উৎপন্ন ফসলও তারা বিক্রির জন্য নিয়ে আসে।
মূল্যায়নঃ রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের চারিত্রিক । বলিষ্ঠতা, মনের প্রসারতা ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তাই তিনি ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার | বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে মনুষ্যত্ববোধের শিক্ষার জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা যা তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও দর্শনের মূলকথা।