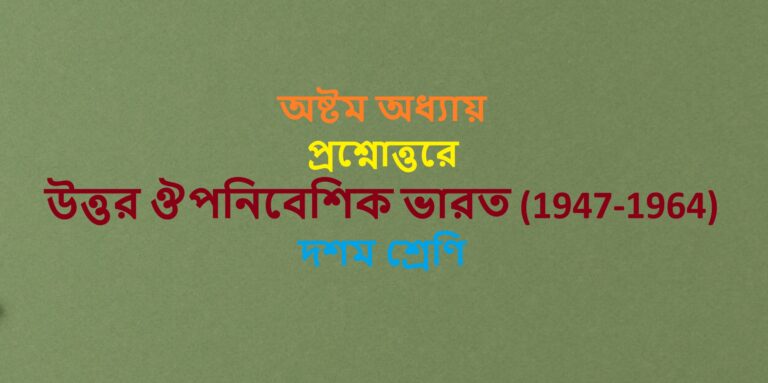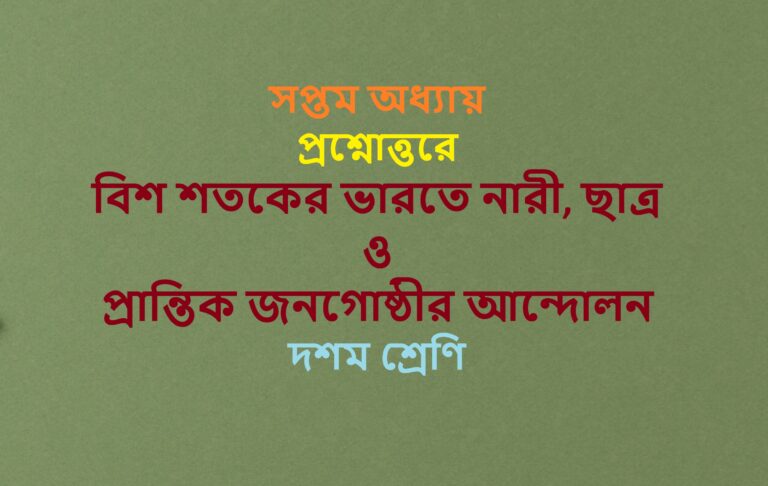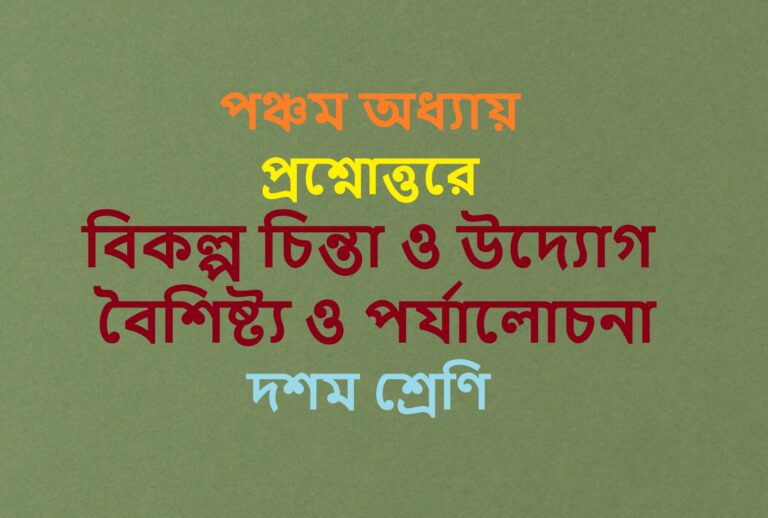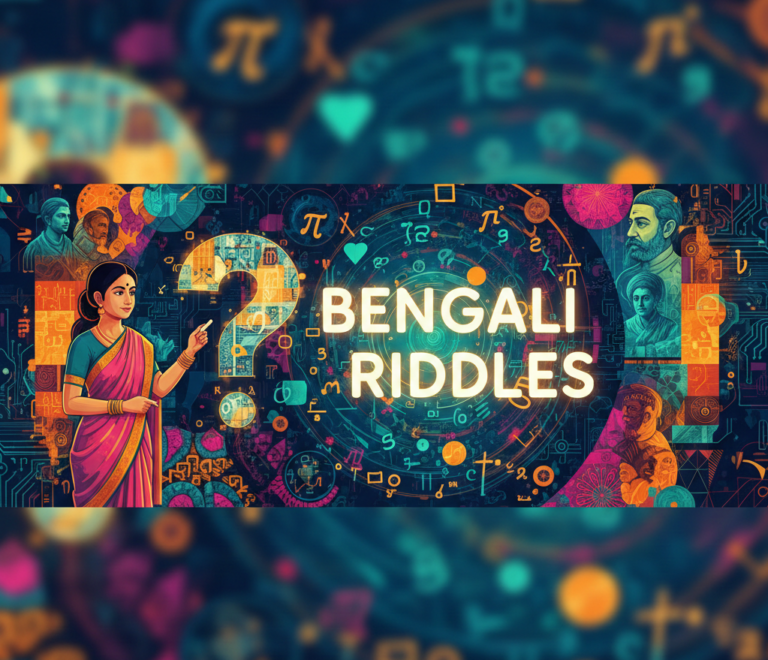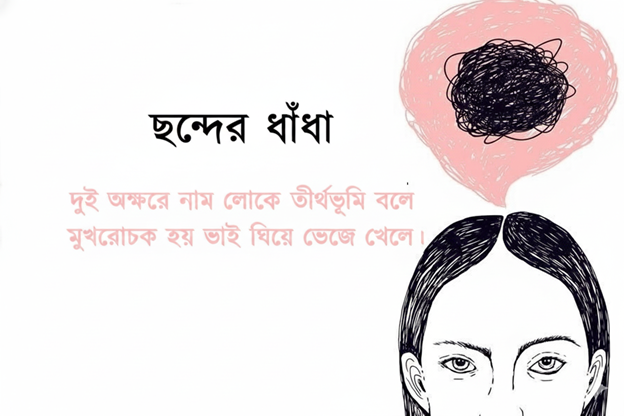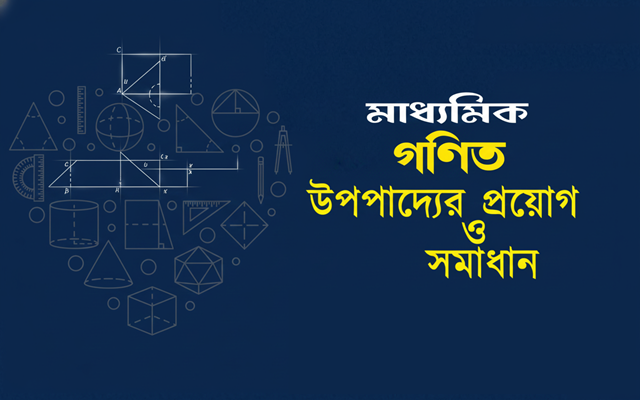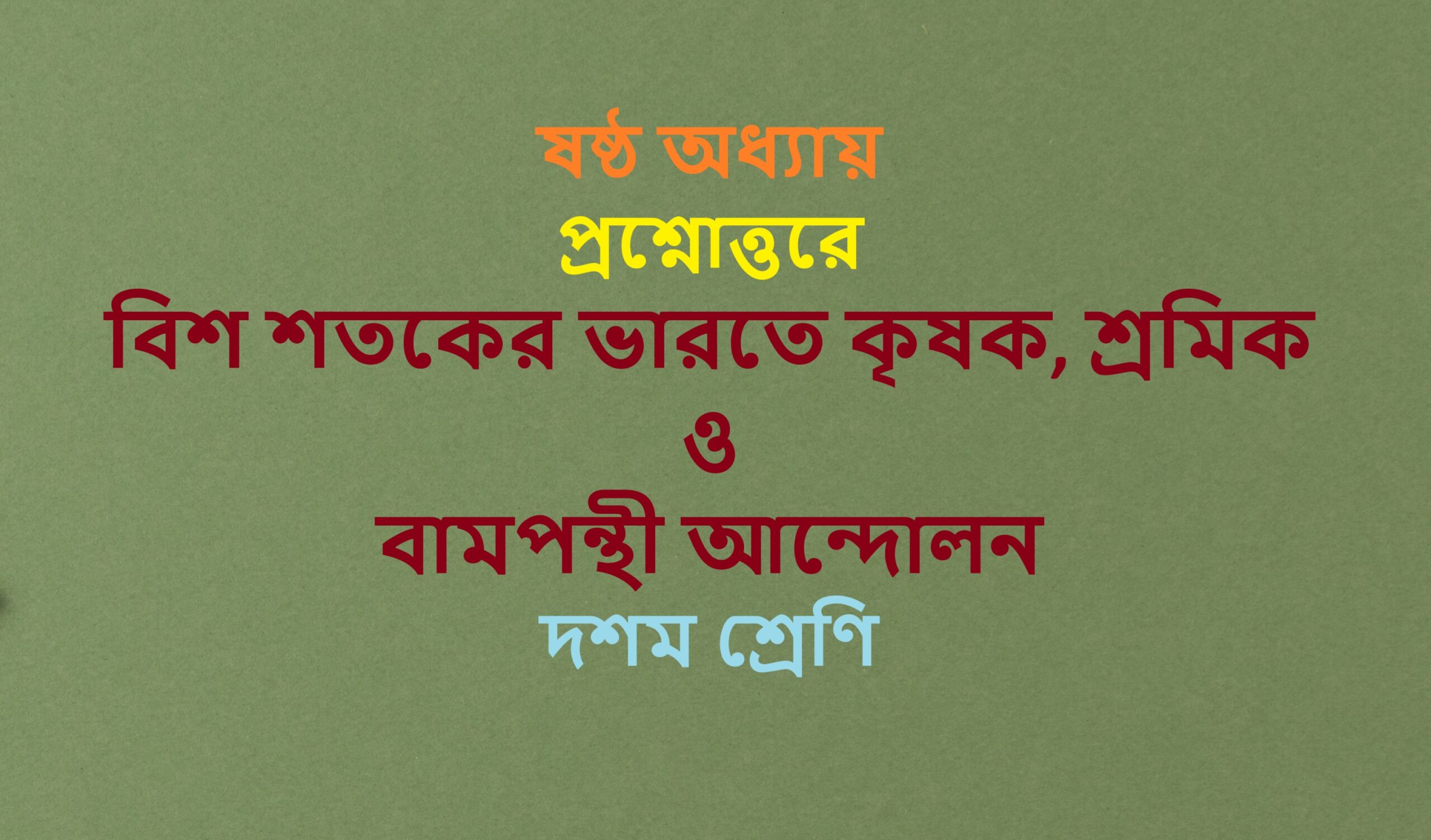
Bis-satakera-bharate krisak-sramik-o-bampanthi-andolan
বিশ শতকের ভারতে কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন
Bis-satakera-bharate krisak-sramik-o-bampanthi-andolan
অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তর বোম্বাই শহরে।
ফরোয়ার্ড ব্লক কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
উত্তর 1939 সালে।
কার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ স্থাপিত হয় ?
উত্তর ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহর নেতৃত্বে।
বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন কবে শুরু হয় ?
উত্তর 1905 খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরপ্রদেশ কিষান সভা‘ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর জওহরলাল নেহরু, গৌরীশঙ্কর মিশ্র ও বাবা রামচন্দ্র ।
কৃষক শ্রমিক দলের মুখপত্র কী ছিল ?
উত্তর ‘লাঙল‘ পত্রিকা।
‘লাঙল‘ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
বিহারে কৃষক আন্দোলনে কে নেতৃত্ব দেন ?
উত্তর স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, ধর্মানন্দ প্রমুখ।
বাংলার ‘কৃষক প্রজা পার্টি‘ কাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তর ফজলুল হক এবং আক্রম খাঁর উদ্যোগে।
‘শের–ই বঙ্গাল‘ নামে কে পরিচিত ছিলেন ?
উত্তর আব্দুল কাশেম ফজলুল হক।
কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর জয়প্রকাশ নারায়ণ ।
ত্রিপুরী অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদে কাকে পরাজিত করেন?
উত্তর পট্টভি সীতারামাইয়াকে।
ভারতের প্রথম শ্রমিক পত্রিকার নাম কী ?
উত্তর ‘ভারত শ্রমজীবী‘।
ভারতে মে দিবস প্রথম কোথায় পালিত হয় ?
উত্তর চেন্নাইয়ে (তৎকালীন মাদ্রাজে)।
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তর তাসখন্দে।
‘জাগরী‘ উপন্যাসের লেখক কে?
উত্তর সতীনাথ ভাদুড়ি।
‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি‘ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তর 1926 খ্রিস্টাব্দে।
‘বেট্টি‘ প্রথা কী ?
উত্তর বেগার শ্রমদান ।
কোথায় ‘পতিদার যুবমণ্ডল‘ গড়ে ওঠে?
উত্তর বারদৌলিতে।
‘লেবার কিষান গেজেট‘ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার।
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
উত্তর 1920 সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম সভাপতি • ছিলেন লালা লাজপত রাই। সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা হয়।
ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
উত্তর দ্য লেবার পেজেন্টস স্বরাজ পার্টি অব দ্য ন্যাশনাল কংগ্রেস নামক দলের নাম পরিবর্তন করে 1928 খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা নির্ধারণ, বাকস্বাধীনতা অর্জন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জন, জমিদারিপ্রথার বিলোপসাধন এবং সর্বনিম্ন মজুরি আইন প্রবর্তন ইতাদি।
কেন একা আন্দোলন শুরু হয় ?
উত্তর 1921 সালে অযোধ্যায় একা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এর কারণ ছিল নির্ধারিত খাজনার চেয়ে 50 শতাংশ অতিরিক্ত খাজনা নির্ধারণ এবং খাজনা আদায়কারী ঠিকাদারদের অকথ্য অত্যাচার ও শোষণ।
কেন বারদৌলি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় ?
উত্তর গুজরাটের সুরাট জেলার বারদৌলি তালুকের কৃষকরা 1928 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বারদৌলি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিল। এর কারণ ছিল হালিপ্রথা, তুলোর দামের পতন এবং বোম্বাই সরকার কর্তৃক প্রথমে 30 ও পরে 22 শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি ।
মাদারি পাসি কে ছিলেন?
উত্তর মাদারি পাসি ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনকালে যুক্তপ্রদেশের একজন বিশিষ্ট কৃষক নেতা। যুক্তপ্রদেশের হরদই, বারাবাঁকি, সীতাপুর সহ একাধিক জেলার কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে তিনি অতিরিক্ত কর নির্ধারণ, খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে অত্যাচার, বেগারশ্রম প্রভৃতির বিরুদ্ধে ‘একা’ বা ‘একতা’ আন্দোলন শুরু করেন।
কৃষক আন্দোলনে বাবা রামচন্দ্রের ভূমিকা কী ছিল ?
উত্তর বাবা রামচন্দ্র যুক্তপ্রদেশে কৃষক আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যেমন—জমিতে বেগার খাটানো, জমি বেদখল করা, আবার অনেকসময় বেআইনিভাবে খাজনা গরিব অসহায় কৃষকদের থেকে আদায় করা হতো। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। বাবা রামচন্দ্র এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংঘটিত করেছিলেন।
মোপালা বিদ্রোহের কারণ কী?
উত্তর দরিদ্র মোপালাদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও আক্রমণ এই বিদ্রোহের জন্ম দেয়। ডিত্তর মোপালারা ছিল মূলত সমুদ্র উপকূলবর্তী কেরল রাজ্যের মালাবার অঞ্চলের কৃষিজীবী। 1873-1896 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে জমিদারের খাজনা, মহাজনদের ঋণের দায়ে অত্যাচার সব মিলিয়ে তীব্র অসন্তোষ দীর্ঘস্থায়ী মোপালা বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল একাধিক সময়ে।
কী উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর 1936 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী দলটি গড়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারিপ্রথার বিলোপ, বেগারশ্রমপ্রথার অবসান, ভূমিরাজস্বের পরিমাণ কমানো, কৃষকদের মধ্যে জমিবণ্টন, কাজের অধিকার ও ন্যায্য পারিশ্রমিকের দাবিতে আন্দোলন সংঘটিত করে দাবি আদায় করা ।
আল্লুরি সীতারাম রাজু কে ছিলেন?
উত্তর আল্লুরি সীতারাম রাজু ছিলেন একজন ভারতীয় বিপ্লবী যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। রাজু 1922-24 সালে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ‘রুম্পা উপজাতিদের বিদ্রোহ’–এ নেতৃত্ব দেন, যা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন উপজাতীয় নেতা এবং তাঁদের অন্য সমর্থকদের দ্বারা। স্থানীয় জনগণের নিকট তিনি ‘মান্যম বীরুদ’ বা ‘অরণ্যের বীর’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
মিরাট ষড়যন্ত্র মামলাটি কী ?
উত্তর 1929 খ্রিস্টাব্দের 20 মার্চ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 33 জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করা হয়, তা ইতিহাসে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। এই মামলায় যেসব নেতার দীর্ঘ কারাবাস হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুজফ্ফর আহমেদ, শিবনাথ ব্যানার্জি, ধরণী গোস্বামী, অমৃত ডাঙ্গে, পি. সি. জোশী, ফিলিপ স্প্রাট, গঙ্গাধর অধিকারী প্রমুখ।
কবে, কোথায় ‘একা আন্দোলন‘ সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর 1922 খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে যুক্তপ্রদেশের উত্তর–পশ্চিম অযোধ্যায়।
কবে, কেন বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন হয় ?
উত্তর 1905 খ্রিস্টাব্দের 16 অক্টোবর লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে ভাগ করলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী __আন্দোলনের সূচনা হয়। জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার জন্যই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বাংলার কৃষকরা কেন যোগদান করেনি?
উত্তর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে কোনো নেতাই কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বা কৃষিজমির খাজনা বন্ধের কথা না বলায় এই আন্দোলনে বাংলার কৃষকরা যোগদান করেনি।
‘তিনকাঠিয়া’প্ৰথা কী ?
উত্তর চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবরা চাষিদের জোর করে প্রতি বিঘা জমিতে 3 কাঠা নীল চাষ করতে বাধ্য করত। আবার এই উৎপাদিত নীল চাষিরা কমদামে নীলকরদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য ছিল। এই প্রথাকেই ‘তিনকাঠিয়া’প্রথা বলা হতো।
কালিপরাজ ও উজালিপরাজ কী ?
উত্তর বারদৌলি তালুকে উচ্চবর্গের মানুষ বা জমির মালিক বা পতিদাররা উজালিপরাজ নামে পরিচিত। যে–সমস্ত গরিব ঋণদাস তাদের জমি চাষকরত তাদের কালিপরাজ বলা হতো।
চৌরিচৌরার ঘটনাটি কী ?
উত্তর 1922 খ্রিস্টাব্দের 5 ফ্রেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে পুলিশ বিনা প্ররোচনায় জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে উত্তেজিত জনতা চৌরিচৌরা থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি চৌরিচৌরার ঘটনা নামে পরিচিত।
তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার কী কী উদ্যোগ নিয়েছিল ?
উত্তর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার সেইসময় হওয়া বিধ্বংসী সাইক্লোন–এর পর ত্রাণ সংগ্রহ ও তা বণ্টনের উদ্যোগে গ্রহণ করে। এ ছাড়া সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদলের জাতীয় সরকারের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলে।
মানবেন্দ্রনাথ রায় কে ছিলেন?
উত্তর মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন ভারতের একজন বামপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি 1920 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।
কাদের গ্রেপ্তার করে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হয় ?
উত্তর 1929 খ্রিস্টাব্দে 33 জন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ সরকার মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুজাফ্ফর আহমেদ, এস.এ. ডাঙ্গে প্রমুখ ।
তেভাগা আন্দোলন কী ?
উত্তর 1937 খ্রিস্টাব্দে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, বাংলার বহু কৃষক পরিবারের কৃষিজমিতে কোনো অধিকার নেই। এই কমিশনের সুবাদে ভাগচাষিরা তিন ভাগের এক ভাগ ফসল জমা দেবে বলে স্থির হয়, যা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত।
কে, কবে ‘মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন‘ প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর 1918 খ্রিস্টাব্দে বি. পি. ওয়াদিয়া মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন।
বাবা রামচন্দ্র কে ছিলেন ?
উত্তর বাবা রামচন্দ্র ছিলেন যুক্তপ্রদেশে অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালের কৃষকনেতা।
কে, কোথায় একা আন্দোলন শুরু করেন?
উত্তর মাদারি পাসির নেতৃত্বে উত্তর–পশ্চিম অযোধ্যার হরদই অঞ্চলে একা আন্দোলন শুরু হয়।
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ‘দ্বিজ‘ বলার কারণ কী?
উত্তর প্রথমে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে 1920 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের নেতৃত্বে 1925 খ্রিস্টাব্দে ভারতের কানপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দু‘বার প্রতিষ্ঠার ফলে কমিউনিস্ট পার্টিকে ‘দ্বিজ’বলা হয় ।
বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর
বারদৌলি সত্যাগ্রহের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের কীরূপ মনোভাব ছিল ?
অথবা, বারদৌলি সত্যাগ্রহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।
অথবা, বারদৌলি সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
উত্তর
সূচনাঃ বিশ শতকে পরাধীন ভারতে সংঘটিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ঘটনা ছিল 1928 খ্রিস্টাব্দের বারদৌলি সত্যাগ্রহ আন্দোলন। গুজরাটের সুরাট জেলার বারদৌলি তালুকে এই শক্তিশালী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
আন্দোলনের কারণঃ বারদৌলি তালুকে বসবাসকারী কুনধি ও পাতিদার কৃষক যারা জমির মালিক ছিল তাদের তুলনায় কালিপরাজ বা খেতমজুর শ্রেণির মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি। 1925 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়া সত্ত্বেও এই নিম্নশ্রেণির কৃষকদের ওপর রাজস্বের পরিমাণ প্রায় 22 শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়, ফলে তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। এর প্রতিবাদস্বরূপ শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহ। এ ছাড়া কুনবরোজি মেহতা, কল্যাণজি মেহতা নামে দু‘জন নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রস্তাব দেন।
বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকাঃ বারদৌলির কৃষকদের বল্লভভাই প্যাটেল ঐক্যবদ্ধ করেন এবং তাদের সংঘবদ্ধভাবে অহিংস আন্দোলনের পথ দেখান। এই সত্যাগ্রহে তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের জন্য বারদৌলি অঞ্চলের নারীরা বল্লভভাই প্যাটেলকে ‘সর্দার’ উপাধি প্রদান করেন।
নারীনেতৃত্বঃ বারদৌলি সত্যাগ্রহে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য নারীনেতৃত্ব লক্ষ করা যায় যাঁরা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন। যেমন—মণিবেন প্যাটেল, মিঠুবেন প্যাটেল, সারদা মেহতা, ভক্তিবাই প্রমুখ।
সত্যাগ্রহের প্রভাবঃ বারদৌলি সত্যাগ্রহ একটি আঞ্চলিক আন্দোলন হলেও সর্বভারতীয় প্রচার পায়। আন্দোলনের চাপে পরে সরকার নিযুক্ত কমিটি 6:03 শতাংশ খাজনা বৃদ্ধির বিষয়টি ঠিক করে এবং কৃষকরা তা দিতে স্বীকৃত হয়।
বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়ে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা কীরূপ ছিল?
উত্তর
সূচনাঃ 1905 খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল বাংলার শ্রমিক সম্প্রদায় । এই আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন থাকায় সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে।
নেতৃত্বঃ এই আন্দোলনে পেশাদার রাজনীতিকরা নেতৃত্ব দেন। তাঁরা কলকারখানা, ছাপাখানা, পাটকল প্রভৃতি স্থানে শ্রমিক ও কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনে শামিল হতে অনুপ্রাণিত করেন। উল্লেখযোগ্য শ্রমিক নেতার মধ্যে ছিলেন—প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অপূর্বকুমার ঘোষ, অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জি, প্রেমতোষ বসু এবং অম্বিকাচরণ ব্যানার্জি প্রমুখ ।
শ্রমিক ধর্মঘটঃ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 1905 খ্রিস্টাব্দের 16 অক্টোবর বাংলার বিভিন্ন কলকারখানায় সারাদিনব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট পালিত হয়। হাওড়ার বার্ন কোম্পানিতে 12500 শ্রমিক ধর্মঘট করেন। বাংলার 37টি পাটকলের মধ্যে 18টিতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। বাংলার শ্রমিকেরা ‘বন্দেমাতরম‘ ধ্বনি দিয়ে ‘রাখিবন্ধন‘ উৎসব পালন করে।
প্রভাবঃ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বাংলার শ্রমিক শ্রেণির সক্রিয় যোগদানে জাহাজ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাট শিল্প, ছাপাখানা শিল্প, রেল শিল্পে ধর্মঘট পালিত হয়।
মূল্যায়নঃ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘটের দরুন তারা সমকালীন অবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণি হিসেবে পরিচিতি পায়। তারা ভবিষ্যতে জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোতের অংশীদার হয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে ভারতের কৃষকদের কী ভূমিকা ছিল তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
অথবা, বিশ শতকে ভারতে কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করো।
অথবা, বিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভারতের কৃষকদের অংশগ্রহণ বর্ণনা করো।
উত্তরঃ উনিশ শতকে ভারতের নানা প্রান্তে কৃষকরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু বিশ শতকে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কৃষকরাও রাজনীতির অঙ্গনে নিজেদের স্বতন্ত্র জায়গা করে নেয়।
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানঃ কংগ্রেস তথা গান্ধিজির আহ্বানে সারাভারতের কৃষকরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে।
বিহারঃ পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, মধুবনি প্রভৃতি জেলার কৃষকরা অসহযোগ আন্দোলনের সময় জমিদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করে ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ।
বাংলাঃ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, বীরভূম, পাবনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুর ও রাজশাহির কৃষকরা এসময়ের আন্দোলনে যোগ দেয়।
যুক্তপ্রদেশঃ বাবা রামচন্দ্রের নেতৃত্বে বারাবাঁকি, সীতাপুর, বারাইচ ইত্যাদি জেলার কৃষকরা আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় এখানে বেশ জোরালো অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত হয়। এছাড়াও পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার একাংশে কৃষকরা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।
আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানঃ সারাভারতের কৃষক শ্রেণি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।
বাংলাঃ শ্রীহট্ট, আরামবাগ, কাঁথি, মহিষাদল ইত্যাদি স্থানে আন্দোলনে কৃষকদের যোগদানে আইন অমান্য তীব্র আকার নেয়।
বিহারঃ কিষানসভার নেতৃত্বে এখানে কৃষকরা আন্দোলনে যোগদান করে।
উত্তরপ্রদেশঃ আগ্রা, লখনউ, রায়বেরিলি সহ নানা স্থানে কৃষকদের যোগদানে এই আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ নেয়।
গুজরাটঃ বারদৌলি, খেদা, সুরাটের কৃষকরা আইন অমান্য আন্দোলনে শামিল হয়। ও ভারতছাড়ো আন্দোলন : এইসময় বাংলা, বিহার ও ওড়িশার কৃষকরা ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে।
বাংলাঃ দিনাজপুরের বালুরঘাট ও মেদিনীপুরের তমলুকে ছিল কৃষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ যা গণআন্দোলনের রূপ নেয়।
বিহারঃ পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগনা ও মুঙ্গেরে কৃষক ও আদিবাসী সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণে ব্রিটিশ প্রশাসন কোণঠাসা হয়ে পড়ে।
ওড়িশাঃ তালচেরে আন্দোলনকারী কৃষক শ্রেণি ‘চাষি মল্লারাজ’ প্রতিষ্ঠা করে। পরিশেষে, জমিদারদের বড়ো অংশ ও একাংশ কংগ্রেস নেতা কৃষকদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানে নারাজ ছিলেন বলে সর্বত্র জোরালো আন্দোলন হয়নি।
টীকা লেখো—W.P.P. বা ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি।
অথবা, ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
উত্তর
সূচনাঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের রাজনীতির অন্যতম দিক ছিল বামপন্থী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে পূর্বের তুলনায় শক্তিশালী করে তোলা। আর এক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল ‘Workers and Peasants Party. ‘
W.P.P.-এর প্রতিষ্ঠাঃ 1920-এর দশকে জওহরলাল নেহরু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থার প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসময়ে 1925 সালের 1 নভেম্বর বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘Workers and Peasants Party’. প্রতিষ্ঠালগ্নে এই দলের নাম ছিল ‘লেবার স্বরাজ পার্টি অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস‘।
W.P.P.-এর উদ্দেশ্যঃ এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা কমানো, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ, শ্রমিক শ্রেণিকে সুসংগঠিত করা।
নেতৃত্ব ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম, কুতুবুদ্দিন আহমেদ, হেমন্ত সরকার প্রমুখ। পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন মুজফ্ফর আহমেদ, গোপেশ চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ। এই দলের মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক ‘লাঙল‘ পত্রিকা যার পরবর্তীকালে নাম হয় ‘গণবাণী’।
মন্তব্যঃ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই সংগঠনটির অবদান অনস্বীকার্য। 1928 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় W.P.P.-এর প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে সংগঠনটি সাধারণ ও অতিসাধারণ মানুষের জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়।
তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে যা জানো লেখো।
অথবা, টীকা লেখো – তেভাগা আন্দোলন।
উত্তর
সূচনাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন Congres তুঙ্গে সেইসময় ভারতের অন্যতম কৃষক আন্দোলন ছিল তেভাগা আন্দোলন। 1946 খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে এটি বামপন্থী ভাবধারায় পরিচালিত ব্যাপক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনের স্লোগান ছিল ‘আধি নয়, তেভাগা চাই”।
তেভাগা আন্দোলনের কারণঃ তেভাগা আন্দোলনের কারণগুলি নিম্নরূপ–
1943 সালের দুর্ভিক্ষঃ বাংলায় 1350 বঙ্গাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণে অভুক্ত কৃষকরা খুবই কমদামে নিজেদের জমিজমা বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল।
জমিদার ও জোতদারদের শোষণঃ এইসময় বাংলায় জমিদার ও জোতদার শ্রেণির অতিরিক্ত রাজস্বের চাপ এবং তা আদায়ের জন্য কৃষকদের ওপর কঠোর অত্যাচারে কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।
কৃষক প্রজা পার্টিঃ 1936 খ্রিস্টাব্দে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ‘সারা ভারত এই সংগ কৃষক সভা’ যা এই কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সহায়ক হয়েছিল।
অন্যান্য কারণঃ এ ছাড়া সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যসংকট ও সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই তেভাগা আন্দোলন সফল হয়েছিল।
আন্দোলনের বিস্তারঃ তেভাগা আন্দোলন 1946 খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলায় রামচন্দ্রপুর গ্রামে শুরু হয়। অল্পসময়ে এই আন্দোলন ময়মনসিংহ, রংপুর, যশোর, খুলনা ও নদিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মেদিনীপুর, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও কাকদ্বীপে এই আন্দোলন গণরূপ নিয়েছিল।
প্রধান নেতাঃ তেভাগা আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন হাজি মহম্মদ, দানেশ (জনক), দেবপ্রসাদ ঘোষ, অজিত বসু, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, ইলা মিত্র প্রমুখ। মেদিনীপুরে এর নেতৃত্ব দেন বিমলা মণ্ডল, কাকদ্বীপে নেতৃত্ব দেন কংসারি হালদার
আন্দোলন দমনঃ খুবই অল্পসময়ের মধ্যে এই আন্দোলন প্রায় সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে ঠিকই কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমননীতি দ্বারা পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীর মাধ্যমে অত্যন্ত হিংস্রতার সাথে এই আন্দোলন দমন করেছিল।
আন্দোলনের ফলাফলঃ তেভাগা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও এর ফলাফল ছিল সুদুরপ্রসারী। এই আন্দোলনের ফলে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ‘বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল’ পাশ হয়েছিল। এর দ্বারা ভাগচাষিদের উচ্ছেদ বন্ধ হয়। এ ছাড়াও উৎপন্ন ফসলের দুই–তৃতীয়াংশ বর্গাদারদের (চাষি) দেওয়ার কথা বলা হয় ।
টীকা লেখো—AITUC.
অথবা, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্বন্ধে কী জানো?
উত্তর
সূচনাঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে যখন সমগ্র বিশ্বজুড়ে শ্রমিক শ্রেণির দাবিদাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেইসময় ভারতবর্ষেও শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে গড়ে উঠেছিল একাধিক শ্রমিক সংগঠন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ‘All India Trade Union লন | Congress’ বা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।
পটভূমিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বামপন্থী রাজনীতি সমগ্র বিশ্বজুড়ে সর্বহারা শ্রমিক এই শ্রেণির স্বার্থে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে সকলকে জাগরিত করে। এইসময় ভারতবর্ষেও বামপন্থী ভাবধারার বিকাশ ঘটে। এ ছাড়া 1920 সালে কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশন ও নাগপুরের বিশেষ অধিবেশনেও শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।
প্রতিষ্ঠাঃ 1920 সালের 30 অক্টোবর থেকে মাদ্রাজে আয়োজিত এক শ্রমিক সম্মেলনে শ্রমিক ইউনিয়নের 806 জন প্রতিনিধি একত্রিত হন। অবশেষে 1820 খ্রিস্টাব্দের 31 বর বোম্বাই শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ বা ‘AITUC’.
AITUC-এর নেতৃবৃন্দঃ AITUC-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন লালা লাজপত রাই, সহসভাপতি ছিলেন জোসেফ ব্যাপ্তিস্তা ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দেওয়ান চমনলাল। এ ছাড়া এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন জিন্না, অ্যানি বেসান্ত, বল্লভভাই প্যাটেল, মতিলাল নেহরু প্রমুখ।
কর্মসূচিঃ এই সংগঠনের মূল কর্মসূচি ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণিকে আরও ণে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলা এবং সকল স্তরের শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করা। সেই সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো।
মন্তব্যঃ AITUC-এর হাত ধরেই ভারতবর্ষে প্রথম শ্রমিকদের দাবিদাওয়া, উদ্যোগ, বিক্ষোভ য়ে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়। যদিও বলা যায়, শ্রমিক শ্রেণি পূর্ণ স্বরাজের জন্য কোনো বৈপ্লবিক পরিকল্পনা করেনি এবং শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর
সূচনাঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে ছোটো–বড় অনেক শ্রমিক ধর্মঘট ও আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এগুলির দ্বারা ভারতবর্ষের ব্রিটিশবিরোধ স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত হয়েছিল মজবুত ও শক্তিশালী। আসলে এইসময় শ্রমিক আন্দোলনগুলি সংগ্রামমুখী চরিত্রলাভ করেছিল।
শ্রমিক আন্দোলনের কারণঃ বিশ শতকে ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনগুলির প্রধান কারণ ছিল কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির হস্তক্ষেপ, শ্রমিক শ্রেণির চরম দুর্দশা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পর শ্রমিক ছাঁটাই, বাণিজ্যিক মন্দা, অবশিল্পায়ন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি। এ ছাড়া বলশেভির বিপ্লবের প্রভাব, কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দের সমর্থন ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রভাবও ছিল শ্রমিক আন্দোলনের কারণ ।
শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবঃ ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন শ্রেণির যোগদান ঘটেছিল। এর ফলে যেকোনে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচিতে প্রচুর শ্রমিকের যোগদান লক্ষ করা যায়। সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্পাঞ্চলগুলিতে শ্রমিক ধর্মঘটের বিরাট প্রভাব লক্ষ করা যায়। শ্রমিকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান প্রতিটি আন্দোলনকেই অনেক সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়ক করে তোলে ৷
শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যঃ ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিকদের ব্রিটিশবিরোধী কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এক পৃথক আন্দোলনের ধারা লক্ষ করা যায়। শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গান্ধিজির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় ও এই আন্দোলনগুলির বেশিরভাগই ছিল হিংসামুক্ত।
মূল্যায়নঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া, উদ্যোগ, বিক্ষোভ একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয় এবং তা এক সর্বভারতীয় রূপলাভ করে। এইসময় ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনগুলি দমন করা সম্ভব নয়। তাই শ্রমিকদের দাবিদাওয়াগুলি পূরণের মাধ্যমে সরকার তাদের অসন্তোষ দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।
বিশ শতকের ভারতে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা আলোচনা করো।
অথবা, বিংশ শতকের ভারতে ঔপনিবেশিক আন্দোলনে বামপন্থী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র পর্যালোচনা করো।
উত্তর
সূচনাঃ বিশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই বিশ্বজুড়ে বামপন্থী ভাবধারা ও রাজনীতির সূত্রপাত ও ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। এইসময় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি জাতীয় আন্দোলনের| মূলধারায় যুক্ত হয়েছিল বামপন্থীদের হাত ধরে। এরাই এইসময় উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করেছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়, মুজফ্ফর আহমেদ–এর নেতৃত্বে বামপন্থী | তৎপরতায় ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গতিশীল হয়ে ওঠে।
বামপন্থী আন্দোলনের ভূমিকা/বৈশিষ্ট্য
বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাবঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে 1917 সালে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে | শ্রমিক শ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণি নতুনভাবে উজ্জীবিত হয় যা ভারতবর্ষে বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি ঘটায়।
কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠাঃ রাশিয়ার তাসখন্দে 1920 খ্রিস্টাব্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এইসময় ভারতে মহম্মদ আলি, অবনী মুখার্জি, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বরকতুল্লা প্রমুখ কংগ্রেসের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বামপন্থী ভাবধারার বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।
আদর্শ ও নীতিঃ বামপন্থী দলের নীতি ও আদর্শ ছিল শ্রেণিহীন–শোষণহীন সমাজ গঠন, | ও জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ ঘটানো, উৎপাদন–উপকরণের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক বিরোধী শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করা। এইসকল নীতি ও আদর্শের কারণে পরাধীন ভারতে বামপন্থী আন্দোলন কোনো ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল।
ঔপনিবেশিকদের দমননীতিঃ ঔপনিবেশিকরা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট নেতাদের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদিতে জড়িয়ে বামপন্থী ভাবধারা ধ্বংসের চেষ্টার পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টিকেও নিষিদ্ধ করে।
কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রের প্রসারঃ ঔপনিবেশিক ভারতে একশ্রেণির কংগ্রেস নেতা বামপন্থী ভাবধারা ও সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হন। এর ফলে 1934 খ্রিস্টাব্দে জয়প্রকাশ নারায়ণ–এর হাত ধরে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠিত হয়।
বামপন্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিঃ বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত নেতাগণ প্রথম থেকেই ব্রিটিশের কাছ থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানালেও 1929 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে এই দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বামপন্থী কর্মসূচিঃ 1939 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে।একদিকে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ‘ফরওয়ার্ড ব্লক‘ দল প্রতিষ্ঠা ও ভারতছাড়ো আন্দোলনকালে | বামপন্থীদের মধ্যে সংহতিসাধন ও আপসহীন উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন বামপন্থী নেতৃত্ব।
লক্ষ্যঃ কৃষক, শ্রমিক সহ সমাজের সকল স্তরের নিপীড়িত মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তি ছিল বামপন্থী রাজনীতির মূললক্ষ্য। এরজন্যই তারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে আগ্রহী ছিলেন|
মন্তব্যঃ ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে বামপন্থী ভাবধারা প্রতিরোধ করার জন্য নানা দমননীতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন মামলায় শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করেছিল। তবু ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কর্মসূচি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল।
বিশ শতকের ভারতে কৃষক আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করো।
উত্তর
ভূমিকাঃ ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলন অষ্টাদশ শতকে শুরু হলেও তা ছিল বিভিন্ন প্রদেশে বিক্ষিপ্তভাবে সংগঠিত কর্মসূচি। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের বিকাশ লক্ষ করা যায়।
বিশ শতকের কৃষক অন্দোলন
চম্পারণ সত্যাগ্রহঃ 1917 সালে গান্ধিজির নেতৃত্বে বিহারের চম্পারণে তিনকাঠিয়াপ্রথার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে কৃষকরা সাফল্য পায়।
খেদা সত্যাগ্রহঃ 1918 খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের খেদা জেলার কৃষকরা ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে খাজনা হ্রাসের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে গান্ধিজি খেদার কৃষকদের নিয়ে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে খেদা সত্যাগ্রহ শুরু করেন।
মোপালা বিদ্রোহঃ অসহযোগ আন্দোলন পর্বে কেরলের মালাবার অঞ্চলে মোপালা নামক মুসলিম কৃষকরা স্বরাজের সমর্থনে জমিদারবিরোধী ব্যাপক কৃষক আন্দোলন শুরু করে।
একা আন্দোলনঃ 1921-22 খ্রিস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস ও খিলাফতি নেতাদের উদ্যোগে এবং মাদারি পাসির নেতৃত্বে কৃষকরা একতা বা ঐক্যবদ্ধ থাকার শপথ গ্রহণ করে হরদোই, সীতাপুর, বারাই, বারাবাঁকি জেলায় ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে।
বারদৌলি সত্যাগ্রহঃ গুজরাটের সুরাট জেলার বারদৌলি তালুকে সরকার 30 শতাংশ খাজনা বৃদ্ধি করলে বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কৃষকরা খাজনা না দেওয়ার আন্দোলন শুরু করে। শেষপর্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি আটকানো সম্ভব হয়।
তেভাগা আন্দোলনঃ 1946-47 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় কৃষক সভার উদ্যোগে এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়৷ কৃষকরা যে জমিতে চাষ করে তার ওপর দখলি স্বত্বপ্রদানের দাবি করে বাংলার প্রায় 60 লক্ষ কৃষক এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল।
পুন্নাপ্রা–ভায়লার গণআন্দোলনঃ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কৃষক ও শ্রমিকরা সেখানকার দেওয়ান রামস্বামী আয়ারের বিরুদ্ধে 1946 সালে যে গণসংগ্রাম পরিচালিত করেছিল তা পুন্নাপ্রা–ভায়লার গণসংগ্রাম নামে খ্যাত।
মূল্যায়নঃ উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে যেসব কৃষক আন্দোলন হয়েছিল সেগুলির ওপর কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কৃষক আন্দোলনগুলি ছিল পুরোপুরি কমিউনিস্ট পরিচালিত। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের এই কৃষক আন্দোলনগুলির বেশিরভাগই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।
ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময়ে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির অবদান কী ছিল ?
অথবা, ভারতছাড়ো আন্দোলন পর্বে কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণির অবদান কীরূপ ছিল ?
অথবা, ভারতছাড়ো আন্দোলন পর্বে শ্রমিক শ্রেণির অবদান কীরূপ ছিল ?
উত্তর
সূচনাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতছাড়ো আন্দোলন পর্বে ভারতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি এইসময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে গতিশীল করে তোলে। তৎকালীন সময়ে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণিকে ভারতছাড়ো আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।
তা
ভারতছাড়ো আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিকা
কৃষকদের যোগদানের কারণঃএইসময় দরিদ্র কৃষকরা জাতীয়তাবাদী আবেগে আন্দোলনে শামিল হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধজনিত কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পেলে দরিদ্র কৃষকরা এই আন্দোলনে যোগদান করে।
বাংলার কৃষকদের ভূমিকাঃ বাংলার মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষকরা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করে। সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’। এ ছাড়াও বর্ধমান, দিনাজপুর, হুগলি, বালুরঘাট প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকরা আন্দোলনে শামিল
হয়।
ওড়িশার কৃষকদের ভূমিকাঃ ওড়িশার তালচের, কটক প্রভৃতি স্থানে লক্ষ্মণ নায়েকের নেতৃত্বে খাজনা বন্ধ, থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে প্রচুর কৃষক ঝাঁপিয়ে পড়ে।
গুজরাটের কৃষকদের ভূমিকাঃ গুজরাটের খান্দেশ, আমেদাবাদ, সুরাট, ক্লোচ প্রভৃতি জেলার কৃষকরা গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণ করে রেল যোগাযোগ ছিন্ন, সরকারি নথিপত্র পুড়িয়ে দিয়ে আন্দোলনকে গণরূপদান করেছিল। এ ছাড়া এইসময় যুক্তপ্রদেশ, বিহার, তামিলনাড়ু প্রভৃতি স্থানেও কৃষক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল।
ভারতছাড়ো আন্দোলনে শ্রমিকদের ভূমিকা
শ্রমিকদের যোগদানের কারণঃ এইসময় বিশ্বব্যাপী আর্থিক মহামন্দার কারণে ভারতে অজস্র কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেলে অগণিত শ্রমিক কর্মহারা হয়ে পড়ে, শ্রমিকদের মজুরিহ্রাস এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির কারণে এইসময় দলে দলে শ্রমিক ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করেছিল।
বাংলার শ্রমিকদের ভূমিকাঃ বাংলার শহরাঞ্চলে কলকারখানা থেকে কর্মচ্যুত শ্রমিকরা এইসময় ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করে আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল ।
মহারাষ্ট্রের শ্রমিকদের ভূমিকাঃ 1942-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় মহারাষ্ট্রের নাগপুর, কোলাপুর, বোম্বাইয়ের শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। বোম্বাই শিল্পাঞ্চল এবং বোম্বাইয়ের শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন অধিক সক্রিয় ছিল।
বিহারের শ্রমিকদের ভূমিকাঃ বিহারে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির শ্রমিকরা 13 দিন ধরে ধর্মঘট চালিয়ে যায়। তাদের দাবি ছিল যতদিন পর্যন্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন তারা ধর্মঘট চালিয়ে যাবে।
এ ছাড়া এইসময় যুক্তপ্রদেশ,কানপুর, আমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি স্থানের শ্রমিকরা ভারতছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।
মন্তব্যঃ দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতছাড়ো আন্দোলন পর্বে শ্রমিক ও কৃষকদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। শুধমাত্র নিজ নিজ দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য নয়, দেশের স্বার্থে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির যোগদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।
আইন অমান্য আন্দোলন পর্বে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির ভূমিকা লেখো।
উত্তর
সূচনাঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষত আইন অমান্য আন্দোলনে সমগ্র ভারতবাস শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির মানুষের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। এইসময় বাংলা, বিহার, গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।
কৃষক ও শ্রমিকদের যোগদানের কারণঃ এইসময় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাজনিত কারণে কৃষিজ পণ্যের মূল্যহ্রাস সমগ্র দেশে শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এইসময় অসহায় শ্রমিক ও কৃষকরা তাই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। 1930-31 এবং 1932-34 খ্রিস্টাব্দে এই দু‘টি পর্যায়ে সংগঠিত আইন অমান্য আন্দোলনে তাই শ্রমিক ও কৃষকদের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো।
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলনঃ 1930 সালে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি কংগ্রেসের নেতৃত্বে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে যোগদান করে।
বাংলায় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনঃ আইন অমান্য আন্দোলনকালে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে। অন্যদিকে মেদিনীপুর, রাজশাহি, হুগলি, দিনাজপুর, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে কৃষকরা চৌকিদারি কর বন্ধ করে ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে।
যুক্তপ্রদেশে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনঃ যুক্তপ্রদেশের রায়বেরিলি, মিরাট, আগ্রা, করাচি, লখনউ প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকরা হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করে। এ ছাড়া যুক্তপ্রদেশ, মিরাট, কানপুরের বস্ত্র কারখানা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয় ধর্মঘটের কর্মসূচি ও আন্দোলন।
মন্তব্যঃ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্বের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন প্রবল আগ্রহে শুরু হলেও অন্তিম পর্বে এতে শ্রমিক ও কৃষকদের যোগদান কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ে নয়, সার্বিক স্বার্থে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির অবদান অনস্বীকার্য।
মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে টীকা লেখো।
অথবা, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
উত্তর
সূচনাঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে এগিয়ে এসেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। এইসময় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রমিক আন্দোলন আরও শক্তিশালী ও গণরূপ ধারণ করেছিল। এইসময় বিশেষ করে 1920 –এর দশকে ভারতবর্ষে বামপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনগুলি দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা যেসকল দমনমূলক মামলা করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম
ছিল ‘মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা।‘
প্রেক্ষাপটঃ 1920-র দশকে কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার শ্রমিক এস.এ. ডাঙ্গে, সিরজাকর–এর নেতৃত্বে ও ‘গিরনী কামগার ইউনিয়ন‘-এর উদ্যোগে বোম্বাইয়ের বস্তুকলে ধর্মঘট করে। 1925 খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনেও কয়েক হাজার শ্রমিক পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলে।
সরকার–এর দমনমূলক নীতিঃ এইসময়ে ব্রিটিশ সরকার শ্রমিকদের ব্রিটিশ বিরোধী কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য ‘জননিরাপত্তা বিল’ ও ‘বাণিজ্যবিরোধী বিল‘ পাশ করে। এ ছাড়া এইসময়ে ‘The Indian Trade Union Act’ অনুসারে শ্রমিকদের রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। এদিকে এইসময় ‘পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট‘ দ্বারা শ্রমিকদের ধর্মঘটে যোগদান করা বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়।
মিরাট ষড়যন্ত্র মামলাঃ উপরিউক্ত বিষয়গুলি যখন ঘটে চলে অর্থাৎ 1920-র দশকের অন্তিম পর্যায়ে তখন ব্রিটিশ সরকার নতুন রণনীতি নিয়েছিল শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য। এই নীতি অনুসারে 1929 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে 31 জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এস. এ. ডাঙ্গে, পি. সি. জোশি, মুজফ্ফর আহমেদ, ফিলিপ স্প্রাট, বেঞ্জামিন ব্র্যাডলি, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ। এঁদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল যে তাঁরা ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। এই অভিযোগ এনে বামপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় ঐতিহাসিক মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা।
মামলার রায় ঘোষণাঃ এই মামলার রায়ে 31/33 জন শ্রমিক নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়। এর সাথে কমিউনিস্ট পার্টি ও সকল বামপন্থী দলের কার্যালয় ও তাদের প্রচারকার্য নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।
মূল্যায়নঃ দীর্ঘ চার বছর ধরে মামলা চলার পর 1933 সালের মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে সমগ্র ভারতবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র লিখেছেন—“এই মামলা শেষপর্যন্ত জাতীয়তাবাদী বামপন্থীদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।”