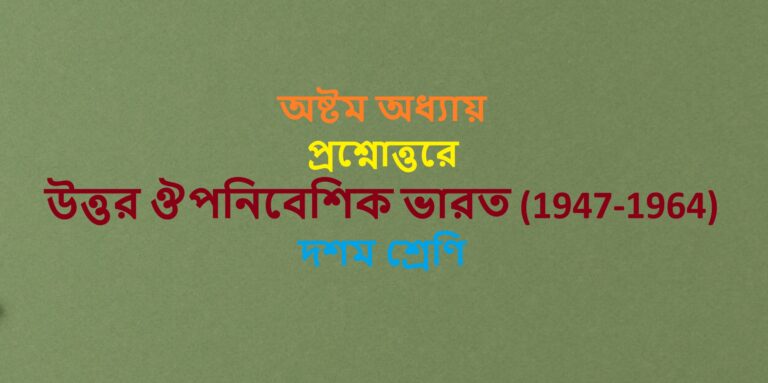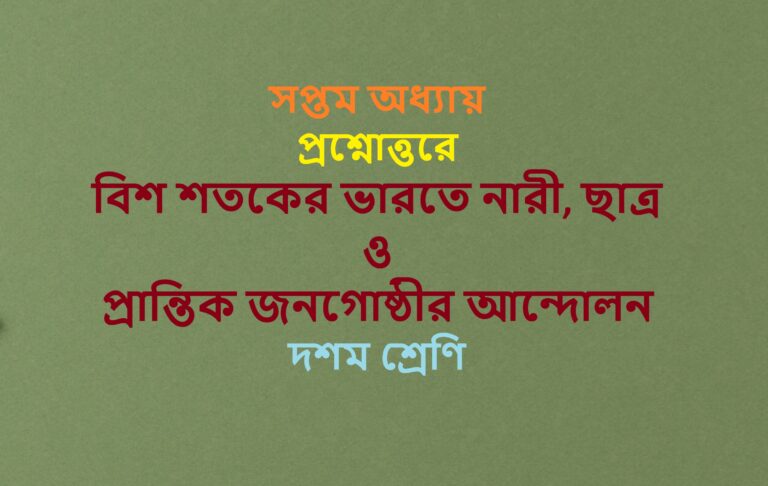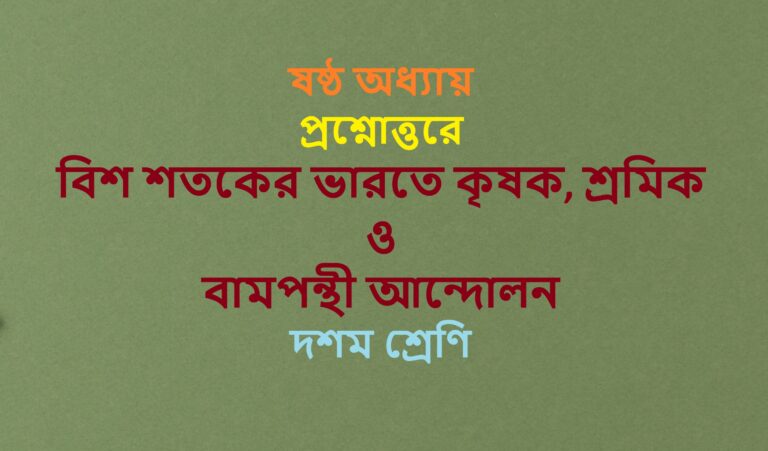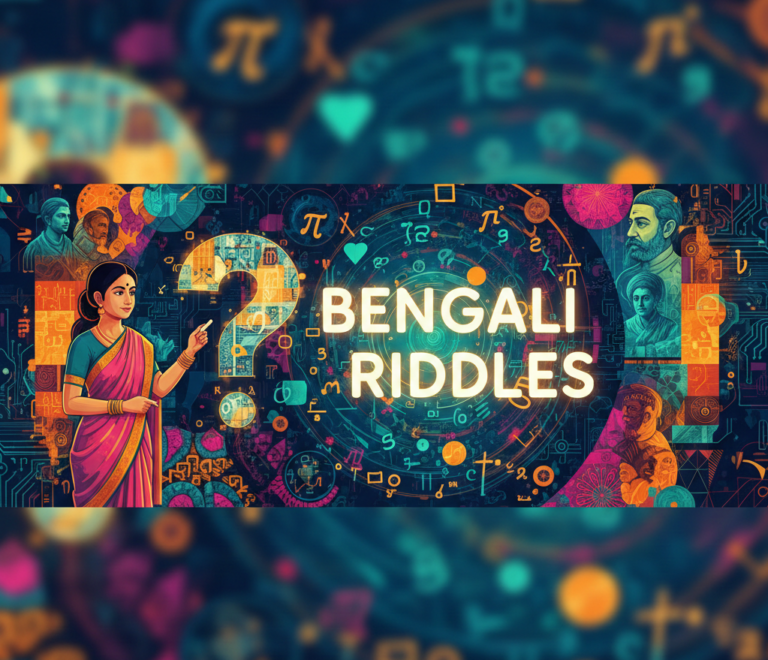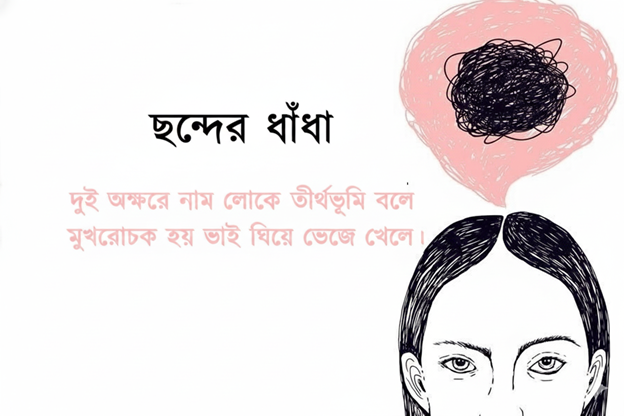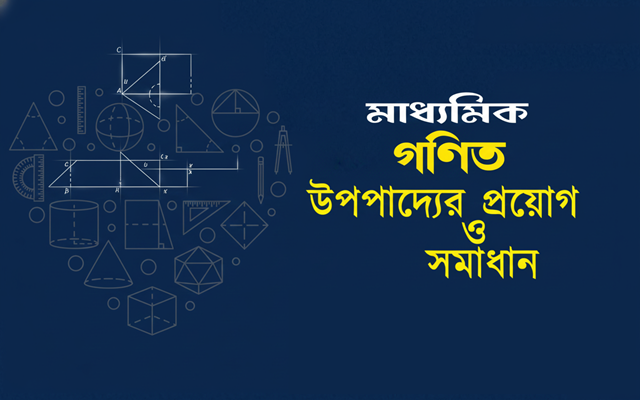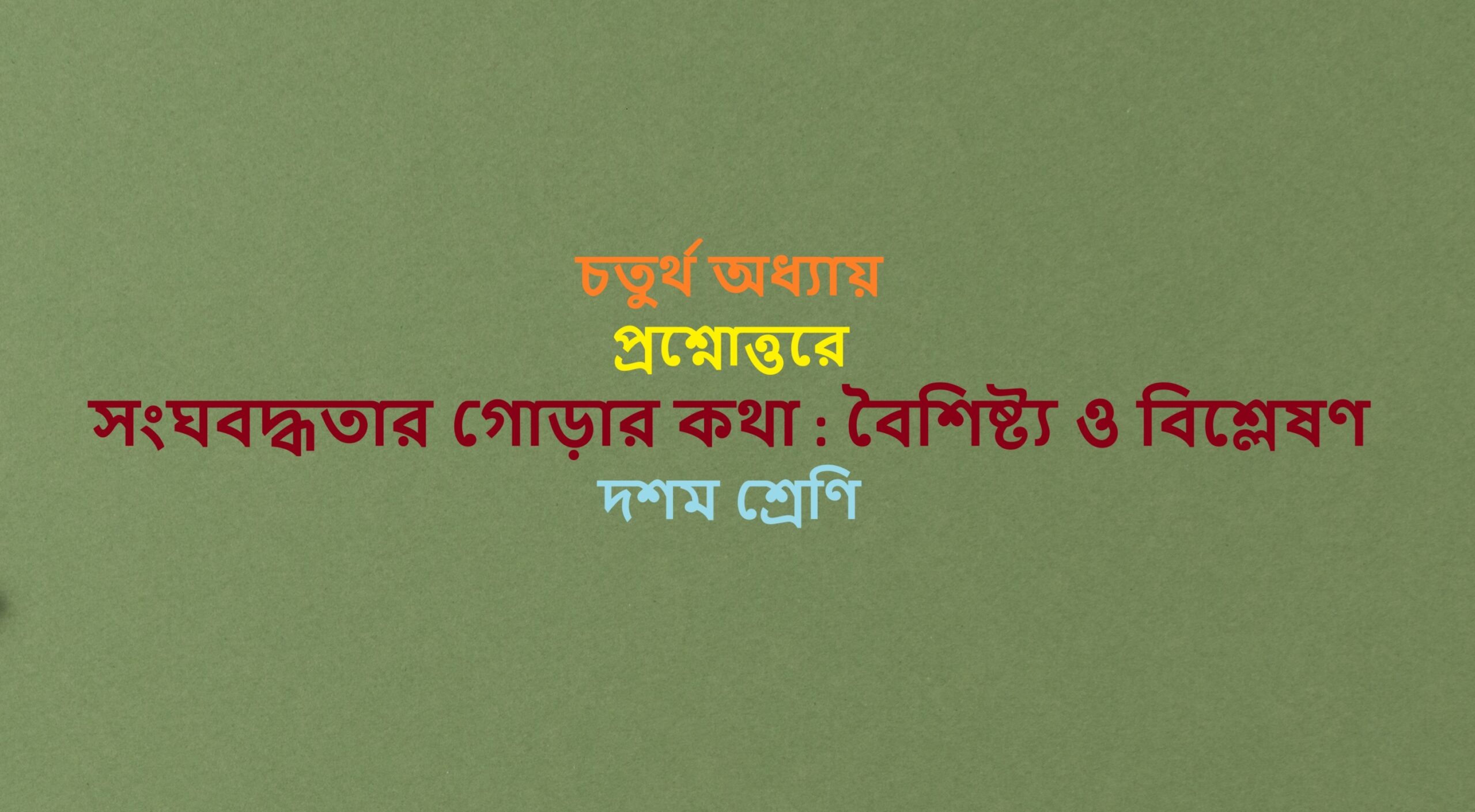
Sanghabaddhatar-gorar-katha-Baisisty-o-bislesan
সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ
Sanghabaddhatar-gorar-katha-Baisisty-o-bislesan
অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ কে বলেছেন ?
উত্তর বিনায়ক দামোদর সাভারকর।
সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা কবে হয়েছিল ?
উত্তর 1857 খ্রিস্টাব্দে।
একজন ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর নাম লেখো।
উত্তর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
1857 খ্রিস্টাব্দে কাকে ‘হিন্দুস্থানের সম্রাট‘ বলে ঘোষণা করা হয়?
উত্তর মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে।
‘অমৃতবাজার পত্রিকা‘র প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উত্তর শিশিরকুমার ঘোষ।
ঊনবিংশ শতাব্দীকে কে ‘সভাসমিতির যুগ‘ বলেছেন?
উত্তর ঐতিহাসিক অনিল শীল।
ইলবার্ট বিল কে রচনা করেন ?
উত্তর লর্ড রিপনের আইন সচিব ইলবার্ট।
‘বন্দেমাতরম‘ সংগীতটি কোন উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে?
উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ থেকে।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কী ধরনের ছবি আঁকতেন?
উত্তর ব্যঙ্গচিত্র।
তাঁতিয়া তোপির প্রকৃত নাম কী ?
উত্তর রামচন্দ্র পান্ডুরঙ্গ।
ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন?
উত্তর লর্ড ক্যানিং।
মহারানির ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ভারতের রাজপ্রতিনিধি হিসেবে প্রথম কে নিযুক্ত হন ?
উত্তর লর্ড ক্যানিং।
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
ভারতসভা প্রতিষ্ঠার যেকোনো দু‘টি উদেশ্য লেখো।
উত্তরঃ প্রথমত, সমগ্র ভারতে শক্তিশালী জনমত জাগ্রত করা।
দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে তোলা।
তৃতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোককে রাজনৈতিক স্বার্থে সংঘবদ্ধ করা।
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে সভাসমিতির যুগ বলা হয় কেন ?
অথবা, সভাসমিতির যুগ বলতে কী বোঝো?
উত্তরঃ ঊনবিংশ শতকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জাতীয়তাবাদের জন্ম। এই জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য এই দেশে নানা সভাসমিতি গড়ে ওঠে। এই পর্বকে অনিল শীল ‘Age of Association’ বা সভাসমিতির যুগ বলেছেন।
‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাস কীভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল ?
উত্তরঃ ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাসে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই উপন্যাসটি ছিল স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র, বিপ্লববাদের প্রেরণা ও শক্তি। সমগ্র দেশের জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে তুলেছিল এই উপন্যাস।
মহারানির ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য কী ছিল ?
উত্তরঃ ব্রিটিশ শাসনকে পুনরায় দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্যে ‘ভারতশাসন আইন’ পাশ করা হয়। তৎকালীন সিপাহি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমন করা। ভারতীয় জনগণের, বিশেষত দেশীয় রাজন্যবর্গের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার আশ্বাস দিয়ে তাঁদের আনুগত্য অর্জন করা এবং তাঁদের আনুগত্য লাভের মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নতুন করে স্থায়ী করা।
জমিদার সভা ও ভারতসভার মধ্যে দু‘টি পার্থক্য লেখো।
উত্তরঃ (ক) জমিদার সভা প্রতিষ্ঠিত হয় জমিদার বা ধনী শ্রেণির মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্যে অন্যদিকে ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের জনগণকে বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শামিল করার জন্যে। (খ) জমিদার সভা হলো ভারতের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন, যা 1838 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে, অন্যদিকে ভারতসভা গঠিত হয় 1876 সালে রাজা রাধাকান্ত দেব–এর সভাপতিত্বে।
ল্যান্ডহোল্ডারস সোসাইটির উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তরঃ 1838 সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করা, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে জমিদারদের স্বপক্ষে আনা এবং ভারতে সর্বোচ্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার ঘটানো।
ভারতমাতা চিত্রটির গুরুত্ব কী ?
উত্তরঃ বিশিষ্ট ভারতীয় চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1905 সালে ভারতমাতা ছবিটি আঁকেন। এই ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ ভারতমাতাকে হিন্দুদের সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর রূপে বৈয়ব সন্ন্যাসিনীর বেশভূষায় চিত্রিত করেছেন। ভারতমাতা চিত্রে গৈরিক বর্ণের ভারতমাতার চারটি হাত। তিনি সাধ্বী রমণীর পোশাকে সুসজ্জিতা। তাঁর এক হাতে রয়েছে পুস্তক, ধানের শিষ, শীতবস্ত্র ও জপমালা। সম্ভবত শিল্পী এই চিত্র দ্বারা ভারতমাতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন।
ব্যঙ্গচিত্র কেন আঁকা হয় ?
উত্তরঃ চিত্রশিল্পের অন্যতম শাখারূপে ব্যঙ্গচিত্রে মূলত তির্যক বা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, ভুলত্রুটি মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। ব্যঙ্গচিত্ত হলো চিত্রকলার একটি বিশেষ অঙ্গ। এমনকী সংস্কৃতির ত্রুটিগুলিকে এখানে আক্রমণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা, ‘বাবু‘ সমাজের ভণ্ডামি এবং ধর্মীয় দ্বিচারিতাকে তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন।
শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটি অংশ কেন মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল ?
উত্তরঃ শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তদের একটি বড়ো অংশ 1857 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের উপর অগাধ বিশ্বাস রাখত। তারা ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করত এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের তীব্র বিরোধী ছিল। বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজদের বিতাড়ন, এরপর কেউ ভারতে জাতীয় রাষ্ট্র বা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে কি না এই বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সন্দিহান ছিল। তাই তারা মহাবিদ্রোহকে সমর্থন করেনি।
নবগোপাল মিত্র কে ছিলেন?
উত্তরঃ হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এ ছাড়া তিনি একজন ভারতীয় নাট্যকার, কবি, প্রাবন্ধিক, দেশপ্রেমিক এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাকর্তাদের অন্যতম।
উনিশ শতকের বাংলায় জাতীয়তাবাদের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের কী ভূমিকা ছিল ?
উত্তরঃ ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছেন। সন্ন্যাসের নতুন আদর্শ প্রচার করে তিনি মাতৃমুক্তি যজ্ঞে নিবেদিতপ্রাণ একদল রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর কথা বলেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হবে মানবমুক্তি, দেশমাতৃকার মুক্তি এবং মানবকল্যাণ ।
মহারানির ঘোষণাপত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?
উত্তরঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর 1858 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটান এবং নিজের হাতে তুলে নেন ভারতের শাসনভার। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ভারতশাসন আইন পাশ করান। এই আইনের বলে ভারতের শাসনভার মহারানি ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয় যা ছিল এই ঘোষণাপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।
কেন বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে রাজনৈতিক সভা বলা হয় ?
অথবা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার রাজনৈতিক আদর্শ কী?
উত্তরঃ 1836 সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা স্বাধীনতার আদর্শকে সম্মান করত। এই সভা ইংল্যান্ডের সমঅধিকার নীতিটির আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। মানুষ মাত্রই সমান এই মহান আদর্শের সমর্থক ছিলেন বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার সদস্যগণ।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা করেছিলেন?
অথবা, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তরঃ গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যঙ্গচিত্রগুলির মাধ্যমে সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি শিক্ষার কারখানা নামক চিত্রে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে কটাক্ষ করেছেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজচেতনা সৃষ্টি করা।
এনফিল্ড রাইফেল কী? অথবা, সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী? অথবা, এনফিল্ড রাইফেলের বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তরঃ সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে সিপাহিদের ব্যবহৃত একটি রাইফেল ছিল এনফিল্ড রাইফেল, যার টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হতো। কিন্তু গুজব রটে যে এটি গোরু ও শূকরের চর্বি দ্বারা তৈরি। ফলে ধর্মনাশের ভয়ে সিপাহিরা বিদ্রোহ করে।
ভারতে জাতীয়তাবোধের বিকাশে ‘গোরা’ উপন্যাসের অবদান লেখো।
উত্তরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘গোরা’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনায় অখণ্ডতাবোধ, দেশপ্রেম জাগ্রত করা, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন যা দেশের জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করতে সহায়ক হয়েছিল।
হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য কী ছিল ?
উত্তরঃ সর্বভারতীয় চেতনা গড়ে তুলে দেশীয় শিল্প, সাহিত্যকে উৎসাহদান এবং সকল শ্রেণির হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করা ও প্রত্যেককে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা।
1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে কারা, কেন প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন?
উত্তরঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে ভারতীয়রা জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়। এইজন্য বিনায়ক দামোদর সাভারকার এই বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।
কী উদ্দেশ্যে ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তরঃ এর উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় স্তরে সকল শ্রেণির মানুষ ঐক্যবদ্ধ করা। বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম শ্রেণির মধ্যে মৈত্রীর প্রসার ঘটানো ও দেশে একটি শক্তিশালী জনমত গঠন করা।
‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা‘ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তরঃ ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা‘ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করা। এ । পতিত জমিকে করমুক্ত করা ও নিষ্কর জমিকে বাজেয়াপ্ত না করা।
ইলবার্ট বিল কী ?
উত্তরঃ ভারতীয় কোনো বিচারকের ব্রিটিশদের বিচার করার অধিকার ছিল না। লর্ড রিপনের শাসনকালে আইন সচিব ইলবার্ট একটি বিল দ্বারা ভারতীয় বিচারকদের এই অধিকার প্রদান করেন যা ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত।
কারা, কেন সিপাহি বিদ্রোহকে সামন্তশ্রেণির বিদ্রোহ বলেছেন?
উত্তরঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে সিপাহি ছাড়াও জমিদার, প্রাদেশিক শাসক সহ সামন্তশ্রেণির মানুষেরা ব্যাপকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই কারণে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, রজনীপাম দত্ত প্রমুখ এই বিদ্রোহকে সামন্তশ্রেণির বিদ্রোহ বলেছেন ।
বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর
জমিদার সভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। অথবা, টীকা লেখো : জমিদার সভা অথবা, জমিদার সভার কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করো।
উত্তর
সূচনাঃ ঊনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যেসকল সভাসমিতি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল জমিদার সভা। 1838 সালের 12 নভেম্বর জমিদার সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
প্রতিষ্ঠাতাঃ জমিদার সভা প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ মিত্র প্রমুখ।
জমিদার সভার লক্ষ্যঃ 1838 সালে প্রতিষ্ঠিত জমিদার সভার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল মূলত জমির সাথে যুক্ত মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করা। যেমন—জমিদারদের স্বার্থরক্ষা এবং নিষ্কর জমিতে কর বসানোর ব্যবস্থা করা, বিচারবিভাগ, পুলিশবিভাগ, ও রাজস্ববিভাগের সংস্কার করার জন্য জনমত গঠন করা।
জমিদার সভার কাজঃ (i) সমর্থন লাভের প্রয়াস : এই সভা ভারতীয়দের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আসার চেষ্টা করে। (ii) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার : জমিদার সভার অন্যতম কাজ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতের সর্বত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা করা ।
মূল্যায়নঃ জমিদার সভা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা স্থাপন করে সেইসব অঞ্চলের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয় । এই সংগঠন সকলের মধ্যে ঐক্যভাব গড়ে তোলার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে—“এই প্রতিষ্ঠানই হলো ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত।”
‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা‘কে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন ?
অথবা, ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা‘ সম্বন্ধে যা জানো লেখো। অথবা, টীকা লেখো—‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা‘।
উত্তর
সূচনাঃ ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ব্রিটিশ সরকার বাংলার জমিদারদের অধিকৃত নিষ্কর জমি পুনর্গ্রহণের প্রস্তাব তোলে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গঠিত বাংলার রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো ছিল ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা‘।
প্রতিষ্ঠাঃ 1836 খ্রিস্টাব্দে টাকির জমিদার কালীনাথ চৌধুরী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্যারীমোহন বসু, রামলোচন ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন এবং প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।
প্রথম অধিবেশনঃ পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে—“এই সভা প্রতিষ্ঠার সঠিক সন–তারিখ আমরা জানিতে পারি নাই।” তবে এই সভার প্রথম অধিবেশন বসে 1836 খ্রিস্টাব্দের 6/8 ডিসেম্বর।
উদ্দেশ্যঃ মূলত নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল—কোম্পানি নিষ্কর ভূমির ওপর কর নেওয়া শুরু করলে তার বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদ করা; ভারতবাসীর মঙ্গল–অমঙ্গলকারী বিষয়গুলির আলোচনা ও পর্যালোচনা করা; বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা; রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা প্রভৃতি।
কার্যাবলিঃ ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা‘ সভার সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের আলোচিত বিষয় ও বিতর্কের দিকে খেয়াল করলে স্বদেশভাবনা ও রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনার দিক থেকে এটিকে তৎকালীন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলা যায়।
মূল্যায়নঃ অল্পসময়ের মধ্যে ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অবলুপ্তি ঘটলেও এটি তৎকালীন ভারতে বিশেষ করে বাংলায় বাঙালি তথা ভারতবাসীর প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। জনগণের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকারের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধনে এই সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।
ভারতসভার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
জাতীয়তাবাদের উত্থানে ভারতসভার ভূমিকা কী ছিল?
অথবা, জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর
সূচনাঃ 1876 খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ভারতসভা প্রাক্কংগ্রেস যুগে সর্বভারতীয় রাজনীতিকে গতিশীল করেছিল।
প্রতিষ্ঠাঃ 1876 খ্রিস্টাব্দের 26 জুলাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতসভা প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ।
উদ্দেশ্যঃ ভারতবর্ষজুড়ে হিন্দু–মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে একটি শক্তিশালী জনমত গঠন করা ছিল ভারতসভার প্রধান উদ্দেশ্য। এ ছাড়া
সিভিল সার্ভিসঃ ব্রিটিশ সরকার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়সসীমা 21 থেকে কমিয়ে 19 করলে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতসভা জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করে।
ইলবার্ট বিল আন্দোলনঃ ইলবার্ট বিল–এর দ্বারা লর্ড রিপন ইংরেজদের বিচার করার অধিকার ভারতীয়দের হাতে দিলে ইউরোপীয়রা এর প্রতিবাদ জানায়। ভারতসভা এই বিলকে সমর্থন করে পালটা আন্দোলন শুরু করে।
মূল্যায়নঃ সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতসভা একের পর এক ব্রিটিশবিরোধী কর্মসূচির দ্বারা সমগ্র ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করে। অবশেষে 1883 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনের প্রেরণায় অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম 1885 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় কংগ্রেস।
1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের কীরূপ মনোভাব ছিল ?
উত্তর
সূচনাঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথম অবস্থায় সিপাহিদের দ্বারা শুরু হলেও কৃষক, কারিগর, শ্রমিক, শিল্পী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত | শিক্ষিত সমাজের মানুষ এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি বরং তারা আন্দোলনের সাথে যুক্ত নেতাদের ব্যঙ্গ করেছিল।
মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব
অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির বিরূপ মনোভাবঃ সিপাহি বিদ্রোহের সময় শিক্ষিত বাঙালি| সমাজ ব্রিটিশ শাসনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কারণ তারা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সরকারি চাকরির প্রতি অনুরক্ত ছিল।
মধ্যযুগীয় শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভয়ঃ শিক্ষিত সমাজের মানুষের ধারণা ছিল বিদ্রোহীরা জয়লাভ করলে মধ্যযুগীয় বর্বরতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তারা বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি।
আধুনিকতা অবসানের ভয়ঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কারের সমর্থক। তারা মনে করত সিপাহি বিদ্রোহীরা সাফল্য পেলে আধুনিকতার অবসান ঘটবে। তাই তারা বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি।
মূল্যায়নঃ সিপাহি বিদ্রোহের শেষ পর্বে ব্রিটিশ সরকার যখন কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্রিটিশদের প্রতি মোহভঙ্গ হয়। তারা অনুভব করে যে ব্রিটিশ শাসন কখনো ভারতবাসীর কল্যাণ করতে পারে না।
জাতীয়তাবাদের প্রসারে হিন্দুমেলার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
অথবা, হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল ?
অথবা, উনিশ শতকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের বিকাশে হিন্দুমেলার অবদান লেখো।
অথবা, টীকা লেখো : হিন্দুমেলা।
উত্তর
সূচনাঃ 1858 সালে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা হস্তান্তরিত হয়েছিল। এইসময়ে ভারতবর্ষে যেসকল সভাসমিতি ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব প্রস্তুতে সহায়ক ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল হিন্দুমেলা। 1867 খ্রিস্টাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে এর প্রথম অধিবেশন বসেছিল বলে একে চৈত্রমেলাও বলা হয়ে থাকে।
প্রতিষ্ঠাঃ রাজনারায়ণ বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের উদ্যোগে 1867 খ্রিস্টাব্দে হিন্দুমেলা নামে এক বার্ষিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নবগোপাল মিত্র ছিলেন হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তা। প্রথমদিকে হিন্দুমেলার সম্পাদক ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহসম্পাদক ছিলেন নবগোপাল মিত্র ।
প্রধান উদ্দেশ্যঃ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে স্বদেশি আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করা, ভারতের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা; হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটিয়ে হিন্দুদের জাগরণ; দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটানো। হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গগনেন্দ্রনাথ বলেছেন—“আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম–কর্মের জন্য নহে, কোনো বিষয়সুখের জন্য নহে, কোনো আমোদ–প্রমোদের জন্যও নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারতভূমির জন্য।”
কার্যাবলিঃ হিন্দুমেলার কার্যাবলির মধ্যে ছিল হিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষভাব প্রতিষ্ঠা করা। এ ছাড়া হিন্দুসমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণী তৈরি করা। এই সংগঠন সম দূর করে ঐক, আি সদস্যদের যোগব্যায়াম, লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দিত। এই উদ্দেশ্যে 1868 খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র ‘ন্যাশনাল জিমনেশিয়াম‘ নামক শারীরশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।
মূল্যায়নঃ উপরিউক্ত বিষয় ছাড়াও হিন্দুমেলার মাধ্যমে তৎকালীন ভারতের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় বিশ্লেষণ করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতবর্ষে বাঙালিদের জাতীয় চেতনা জাগরণে হিন্দুমেলার অবদান চিরস্মরণীয়।
1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বা সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ লেখো।
উত্তর
সূচনাঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের 29 মার্চ শুরু হওয়া সিপাহি বিদ্রোহ খুব অল্পসময়ে দ্রুত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক গণআন্দোলনে পরিণত হয়। যদিও গোর্খা বাহিনীর সাহায্যে ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহ স্তব্ধ করেছিল। এর কারণ হিসেবে বলা যায়—
বিদ্রোহের বিচ্ছিন্নতাঃ ভারতের সর্বত্র বিদ্রোহ একযোগে না হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে এই বিদ্রোহ হয়। ফলে ইংরেজদের পক্ষে বিদ্রোহ দমন করা খুব সহজ হয়ে ওঠে।
সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবঃ সিপাহি বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপি প্রমুখ সাহসী ও সমরকুশলী হলেও ইংরেজ সেনাপতি লরেন্স, হ্যাভলক, আউটরাম প্রমুখের মতো সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল বিদ্রোহীদের মধ্যে। একে অনেকে এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলে মনে করেছেন।
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবঃ বিদ্রোহীরা জনগণের কাছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য তুলে ধরতে পারেননি যা ছিল বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।
সংকীর্ণতাঃ সিপাহি বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে আঞ্চলিক স্বার্থ ও সংকীর্ণতা বিদ্যমান থাকায় তাঁরা সর্বত্র একই নীতি অনুসরণ করতে পারেননি।
মূল্যায়নঃ এই আলোচনায় স্পষ্ট যে সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতা ছিল একাধিক কারণের যৌগিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের পরিচয় দাও ।
অথবা, ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রসারে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের প্রভাব আলোচনা করো।
অথবা, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে তাঁর অঙ্কিত সামাজিক সমস্যামূলক ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা করেছেন?
উত্তর
সূচনাঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনকালে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর আঁকা ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে সমকালীন | সমাজের সমালোচনা ও বিদ্রুপ লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় ঘরানার এক বিশিষ্ট চিত্রকর ও ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী হিসেবে গগনেন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য। এ কারণে তাঁকে আধুনিক চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ বলা হয় ৷
ব্যঙ্গচিত্রে সমকালীন সামাজিক প্রতিচ্ছবিঃ গগনেন্দ্রনাথ তাঁর কার্টুনচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন ঔপনিবেশিক সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা, মন্দিরে পান্ডাদের দৌরাত্ম্য, ব্রাক্ষ্মণশ্রেণির অত্যাচার, বাল্যবিধবাদের দুরবস্থা, বাঙালি মধ্যবিত্ত বাবুদের ইংরেজপ্রীতি। তিনি ‘জাতাসুর‘ নামক ব্যঙ্গচিত্রে দেখিয়েছেন সমাজের বর্ণবৈষম্যের ভয়াবহতা।
বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্রঃ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে ‘অদ্ভুত লোক “বিরূপ বজ্র’এবং ‘নয়া হুল্লো উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিদ্যা কারখানা, জাতাসুর, বাগ্যন্ত্র প্রভৃতি তৎকালীন সমাজে সাড়া জাগিয়েছিল।
পাশ্চাত্য ভাবধারার সমালোচনাঃ বিংশ শতকে বাংলার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কঠোর অনুরাগী বাঙালি সমাজের তীব্র সমালোচনা করেন গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে।
মূল্যায়নঃ কেবলমাত্র বাংলায় নয় সমগ্র ভারতবর্ষেই গগনেন্দ্রনাথ একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে ব্যঙ্গচিত্রের মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আসলে তিনি নিম্নরুচির ও নারীর প্রতি কুদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কঠোর সমালোচনা করেছেন তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে।
টীকা লেখো—মহারানির ঘোষণাপত্র।
অথবা, মহারানির ঘোষণাপত্রের (1858 খ্রিস্টাব্দ) ঐতিহাসিক তাৎপর্য লেখো।
উত্তর
সূচনাঃ স্বাধীনতার পূর্বে সংঘটিত বিদ্রোহগুলির মধ্যে প্রথম সর্বভারতীয় স্তরের বিদ্রোহ ছিল 1857 খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ। সমকালীন ইতিহাসবিদদের মতে, এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই বিদ্রোহের চাপে পড়েই 1858 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর ইংল্যান্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতশাসন সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করেন যা ‘মহারানির ঘোষণাপত্র‘ নামে পরিচিত।
ঘোষণাপত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য
E.I.C. শাসনের অবসানঃ এই ঘোষণাপত্র অনুসারে স্থির হয় ভারতবর্ষের মতো সুবিশাল দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (EI.C.) শাসনের অবসান হবে এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেবে।
অন্যান্য শর্তঃ প্রথমত, এই ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং দেশীয় রাজাদের দত্তক পুত্রগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়।
দ্বিতীয়ত, স্থির হয় ভারতবাসীর সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না।
তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে ভারতে কোনো সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হবে।
চতুর্থত, কোম্পানির সঙ্গে স্বাক্ষরিত দেশীয় রাজন্যবর্গের চুক্তি ও সন্ধিগুলিকে মান্যতা দেওয়া হবে।
মন্তব্যঃ বলা হয়, মহারানির ঘোষণাপত্রের এইসব প্রতিশ্রুতি কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতিই ছিল। তা বাস্তবে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এরই ফলশ্রুতিতে শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে তীব্র ক্ষোভ, হতাশা, ঘৃণার সঞ্চার হয় যা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।
রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর
‘গোরা‘ উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথের যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করো।
অথবা, ‘গোরা‘ উপন্যাস ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশে কী ভূমিকা নিয়েছিল?
উত্তর
সূচনাঃ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি গঠনে ঊনিশ শতকের ভারতে যেসব উপন্যাস গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা‘ উপন্যাস। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন ভারতীয় সমাজের অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণে ভারতআত্মার এক চিরন্তন বাণী প্রতিফলিত করেছেন।
প্রকৃত ভারতের রূপঃ এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা। তৎকালীন গ্রাম্যসমাজের সাধারণ মানুষের সুখ–দুঃখের খোঁজখবর নিতে গিয়ে তিনি সত্যিকারের ভারতীয় সমাজের রূপটি চিনতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে যা ছিল উদার প্রেমভিত্তিক বিশ্বমানবতার আদর্শ।
গোরার আঘাতঃ গোরা উপলব্ধি করেছিলেন তৎকালীন শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেয়ে পল্লিগ্রামের মানুষের সামাজিক বন্ধন অনেক তীব্র। তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কারই যে গ্রাম্যসমাজের বিভাজন তৈরি করে তা তিনি স্পষ্ট করেছেন। গোরা এইরূপ সমাজের ওপর তীব্র আঘাত হানেন ।
জাতীয়তাবাদ বিকাশেঃ হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকাশে ‘গোরা’ উপন্যাসটি সহায়ক হয়েছে। জাতপাতের গণ্ডি জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না এবং তা যে অসাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করতে সহায়ক হয়ে পর উঠতে পারে, গোরা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণ হয়।
উদারতার প্রতিফলনঃ ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজের মধ্যে বিরোধ দেখাতে গিয়ে উপন্যাসটির কিছু অংশে হিন্দুসমাজের উদারতা ও তার দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।
ধর্মীয় পরিচয়ের গুরুত্বহীনতাঃ ধর্মীয় পরিচয়–ই যে একমাত্র বা সবচেয়ে বড়ো পরিচয় নয় সেকথা স্পষ্টভাবে ‘গোরা‘ উপন্যাসের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি সমাজকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন।
আক্রমণের বিরোধিতাঃ ‘গোরা‘ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষে মুগ্ধ হন এবং সংকল্প করেন যে স্বদেশের প্রতি স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা তিনি ফিরিয়ে আনবেনই, তারপর অন্য কাজ। হিন্দু সভ্যতার বিরোধী জনৈক মিশনারির বিরুদ্ধে তিনি সম্মুখ বিতর্কে অংশগ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেন।
মূল্যায়নঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাসের হিংসাত্মক জাতীয়তাবাদ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। কিছু ইতিহাসবিদদের মতে, তারই প্রতিবাদে যেন ‘গোরা‘ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতাবাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মিল দেখিয়েছেন।
উনিশ শতককে সভাসমিতির যুগ বলা হয় কেন ?
উত্তরঃ উনিশ শতকে ভারতে একদিকে ব্রিটিশের শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার বৃদ্ধি, অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, যুক্তিবাদের উন্মেষ, জাতীয়তাবাদের প্রসার ইত্যাদির ফ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এই ঘটনাকে কেমব্রিজ ইতিহাসবিদ ড. অনিল শীল ‘সভাসমিতির যুগ‘ বা Age of Association বলে উল্লেখ করেছেন।
সভাসমিতি প্রতিষ্ঠাঃ উনিশ শতকে গড়ে ওঠা সভাসমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ __হলো—বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (1836 খ্রিস্টাব্দে), জমিদার সভা (1838 খ্রিস্টাব্দে), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (1839 খ্রিস্টাব্দে), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (1843 খ্রিস্টাব্দে, হিন্দুমেলা (1857 খ্রিস্টাব্দে), ইন্ডিয়ান লিগ (1875 খ্রিস্টাব্দে), ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান (1876 খ্রিস্টাব্দে) প্রভৃতি ।
সভাসমিতির বৈশিষ্ট্যঃ সভাসমিতিগুলি প্রথমে বাংলায় পরে বাঙালির অনুকরণে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পর্বের সভাসমিতিগুলি ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করা ছিল সভাসমিতিগুলির উদ্দেশ্য।
গুরুত্বঃ জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারে ও ব্রিটিশবিরোধী জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এইসব সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।
সভাসমিতির চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। দেশের স্বার্থরক্ষা ও সরকারের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য সভাসমিতিগুলি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।
মূল্যায়নঃ সভাসমিতি প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ প্রথমে আঞ্চলিকভাবে, পরে জাতীয়স্তরে ঐক্যবদ্ধ হয় যা সর্বভারতীয় আন্দোলন সংগঠিত করার পথ প্রশস্ত করে। অনিল শীল তাঁর ‘The Emergence of Indian Nationalism’ গ্রন্থে লিখেছেন, সমিতির মাধ্যমেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত আধুনিক রাজনীতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে।
1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।
অথবা, সংক্ষেপে মহাবিদ্রোহের (1857) চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
অথবা, 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ ঘিরে ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতদের মধ্যে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার পরিচয় দাও।
উত্তর
সূচনাঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ বাংলার ব্যারাকপুরের সেনা প্রশিক্ষণ শিবিরের সিপাহিদের নেতৃত্বে শুরু হয়। খুব অল্পসময়েই এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই বিদ্রোহে যোগদান করে। একারণে সিপাহি বিদ্রোহের চরিত্র বা প্রকৃতি নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। এই বিদ্রোহ প্রায় সকল শ্রেণির মানুষের যোগদানে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।
সিপাহি বিদ্রোহের প্রকৃতিঃ কিছু ইতিহাসবিদ ও গবেষক মনে করেন সিপাহি বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁদের মতামত এইরকম—
সামন্ত বিদ্রোহঃ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, রজনীপাম দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ মনে করেন, 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ ছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বা সনাতনপন্থীদের বিদ্রোহ। কারণ কোম্পানির বিভিন্ন নীতির দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত শাসকেরা যেমন—রানি লক্ষ্মীবাই, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি সহ অনেক প্রাদেশিক শাসক এই বিদ্রোহে শামিল হন।
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এই মত স্বীকার করেন না। কারণ না ছিল বিদ্রোহীদের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য, না এই বিদ্রোহ থেকে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। এ ছাড়া অনেক ভারতীয় রাজা, শিখ ও গোর্খা সৈনিকরা ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন।
গণবিদ্রোহঃ জন কে., সি.এ. বেইলি, বল প্রমুখ 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে গণবিদ্রোহ বলার পক্ষপাতী। কারণ সিপাহিদের সাথে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এই বিদ্রোহকে গণবিদ্রোহের রূপ দিয়েছিল। এ ছাড়া মুজফফরনগর, অযোধ্যা, কানপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহে গণবিস্ফোরণ ঘটে।
সিপাহি বিদ্রোহঃ 1857 খ্রিস্টাব্দে ভারতসচিব আর্ল স্ট্যানলি তাঁর এক প্রতিবেদনে এই বিদ্রোহকে ‘Sepoy Mutiny’ বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের অভিমত হলো সিপাহিরা বিদ্রোহের সূচনা করে কিন্তু দেশের সকল শ্রেণির মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির এতে যোগদান ঘটেনি। এ ছাড়া এই বিদ্রোহের মূলে কোনো রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল না।
জাতীয় বিদ্রোহঃ ডিসরেলি, আউটরাম, নর্টন, ডাফ প্রমুখ 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মুজফফরনগর প্রভৃতি স্থানে সিপাহি নেতৃত্ব ছাড়াও স্থানীয় রাজন্যবর্গ–জমিদাররা বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে বিদেশি শাসনমুক্ত একটি দেশীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হন ৷
মহাবিদ্রোহঃ ভারতের বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ বিদ্রোহের ব্যাপকতা লক্ষ করে এই বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছিলেন। এরিখ স্ট্রেস বলেছেন যে এই বিদ্রোহ ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের শেষ অধ্যায়।
মূল্যায়নঃ উপরিউক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে সিপাহিদের অসন্তোষ মূল কারণ হলেও এই বিদ্রোহের মূলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের গভীর অসন্তোষ ও হতাশা।অধ্যাপক রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্র প্রমুখ ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের গণচরিত্রের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।
লেখায় ও রেখায় ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ আলোচনা করো।
অথবা, ভারতে জাতীয়তাবাদ বিকাশে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অবদান লেখো।
উত্তর
সূচনাঃ পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনে ও শোষণে অতিষ্ঠ ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশার ঘটনা বিকাশে সাহিত্য–সংস্কৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। বিভিন্ন সাহিত্যিক ও শিল্পী তাঁদের দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ তথা জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আর এই জাতীয়তাবাদের লেখনী ও চিত্রকলার দ্বারা ভারতীয়দের মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন।
লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবাদের বিকাশঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ – যেসকল লিখিত উপাদান ভারতবাসীর মনে গভীর দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় তার মধ্যে ‘আনন্দমঠ’ অন্যতম। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় আনন্দমঠ উপন্যাসটি রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই বিখ্যায় উপন্যাসে দেশমাতৃকার যে বর্ণনা প্রদান করেন এবং যেভাবে দেশপ্রেমকে মুক্তিকামী জনগণের মধ্যে পরিস্ফুট করেছেন তা অকল্পনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসে ‘বন্দেমাতরম্‘ সংগীতে দ্বারা দেশাত্মবোধের মন্ত্র প্রদান করেছেন।
স্বামী বিবেকানন্দের ‘বর্তমান ভারতঃ ‘বর্তমান ভারত‘ গ্রন্থে স্বামীজি ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস মন্থন করে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে সংগত আকারে প্রকাশ করেছেন। তিনি ভারতীয় যুবসমাজকে তাঁর লেখার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ রচিত ‘বর্তমান ভারত‘ গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের মতোই সংক্ষিপ্ত এবং তার জীবনের মতোই শক্তি ও সম্ভাবনায় স্পন্দিত।
রবীন্দ্রনাথের ‘গোরাঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা ‘গোরা’ উপন্যাসের বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ জাগরণের এক মঞ্চ প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্যের পরিচয় ও দেশপ্রেমের আদর্শ তুলে ধরার মাধ্যমে ভারতবর্ষ তথা বাংলাকে বিশ্বের মানুষের কাছে জ্যোতির্ময়ী করে তুলেছিলেন।
অবনীন্দ্রনাথের ‘ভারতমাতা‘ চিত্রঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র হলো ‘ভারতমাতা’। যেখানে তুলির টানে তিনি দেশমাতৃকার বন্দনা করেছেন। এই চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য যথাযোগ্যভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শুধুমাত্র লেখার মাধ্যমে নয়, রেখার দ্বারাও জনমানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রঃ শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নন বিশ্বের জনপ্রিয় ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে তিনি সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীদের মধ্যে একজন। সমকালীন সময়ে তিনি ইংরেজদের অত্যাচার, জমিদারদের আচরণ, সাধারণ মানুষদের অবস্থা তাঁর শিল্পীসত্তার মাধ্যমে ব্যঙ্গাত্মক রূপে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর এরূপ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গচিত্র হলো—বিরূপ বজ্র, নবহুল্লোড়, ভোঁদড় বাহাদুর প্রভৃতি ।
মন্তব্যঃ এইভাবে দেশীয় লেখক ও সাহিত্যিক এবং চিত্রশিল্পী ও ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীরা তাদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করেছেন। ফলস্বরূপ একের পর এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে আজকে আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষে বসবাসের সুযোগ লাভ করেছি।
1857 সালের মহাবিদ্রোহের তাৎপর্য কী ?
উত্তর
সূচনাঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও নিষ্ফল ছিল না। বিদ্রোহের ঝড় থেকে ব্রিটিশ শাসন আপাতত রক্ষা পেলেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নতুন ভিত্তি গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেজন্যই স্যার লেপেল গ্রিভিন মন্তব্য করেছেন, “মহাবিদ্রোহ ভারতের আকাশ থেকে বহু মেঘ দূরে সরিয়ে দেয়।”
কোম্পানির শাসনের অবসানঃ মহাবিদ্রোহের তীব্রতা ও ভয়াবহতায় ব্রিটিশ সরকার বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতের শাসনভার কোম্পানির হাতে না রেখে ব্রিটিশ সরকারের হাতে নেওয়ার দাবিতে ইংল্যান্ডের জনগণ সরব হয়। 1858 খ্রিস্টাব্দের ভারতশাসন আইন দ্বারা ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের মহারানির ওপর বর্তায় ও কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। কিথ এই ক্ষমতার হস্তান্তরকে “more nominal than real” বলে অভিহিত করেছেন।
মহারানির ঘোষণাপত্রঃ মহাবিদ্রোহের পরবর্তীতে তড়িঘড়ি ব্রিটিশ সরকার 1858 খ্রিস্টাব্দের 1 নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্র জারি করে।
(iii) ভারতের ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ না করা।
(iv) জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার অধিকারদান প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
প্রশাসনিক পরিবর্তনঃ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কিছু আইন ও সনদ আইন পাশ করা হয়। 1833 খ্রিস্টাব্দে পাশ হওয়া সনদ আইনে যে কেন্দ্রীকরণ নীতির প্রস্তাব ছিল 1861 সালে এক কাউন্সিল আইন পাশ করে তা বাতিল করা হয়। পরিবর্তে প্রশাসনকে জাতীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করা হয়।
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। তাই 1859 সালে জেমস উইলসন গভর্নর জেনারেলের অর্থনৈতিক সদস্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি আয়কর প্রবর্তন করেন, সমস্ত দ্রব্যের ওপর 10 শতাংশ আমদানি শুল্ক বসান, কাগজের নোট চালু করেন এবং কর্মচারীর সংখ্যাহ্রাস করে ব্যয়হ্রাস করার পরিকল্পনা করেন। উইলসনের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় পরবর্তী অর্থনৈতিক সদস্য স্যামুয়েল লেইং উইলসনের নীতি অব্যাহত রাখেন এবং তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করেন।
সামরিক সংস্কারঃ বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যেগ নেয়। ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ইংরেজ ও সিপাহি বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেশে ব্রিটিশ সরকার সামরিক ইউরোপীয় সেনার সংখ্যা বাড়ানো হয়। শ্বেতাঙ্গ সেনার সংখ্যা 45000 থেকে বাড়িয়ে 65000 করা হয়। আর ভারতীয় সেনার সংখ্যা 238000 থেকে কমিয়ে 140000 করা হয়। গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ বন্ধ করা হয় ।
মূল্যায়নঃ পরিশেষে বলা যায়, 1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ‘After Mass of the Revolt’ গ্রন্থে চার্লস মেটকাফ বলেছেন, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বর্ণজনিত ব্যবধান মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পরে অঘোষিত রূপ নেয়। মানবিক সম্পর্কের এই অবনমনই মহাবিদ্রোহের প্রধান উত্তরাধিকার।
দেশপ্রেম বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের ভূমিকা কী ছিল ?
অথবা, ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাস ও ‘বর্তমান ভারত গ্রন্থ কীভাবে জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিস্তারে সাহায্য করেছিল?
উত্তর
সূচনাঃ ঊনবিংশ শতকে ভারতবাসীর নেতৃত্বে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুতে যেসকল ব্যক্তির অবদান গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাসে এবং বিবেকানন্দ তাঁর ‘বর্তমান ভারত‘ গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সমগ্র ভারতবাসীকে মানসিকভাবে শক্তি জুগিয়েছিলেন।
বঙ্কিমচন্দ্র ও আনন্দমঠ গ্রন্থ
পটভূমিঃ 1176 বঙ্গাব্দে বাংলায় যখন 76-এর মন্বন্তর নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ঠিক সেইরকম পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি রচনা করেন।
‘আনন্দমঠ‘-এর উদ্দেশ্যঃ ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাসটি রচনার মধ্য দিয়ে লেখক ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। দেশবাসীকে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন।
ব্রিটিশ শাসনের দুর্দশার চিত্রঃ ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন ভারতবাসীর সামনে পরাধীন ভারতমাতার দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বৈরাচারী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ৷
দেশমাতার আদর্শঃ ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— “দেশমাতা হলেন মা, দেশপ্রেম হলো ধর্ম, দেশসেবা হলো পূজা।”
বন্দেমাতরম সংগীতঃ ‘আনন্দমঠ‘ উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বন্দেমাতরম সংগীত যা ছিল সমকালীন পরাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত তথা বিপ্লবীদের মন্ত্র। 1907 খ্রিস্টাব্দে মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা রূপায়িত ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকায় এই ধ্বনি স্থান পেয়েছে।
বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত গ্রন্থঃ
স্বদেশপ্রেম জাগরনঃ সমগ্র দেশবাসীকে দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া বা নিজের দেশকে ভালোবাসার মনোভাব প্রস্তুতে ‘বর্তমান ভারত‘ গ্রন্থের অবদান কোনো অংশে কম নয়। এই গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশমন্ত্ৰতে লিখেছেন —“বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ” এই বাণীর মাধ্যমে বিবেকানন্দ ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের জাগরণ ঘটান।
আত্মনির্ভরশীল হওয়াঃ ‘বর্তমান ভারত‘ গ্রন্থে বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মন্ত্র দিয়েছেন। তিনি সকল ভারতবাসীকে কাপুরুষতা দূর করে আত্মশক্তি ও আত্মবললাভের কথা বলেছেন। তিনি বিদেশি সংস্কৃতি বর্জন করে প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অনুকরণ ও অনুসরণ করার প্রস্তাব দেন এই গ্রন্থে।
সৌভ্রাতৃত্বের সজ্ঞারঃ ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থে লিখেছেন – “ …… বল আমি ভারতবাসী, প্রতিটি ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র কাঙাল ভারতবাসী, ব্রাক্ষ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই।” অর্থাৎ সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরি করার ডাক দিয়েছেন তিনি।
1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা যায় কি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
উত্তর
সূচনাঃ 1857 খ্রিস্টাব্দে সিপাহিদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া বিদ্রোহ খুব অল্পসময়ের মধ্যেই প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের তীব্রতা ও প্রসার লক্ষ করে বিভিন্ন ইতিহাসবিদ এর বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। যেমন—বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর ‘দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইনডিপেন্ডেন্স‘ গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ‘ বলে উল্লেখ করেছেন।
পক্ষে মতামতঃ যে–সমস্ত ব্যক্তিত্ব 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন তাঁদের মতামত ছিল এইরকম–
প্রথমত, বেশ কিছু পণ্ডিতের মতে, 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহিরা শুরু করলেও তা শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে উন্নীত হয়েছিল। এটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিবাদ।
দ্বিতীয়ত, সাভারকর বলেছেন—সিপাহিদের নেতৃত্বে ভারতীয়রা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এত ব্যাপক ব্রিটিশবিরোধী গণআন্দোলন ভারতে ইতিপূর্বে হয়নি।
তৃতীয়ত, ড. সুশোভন সরকার বলেন, 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে মুক্তিযুদ্ধ না বলা অযৌক্তিক। তাঁর মতে, যদি 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম বলে স্বীকার করা না হয় তাহলে ইটালির মুক্তিযুদ্ধ বলে সেখানকার কার্বোনারি আন্দোলনকেও স্বীকার করা যাবে না।
চতুর্থত, ‘1857 in Our History’ নামক প্রবন্ধটিতে পি. সি. জোশি 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে সমর্থন জানিয়েছেন।
পঞ্চমত, লন্ডনে আয়োজিত সিপাহি বিদ্রোহের এক স্মরণসভায় ভারতীয় বিপ্লবীরা একে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন। কারণ সিপাহি বিদ্রোহ সিপাহিদের দ্বারা শুরু হলেও তা কেবলমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই বিদ্রোহে ব্রিটিশবিরোধী স্লোগান তুলেছিল।
ষষ্ঠত, কার্ল মার্কসও 1857 খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতীয়দের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন।
মন্তব্যঃ 1857 খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ‘ বলে কেউ কেউ মেনে না নিলেও একথা বলা যায়, 1857-র পরবর্তীকালের স্বাধীনতা আন্দোলনগুলি সিপাহি বিদ্রোহ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল—এই কারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম।