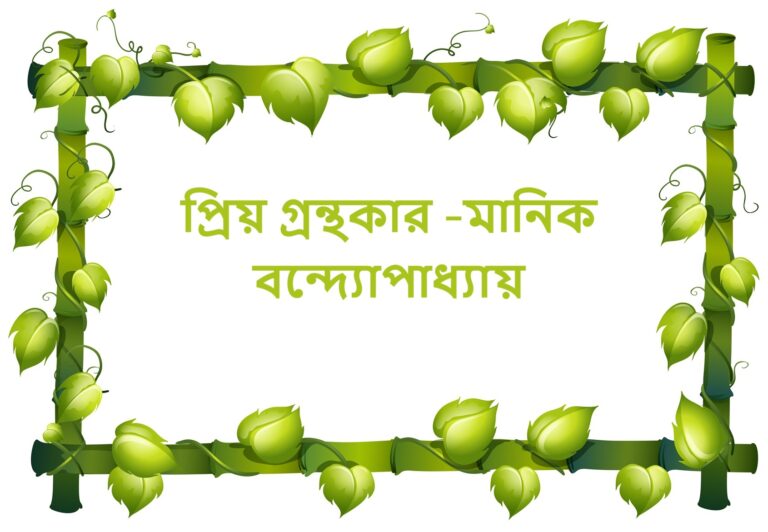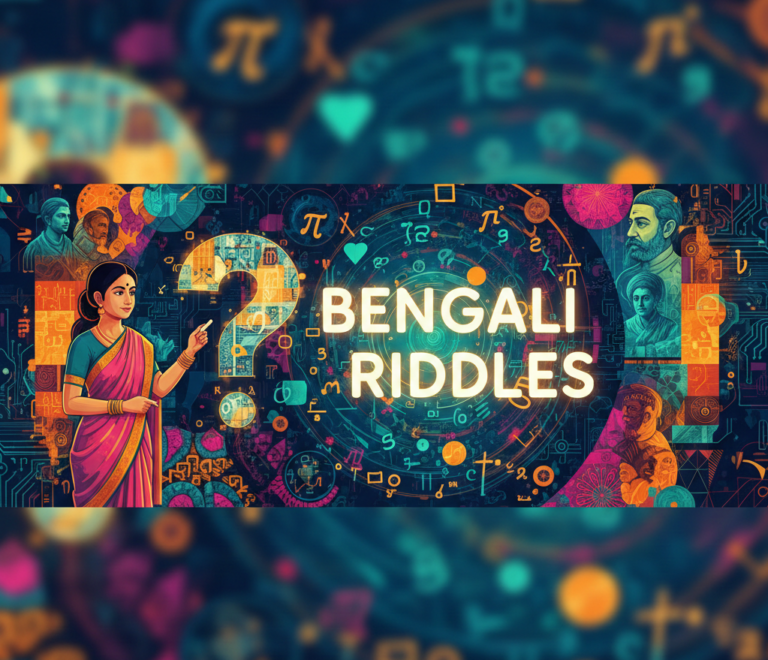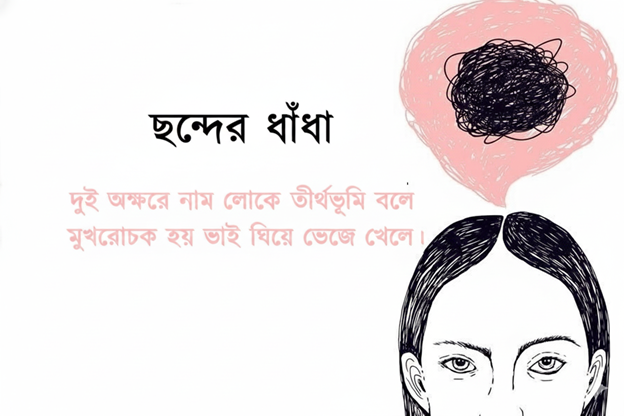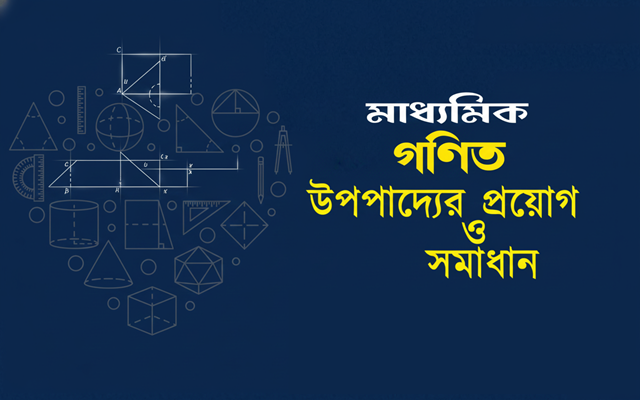গ্রাম উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক
Gram unnayane gramin bank-Rochona Bengali
[ ভূমিকা— ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ইতিহাস–ব্যাঙ্কের কাজ— গ্রামীণ অর্থনীতির দূরাবস্থা দূরীকরণ—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখা– গ্রামীণ ব্যাঙ্ক —ভাসমান ব্যাঙ্ক—উপসংহার ]
ভূমিকাঃ দেশের বিশেষ করে সভ্য দেশের অর্থনৈতিক চলমানতার মূল স্নায়ু কেন্দ্র তার ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা। ব্যাঙ্কই হচ্ছে এমন এক প্রতিষ্ঠান যে একদিকে জনসাধারণের অর্থ সঞ্চয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে এবং সঞ্চিত অর্থের সুদ প্রদানে সঞ্চয়কে উৎসাহ দেয় । অন্যদিকে আমানতের টাকা বিভিন্ন শিল্পে বাণিজ্যে নিয়োগ করে দেশের সার্বিক উৎপাদন কর্ম নির্বাহ করে থাকে। আধুনিক যুগে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতি তার আর্থিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার সুযোগ পায় । যন্ত্র যুগেও শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে পাশ্চাত্ত্য দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নততর হয়েছে । তবে ব্যাংকের এই প্রতিষ্ঠা সবই প্রায় শহর কেন্দ্রিক হওয়ায় সংযোগ পেয়েছে শহরের বণিক ও শিল্পপতিরা । গ্রামের ধনী জমিদার, জোতদার ও সম্পন্ন চাষীরা তাদের ধন নিরাপদ স্থানে গচ্ছিত রাখতে শহরে ছুটে যেতে হয়। আর শহরের তথা দেশের আর্থিক বুনিয়াদ সদৃঢ় করতে যে গ্রাম তার সব কিছু উজাড় করে দিচ্ছে—সেই গ্রাম ও গ্রামের অর্থ নীতি কিভাবে টিকে থাকতে পারে যদি গ্রামের মানুষ তথা গ্রামের অর্থ নীতি বিকল হয়ে যায় । সেই কারণেই আজ গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যাংক ব্যবস্থাকে । ব্যাংক যত তাড়াতাড়ি সমাজের অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পারবে—গ্রাম প্রধান ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি তত শীঘ্র সাধিত হবে ।
ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাসঃ ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রাচীন, খুবই প্রাচীন। ‘ব্যাঙ্ক‘ এই শব্দটি ইংরেজ আমলের । পূর্বে গ্রামীণ অর্থনীতিকে, গ্রামের দরিদ্র কৃষক কুলকে, গ্রামের ছোট শিল্পকে অর্থ সাহায্য করত এক শ্রেণীর বৈশ্য যারা “শ্রেষ্ঠী”( শেঠ) নামে পরিচিত ছিল। গরীব, কৃষকেরা, শিল্পী সম্প্রদায় এদের লগ্নী করা অর্থেই ক্ষেতে সোনা ফলাতো ও উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যে বিদেশীদের মুগ্ধ করত। প্রাচীনকালের এই ধারণাই মধ্য যুগে ও আধুনিক যুগের একেবারে গোড়ার দিকে মহাজনরপে দেখা দেয়। এরাই পরবর্তীকালে গরীব প্রজার কল্যাণের পরিবর্তে তাদের অর্থে‘র ঋণ বণ্টন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর কোরে তোলে। মহাজনদের অত্যাচারে দরিদ্র প্রজাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠে । এদের উদ্ধার করার জন্যই এদেশে সবার আগে প্রথমে সমবায় প্রথা এবং তার পরেই ব্যাংক ব্যবস্হা প্রচলন হয়। ইষ্ট–ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে, ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় আমাদের দেশের মধ্যে আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্হার প্রথম সূত্রপাত হয় ।
গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির নানা সপোরিশঃ আধুনিক যুগে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আশীর্বাদ শহরের মানুষই বেশী করে পেয়েছে । গ্রামের গরীব মানুষদের বেশীর ভাগকেই মহাজনী ব্যবস্থার শিকার হয়ে দুঃসহ কষ্ট দীর্ঘকাল ভোগ করতে হয়েছে । তবে ইদানিং কালে গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছ, জমি বন্দকী ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকের অস্তিত্বও দেখা গেছে । কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মহাজনী ব্যবস্হার দাপটের কাছে এই সব ব্যাংকের সংখ্যা অতি সামান্য বলে ১৯৫০ সালে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করেন। এই সুপারিশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য। (১) গ্রামের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদান একই সংস্হার অধীনে হওয়া উচিত। (২) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যক শাখা স্তাপন প্রয়োজন ও ডাকঘরেও সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন করা দরকার । (৩) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয় করণ এবং (8) কেন্দ্রীয় কৃষিঋণ দান কর্পোরেশন গঠন করা আবশ্যক। এই সমস্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ করে তার নতুন নামকরণ করা হল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া । ১৯৬৯ সালে ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রথম জাতীয়করণ করা হয় ৷ তারপর এইসব ব্যাংককে তাদের শাখা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতেও বলা হয় । সেই অনুসারে ১৯৬৬ সালে গ্রামীণ শাখার যে সংখ্যা ছিল ১৮৩৩, ২০২০ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২১,৯৯৫ ।
বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রামীণ শাখাঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রামীণ শাখা বৃদ্ধি পেলেও গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না হওয়ায় ১৯৭৫ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক গ্রামীণ অর্থনীতির সার্বিক উন্নতির জন্য একটি কার্যকরী দল ( working group ) নিযুক্ত করেন। এই দল গ্রামীণ ঋণদানের সমস্যাগগুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সমবায় ঋণদান সমিতি ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সীমাবদ্ধতা কোথায় তা বিশ্লেষণ করেছেন । তাঁদের মতে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যয় আয়ের তুলনায় খুব আশাব্যঞ্জক নয় । দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ শাখাগুলি প্রধানতঃ আমানত জমার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঐ আমানত বিনিয়োগ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র গ্রামে না থাকায় ব্যাংকের ব্যবসায়িক দিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।
গ্রামীণ ব্যাংক—তাই ঐ working group গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এমন এক ধরনের আর্থিক সংস্হার পারিশ করেছেন যেখানে সমবায় সমিতির গ্রামীণ অভিজ্ঞতা থাকবে অথচ তার অপটুতা থাকবে না। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শিল্প বাণিজ্যিক তৎপরতা থাকবে কিন্তু, তার শহরমুখী প্রবণতা থাকবে না । এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশে কতকগুলি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন। এই ব্যাংকগুলি গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করবে । গ্রামের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষিজীবী, কৃষি শ্রমিক, কারিগর ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগীদের আর্থিক সাহায্য করবে। কৃষিজীবীদের উৎকৃষ্ট বীজ, আধুনিক কৃষি যন্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা এই শ্রেণীর ব্যাংকের করণীয় হবে । কৃষকদের কাছে পণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করা এবং বিভিন্ন স্বার্থসাধক সমিতির সঙ্গে কৃষিজীবীদের অর্থনৈতিক যোগ স্থাপন করাও এই জাতীয় ব্যাংকের লক্ষ্য ।
ভাসমান ব্যাংকঃ গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যতম অঙ্গ ভাসমান ব্যাংক । ১৯৭৫ সালের ২১শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংকের বিকল্প রূপে এর আত্মপ্রকাশ । “এম. ভি. রূপসী বাংলা” নামে একটি লঞ্চের উপর খোলা হয় এই ভাসমান ব্যাংক । সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত এই লঞ্চটি দক্ষিণ ২৪ পরগণার মোল্লাখালি থেকে রামপুর পর্যন্ত যাতায়াত করে গ্রামীণ মানুষের অভাব মেটাচ্ছে। ন্যাজাট গ্রামে স্থাপিত ইউ. বি. আই. ব্যাংকের শাখাকে কেন্দ্র করে এই ভাসমান ব্যাংকের প্রকল্প রচিত হয়েছে ।
উপসংহারঃ গ্রামীণ ব্যাংকের স্থাপনে গ্রামের কৃষককুলের সার্বিক কল্যাণ সাধন হয়েছে। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন গ্রামীণ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কাজ । মহাজনদের ঋণের নাগপাশ, জমিদারদের রক্তচক্ষর ভয়াল দৃষ্টি—হকুম তামিল করার হীনতা আর কৃষকদের করতে হবে না । কৃষকরা তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে এখন । পূর্বে ঋণ পরিশোধের ( মিথ্যা ? ) জন্য তাকে আর বেগার খাটতে হবে না । ক্ষুদ্রশিল্পীরা তাদের শিল্পসৃষ্টিতে মন দিতে পেরেছে। রাত পোহালে টাকার চিন্তায় মাথার শিরা আর তাদের টনটন করবে না। গ্রামীণ ব্যাংক আজ তাদের কাজকে গ্রামের প্রতিটি ঘরের দরজার সাহায্যের হাত ছড়িয়ে দিয়ে সত্যিই এক নবযুগের সৃষ্টি করেছে ।
অনরূপ প্রবন্ধঃ ভারতের উন্নতিতে ব্যাংকের অবদান ।
[ ভূমিকা — উন্নতির প্রধান অন্তরায় আর্থিক সমস্যা – বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক —ব্যাংক জাতীয়করণ—গ্রাম ও শহরে ব্যাংকের ঋণ দান – ঋণতায় ও আর্থিক সাহায্য আরও ব্যাপক প্রয়োজন – উপসংহার ]