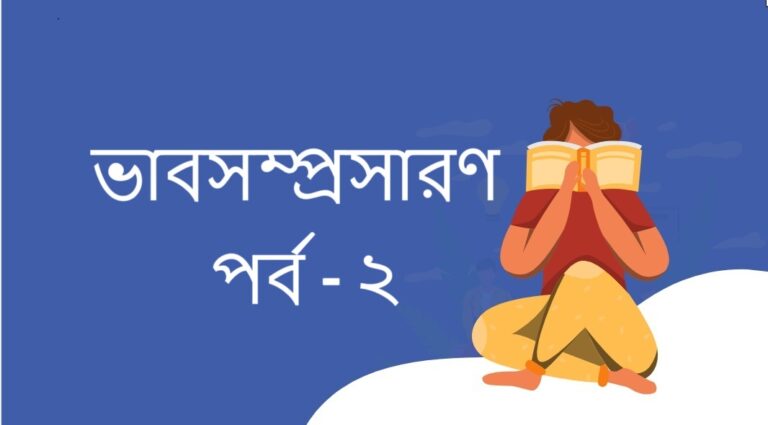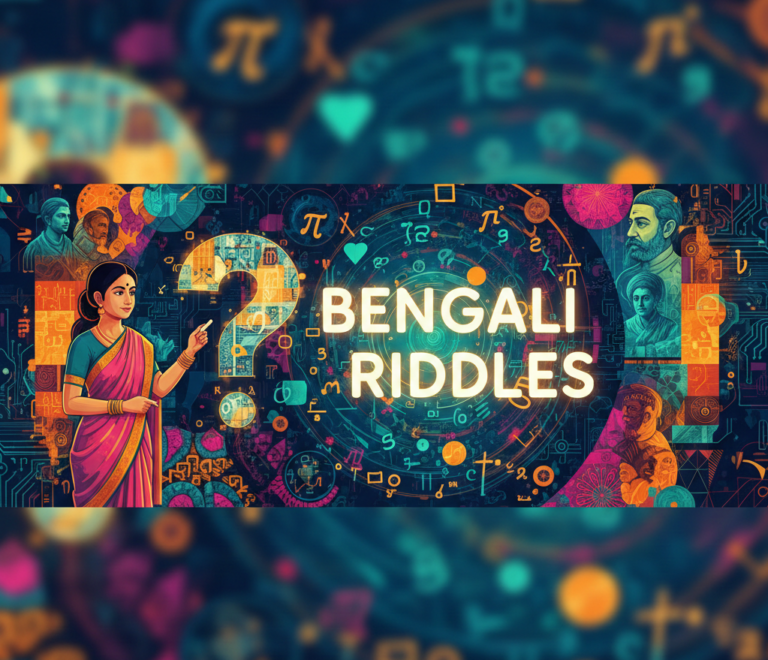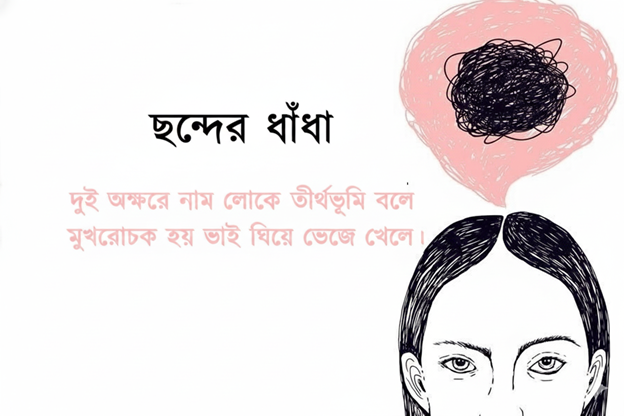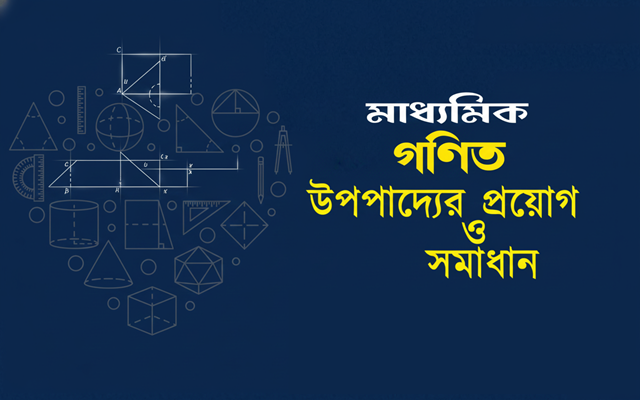উক্তি পরিবর্তন
উক্তি-পরিবর্তন | Ukti Poriborton in Bengali Grammar Notes to each chapter is provided in the list so that you can easily browse throughout different chapter উক্তি-পরিবর্তন | Ukti Poriborton in Bengali Grammar and select needs one.
উক্তি পরিবর্তন:জীবজগতে একমাত্র মানষই কথা বলে। এই ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কারুর নেই । একজন বলে; আর একজন শোনে। যে বলে সে বক্তা- যে শোনে সে শ্রোতা। সমাজ সংসার বক্তা আর শ্রোতাকে নিয়েই চলছে।বক্তা যখন অন্যের কথা শ্রোতার কাছে বলে, তখন সে তা দুভাবে বলতে পারে । এক নিজের জবানিতে এবং দুই অন্যে যে ভাবে বলেছে, হুবহু ঠিক সেইভাবে অন্যের জবানিতে। এই বলা ব্যাপারটাকেই বলে উক্তি।
উক্তি-(Narration):-বক্তার বাক্যটিতে অবিকৃতভাবে উদ্ধত করা বা প্রকাশকের নিজের কথায় রূপান্তরিত করে বলাকে ব্যাকরণে উক্তি বলে।বক্তা শ্রোতার সম্মুখে তাঁর বক্তব্য দুই প্রকারে উপস্থাপিত করতে পারে। — নিজস্ব উক্তিতে অথবা অপরের উক্তিতে। কাজেই, উক্তি দুই প্রকার: প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তি ।
১।প্রত্যক্ষ উক্তি: বক্তা যদি বক্তার উক্তি অপরিবর্তিত ভাবে হুবহু, বা সরাসরি শ্রোতার কাছে উপস্থাপিত করে, তবে তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে । অর্থাৎ বক্তার কথা নিজের ভাষাতেই পুনরুক্ত হলে তাকে বলে প্রত্যক্ষ উক্তি৷ যথা—শ্যামল বলল, “আমি অফিস যাচ্ছি।” আলেকজাণ্ডার পরু কে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি আমার নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন?” তুমি বললে “আমি ভাত খেয়েছিলাম।” নরেশ বললে, “আমি খেলা দেখছি।”
এই চারটি বাক্যে “আমি অফিস যাচ্ছি”, “আপনি আমার নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন”, “আমি ভাত খেয়েছিলাম” এবং “আমি খেলা দেখছি” উদ্ধৃতি চিহ্নের অংশগুলি, যা এক-একটি সম্পূর্ণ বাক্য, বক্তার কথা হুবহু, অননুসরণ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রধান ঝোঁক প্রত্যক্ষ উক্তির অনুকুলে।
২।পরোক্ষ উক্তি:বক্তার নিজের কথা হুবহু, পুনরুল্লেখ না করে অন্য ব্যক্তির কথায় বা জবানীতে মূলভাব জানানো হলে তাকে বলা হয় পরোক্ষ উক্তি । যথা—শ্যামল বলল যে সে অফিস যাচ্ছে। আলেকজান্ডার পুরু কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি তাঁর নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন। তুমি বললে যে তুমি ভাত খেয়েছিলে । নরেশ বললে যে সে খেলা দেখতে থাকবে।”
চারটি বাক্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি দেখা যাচ্ছে ।
(ক)উদ্ধৃতি চিহ্ন বর্জিত হয়েছে । (খ) প্রত্যক্ষ উক্তি যেখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে সেখানে ব্যবহৃত কমা বা প্রথমচ্ছেদ বর্জিত হয়ে আগমন ঘটেছে “যে” অব্যয়ের (গ) সর্বনাম পদে পুরুষের পরিবর্তন (উত্তম পুরুষ ‘আমি’ স্থলে প্রথম পুরুষ ‘সে’ ইত্যাদি)হয়েছে । (ঘ) সমাপিকা ক্রিয়াপদের পুরুষবাচক রূপের পরিবর্তন হয়েছে এবং কালরূপেরও পরিবর্তন (দেখছি-স্থলে ‘দেখতে থাকবে’ ) দেখা দিয়েছে ।
বাংলায় উক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম প্রচলিত নেই। আধুনিককালে ইংরেজী ভাষার রীতি অনুসরণ করে বাংলা-উক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে এগুলি ক্রমশঃ প্রচলিত হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বাংলা ভাষার ধর্ম— ইংরেজী পরোক্ষ উক্তির ঠিক অনুকূল নয়। ইংরেজীতে উক্তি পরিবর্তন ব্যাপারটি আরো বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। যথা—
Ram said, “I was coming,”
Ram said that he had been coming.
ইংরেজীতে সর্বনাম, ক্লিয়ার কাল, উদ্ধৃতি চিহ্ন প্রভৃতি পরিবর্তন সর্বস্তরে দেখা যায় । ইংরেজীতে প্রত্যক্ষ উক্তিকে বলে Direct Narration এবং পরোক্ষ উক্তিকে বলে Indirect Narration.
কালের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলা ভাষাতে প্রত্যক্ষ উক্তি বা পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার দুইই প্রচলিত হচ্ছে।তবে আজকাল অনেক বিখ্যাত লেখক এই “ ” উদ্ধরণ চিহ্নের ব্যবহার করছেন না, তাই আজকাল এই চিহ্ন না দেওয়ারই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে ।
প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের নিয়ম:
১।প্রত্যক্ষ উক্তিতে বাক্যের দুটি অংশ থাকে । বক্তা যে—কথা বলেছে সেই কথা অন্য ব্যক্তির কথার অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা নির্দেশিত হলে, সেই নির্দেশিত অংশকে বলা হয় ঘোষক অংশ (Reporting Speech); তার ক্লিয়াকে বলা হয় ঘোষক ক্রিয়া (Reporting Verb। বক্তার হুবহু, কথা বা বাক্যটিকে বলা হয় ঘোষিত অংশ (Reported Speech), তার ক্রিয়াকে বলা হয় ঘোষিত ক্রিয়া (Reported Verb) । ঘোষিত অংশের ভাষার অনুসরণে পরোক্ষ উক্তির ভাষা পরিবর্তিত করতে হয়। অর্থাৎ সাধু হলে সাধু, চলিত হলে চলিত ভাষা হবে ৷
২।প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কথাগুলি উদ্ধৃতি চিহ্নের (‘-‘ বা ‘–‘) মধ্যে থাকে এবং উদ্ধৃতি চিহ্নের পুর্বে প্রথম চ্ছেদ বসে। পরোক্ষ উদ্ধৃতি চিহ্ন বর্জিত হয়, এবং উক্তির আরম্ভে বসাতে হয় ‘যে’ সংযোজক অব্যয়। আজকাল বাংলায় উদ্ধতি চিহ্ন প্রায় থাকে না, আর বক্তার অদৃশ্য উপস্থিতি ধরে নিতে হয় ৷
৩।ঘোষিত অংশের উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষগুলি ঘোষক অংশের বচন ও কারকের সঙ্গে সংগতি রেখে সর্বনাম পদে পরিবর্তিত হবে। যেমন—
(ক) রমেশ বলিল, “আমি যাইতে পারিব না।” (প্রত্যক্ষ)
রমেশ বলিল ‘যে,’ ‘সে’ যাইতে পারিবে না।” (পরোক্ষ)
(খ) ইন্দ্রনাথ কহিল, “আর ভয় নাই; আমরা বড় গাঙে এসে পড়েছি।” (প্রত্যক্ষ)
ইন্দ্রনাথ কহিল ‘যে’, আর ভয় নাই, ‘কারণ’ ‘তাহারা’ বড় গাঙে আসিয়া পড়িয়াছে। (পরোক্ষ)
(গ) প্রত্যক্ষ উক্তির পুনরুক্ত অংশের ভাষা পরোক্ষ উক্তিতে প্রকাশকের ব্যবহৃত ভাষায় পরিবর্তিত হয়; অর্থাৎ প্রকাশকের অংশ যদি সাধুভাষার লিখিত হয়। তাহলে পরের অংশটিও সাধুভাষায় লিখতে হয়; আবার পূর্বেভাগ কথ্যভাষায় লিখিত হলে উত্তর ভাগ কথ্যভাষাতেই লেখা উচিত ।
এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রকাশকের অংশের ক্রিয়া অতীতকালের হলে পরোক্ষ উক্তিতে প্রত্যক্ষ উক্তির পুনরুক্ত অংশের ক্রিয়াও সাধারণতঃ অতীতকালের হয়ে থাকে।
দ্রষ্টব্য: প্রত্যক্ষ উক্তির কতকগুলি বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নোক্ত আকারে পরিবর্তিত হবে। যথা ,
এবার = সেবার
এখানে = সেখানে
যখন = তখন
গতকল্য = পূর্বে দিন
এখন =তখন
এই = সেই
এটা = সেটা
আজ ‘অদ্য = সেদিন / সেইদিন
আগামীকলা/কাল = পরদিন/পরেরদিন/পরদিবস
গতকাল = পূর্বেরদিন/পূর্বদিবস/আগের দিন
আসা = যাওয়া
গতরাত্র = পূর্বরাত্র
এস = যাও
এইরূপ|এরূপ = সেইরূপ/সেরূপ ইত্যাদি। যেমন—
সে লিখেছিল, “এবার খুবে আম হয়েছে।” (প্রত্যক্ষ)
সে লিখেছিল যে, সেবার খুব আম হয়েছিল। (পরোক্ষ)
রাম বলেছিল, “আমি ইহা করি।” (প্রত্যক্ষ)
রাম বলেছিল যে, সে তাহা করিল। (পরোক্ষ)
(ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তি প্রশ্নবাচক হলে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের সময় প্রকাশকের অংশের ক্রিয়ার পরিবর্তে “জিজ্ঞাসা করলেন”, “প্রশ্ন করলেন”, জানতে চাইলেন; ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় । যথা-
(১) সন্নাসী বললেন, “তুমি কে?” প্রত্যক্ষ)
সে কে তা সন্ন্যাসী জানতে চাইলেন । (পরোক্ষ)
(২) পরুষ বলল, ‘তোমার বাড়ী কোথায়?’ (প্রত্যক্ষ)
পুরুষ জিজ্ঞাসা করল তার বাড়ী কোথায়। (পরোক্ষ)
(৩) সে আমাকে বলল, “তুমি কি স্কুলে যাবে? (প্রত্যক্ষ)
সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি স্কুলে যাব কিনা। (পরোক্ষ)
(ঙ) আদেশ-বিস্ময়াদির ভাববোধক উক্তি প্রত্যক্ষ উক্তির ভাবানুযায়ী অন্য শব্দ বা শব্দসমষ্টি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
(১) আদেশ – বাবা বললেন, “যা বেরিয়ে যা এখনই বাড়ী থেকে।” (প্রত্যক্ষ)
বাবা (তাকে)বাড়ী থেকে সেই মুহুর্তেই বের হয়ে যাবার জন্য আদেশ করলেন।(পরোক্ষ)
(২) সম্বোধনঃ রহমত মিনিকে বলত,“খোঁখী, শ্বশুর-বাড়ী কখুনু যাবে না।” (প্রত্যক্ষ )
রহমত মিনিকে খোঁখী নামে সম্বোধন করে বলত সে যেন শ্বশুরবাড়ী কখনও না যায়।(পরোক্ষ)
দ্রষ্টব্য:বাংলা গদ্যের আধুনিক-পূর্ব যুগে পরোক্ষ ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না, কারণ প্রত্যক্ষ উক্তিই বাংলাভাষায় অধিক প্রচলিত রীতি। বাংলা গদ্যের উপর ইংরেজি গদ্যের প্রভাবের ফলে আধুনিক যুগে বাংলা গদ্যে পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।
বিভিন্ন প্রকার বাক্যের উক্তি পরিবর্তনের বিশেষ নিয়ম:
(১) নির্দেশাত্মক/ নির্দেশমূলক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন:
নির্দেশাত্মক বাক্যে সর্বনামে পুরুষের পরিবর্তন এবং অন্যান্য সাধারণ নিয়ম ছাড়া বিশেষ কিছু নিয়ম নেই ৷
প্রত্যক্ষ — দীপক বলল, “আমি বই পড়ছি।”
পরোক্ষ — দীপক বলল যে সে বই পড়ছে।
প্রত্যক্ষ — রমা বলল, “আমরা গতকাল বেড়াতে গেছলাম।”
পরোক্ষ— রমা বলল যে তারা আগের দিন বেড়াতে গেছল।
প্রত্যক্ষ — বলরাম বললেন, ‘আমি এই সভার অধ্যক্ষ, আমার আজ্ঞা অবশ্য পাল্য।’
পরোক্ষ — লরাম বললেন যে, তিনি ওই সভার অধ্যক্ষ, তাঁর আজ্ঞা অবশ্য পাল্য।
প্রত্যক্ষ — রামসুন্দর কহিলেন, ‘তা-হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।’
পরোক্ষ — রামসুন্দর সস্নেহে কহিলেন যে, তাহা হইলে তাহাকে আসিতে দিবে না।
প্রত্যক্ষ — রাজসিংহ বলিলেন, ‘আমি তোমার জীবন দান করিলাম।’
পরোক্ষ — রাজসিংহ বলিলেন যে, তিনি তাহার জীবন দান করিলেন।
প্রত্যক্ষ — অপূর্ব কহিল, ‘বেলা হয়ে গেল, আমি তবে চললুম কাকাবাবু’।
পরোক্ষ — অপূর্ব কাকাবাবুকে বেলা হইবার দরুন চলিয়া যাইবার কথা বলিল।
প্রত্যক্ষ — আগন্তুক অনুচ্চস্বরে বললেন, ‘মহারাজ, আমি সুবলপুত্র মৎকুনি, শকুনির বৈমাত্র ভ্রাতা’।
পরোক্ষ — আগন্তুক অনুচ্চস্বরে মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন যে, তিনি সুবলপুত্র মৎকুনি, শকুনির বৈমাত্র ভ্রাতা।
(২) প্রশ্নাত্মক/ প্রশ্নবোধক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন:
প্রশ্নাত্মক বাক্যে ঘোষক ক্রিয়া “প্রশ্ন করলেন/অনুসন্ধান করলেন/খোঁজ করলেন,নিলেন” প্রভৃতি রূপে পরিবর্তিত হয়। সংযোজক অব্যয় ‘যে’ প্রয়োজনবোধে ব্যবহৃত হবে। বাক্যের শেষে প্রশ্নাত্মক চিহ্নের (?) পরিবর্তে পূর্ণচ্ছেদ আসবে। ‘কিনা’ ( whether ) শব্দ প্রয়োগ করতে হয় কখনো-কখনো। সমগ্র বাক্যটিকে নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত করতে হবে ।
প্রত্যক্ষ — সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, “তোমার নাম কি?”
পরোক্ষ — সে আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল।
প্রত্যক্ষ – তুমি আমাকে বললে, “তুমি আমার বাড়ী কখন আসবে?”
পরোক্ষ – তুমি আমার নিকট খোঁজ নিলে আমি তোমার বাড়ী কখন যাব।
প্রত্যক্ষ — সর্দারজী শুধালেন, ‘অন্য কয়েদীরা চুপ করে রইল?”
পরোক্ষ – সর্দারজী জিজ্ঞেস করলেন যে, অন্য কয়েদীরাও চুপ করে ছিল কি না।
প্রত্যক্ষ — নিমাইবাবু কহিলেন, ‘তুমি গাঁজা খাও?’
পরোক্ষ -নিমাইবাবু সে গাঁজা খায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।
প্রত্যক্ষ — অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, ‘পলিটিক্যাল আসামী বুঝি?”
পরোক্ষ – অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল যে (লোকটি) পলিটিক্যাল আসামী ছিল কি না।
প্রত্যক্ষ — বেণী ধমক দিয়া কহিল, ‘পারবিনে কেন?’
পরোক্ষ -বেণী ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে (সে) পারিবে না কেন।
প্রত্যক্ষ — রমা মৃদুকণ্ঠে একবার মাত্র কহিল, ‘পারবে না আকবর?”
পরোক্ষ -রমা মৃদুকণ্ঠে একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিল যে, আকবর পারিবে কিনা।
(৩) অনুজ্ঞাবাচক/ অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন:
এই রীতির বাক্য-পরিবর্তনে ঘোষক ক্রিয়াটিকে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্য শব্দে রূপান্তরিত করতে হয়: অনুরোধ করলেন, আদেশ করলেন, উপদেশ দিলেন ইত্যাদি। এখানে সংযোজন অব্যয় ‘যে’ ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু, ‘পরামর্শ’, ‘প্রস্তাব’ প্রসংগ অনুসারে ব্যবহার করতে হয়।
প্রত্যক্ষ — আমি তাঁকে বলেছিলাম, “দয়া করে কিছ, টাকা ধার দিন।”
পরোক্ষ — আমি তাঁকে কিছু টাকা ধার দিতে অনুরোধ করেছিলাম।
প্রত্যক্ষ — সে আমাকে বলেছিল, “চলো বাড়ী যাই ।
পরোক্ষ — সে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে আমাদের বাড়ী যাওয়া উচিত।
প্রত্যক্ষ — একদিন রামেন্দ্রসুন্দরকে কহিল, ‘বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।’
পরোক্ষ — একদিন রামেন্দ্রসুন্দরকে বক্তা তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য খুবই অনুরোধ করিল।
প্রত্যক্ষ — দস্যু বলিল, ‘মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।
পরোক্ষ — দস্যু মহারাজকে ওই দণ্ড মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করিল।
প্রত্যক্ষ — মৎকুনি জিহ্বা দংশন করে বললেন, ‘ওকথা আর তুলবেন না মহারাজ। আমার বক্তব্য সবটা শুনুন।’
পরোক্ষ — মৎকুনি জিহ্বা দংশন করে মহারাজকে ওকথা আর না তুলতে ও তাঁর বক্তব্য সবটা শোনার জন্যে অনুরোধ করলেন।
প্রত্যক্ষ — রাজসিংহ বলিলেন, ‘মাণিকলাল, তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুর যাও।’
পরোক্ষ — রাজসিংহ মাণিকলালকে তাহার কন্যা লইয়া উদয়পুর যাওয়ার জন্য আদেশ করিলেন।
প্রত্যক্ষ — প্রশ্নকর্তা বলিলেন, ‘আপনি এইখানে থাকুন।’
পরোক্ষ — প্রশ্নকর্তা তাহাকে ওইখানে থাকিবার জন্য উপদেশ দিলেন।
(৪) প্রার্থনাসূচক/ প্রার্থনাসূচক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন:
এই রীতির বাক্যের ঘোষক ক্রিয়াটিকে ‘প্রার্থনা করলেন’, ‘ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করতে হয় এবং ক্রিয়ার পর যেন, যাতে ব্যবহৃত হয় এবং প্রয়োজনে ‘যে’ অব্যয় ব্যবহৃত হতে পারে।
প্রতাক্ষ — সে তোমাকে বলল, “ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।”
পরোক্ষ — সে প্রার্থনা জানাল যেন ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করেন।
প্রত্যক্ষ — সে আমাকে বলল, “তুমি সুখী হও।”
পরোক্ষ — সে প্রার্থনা জানাল/ইচ্ছা প্রকাশ করল যাতে আমি সুখী হতে পারি।
প্রত্যক্ষ — মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, ‘মহারাজাধিরাজ, আমার জীবন দান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত।’
পরোক্ষ — মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে সে শরণাগত বলিয়া মহারাজাধিরাজকে তাহার জীবন দান করিতে ও তাহাকে রক্ষা করিতে প্রার্থনা জানাইল।
প্রত্যক্ষ — মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, ‘মহারাজাধিরাজ! অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডের বিধান করুন।’
পরোক্ষ — মাণিকলাল বিনীতভাবে মহারাজাধিরাজকে অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রতি লঘু দণ্ডের বিধান করিতে প্রার্থনা করিল।
প্রত্যক্ষ — রমণী কহিল, ‘শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।’
পরোক্ষ — রমণী শৈলেশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইল যে, তিনি যেন তাঁহার মঙ্গল করেন।
প্রত্যক্ষ — নরেন্দ্রনাথ দেবীকে বলিলেন, ‘মা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।’
পরোক্ষ — নরেন্দ্রনাথ দেবীর কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, দেবী যেন তাঁহাকে শুদ্ধা ভক্তি দেন।
প্রত্যক্ষ — তিনি বলিলেন, “ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।’
পরোক্ষ — তিনি ঈশ্বরের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন।
(৫) বিস্ময়াদিসূচক/ বিস্ময়াদিসূচক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন:
এই রীতির বাক্যে ঘোষক ক্রিয়াটি বিস্ময়, হর্ষ’, প্রার্থনা ইত্যাদি অর্থে পরিবর্তিত করে বাক্যটিকে নির্দেশাত্মক করতে হয় এবং “যে” এই সংযোগমূলক অব্যয় ‘যে’ ব্যবহৃত হয়।
প্রত্যক্ষ — রমা বলল, “সে কি! ঘরে যে সব বাড়ন্ত।”
পরোক্ষ – রমা বিস্ময় প্রকাশ করে জানাল যে ঘরে সব বাড়ন্ত ।
প্রত্যক্ষ—সে বলল, “কী সুন্দর দৃশ্য।”
পরোক্ষ —সে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল যে দৃশ্যটি সুন্দর।
প্রত্যক্ষ — নিমাইবাবু কহিলেন, ‘দেখো বাবা, এসব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না।’
পরোক্ষ -নিমাইবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া ওইসব কথা কোথাও প্রকাশ করিতে তাহাকে নিষেধ করিলেন।
প্রত্যক্ষ — আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, ‘সাবাস! হ্যাঁ—মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু। লাঠি ধরলে বটে!’
পরোক্ষ আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া মুগ্ধ ও সপ্রশংসকণ্ঠে ছোটবাবু যে যথার্থই মায়ের দুধ খাইয়াছিল তাহা বলিয়া তাহার (ছোটবাবুর) লাঠি ধরিবার কৃতিত্বের কথা বলিয়াছিল।
প্রত্যক্ষ — শাশুড়ী ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, ‘শ্রী তো ভারি! যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।’
পরোক্ষ – শাশুড়ী ঝংকার দিয়া উঠিয়া তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে বলিল যে, উহা আদৌ শ্রী নহে। যেমন ঘরের মেয়ে শ্রীও তেমনই হয় জানাইয়া সে আরও বিরক্তি প্রকাশ করিল।
প্রত্যক্ষ —নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, ‘আগে তো পাই!’
পরোক্ষ -নিমাইবাবু আগে পাওয়া যায় কিনা তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিলেন।
প্রত্যক্ষ —জগদীশবাবু চটিয়া কহিলেন, ‘দয়ার সাগর! পরকে সেজে দিই, নিজে খাইনে! মিথ্যেবাদী কোথাকার!’
পরোক্ষ -জগদীশবাবু চটিয়া দয়ার সাগর বলিয়া (তাহাকে) ব্যঙ্গ করিলেন। পরকে সাজিয়া দেয়, নিজে খায় না বলিয়া উপহাস করিলেন এবং মিথ্যাবাদী বলিয়া ধমক দিলেন।
পরোক্ষ উক্তি হতে প্রত্যক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ–
(১)পরোক্ষ—আলেকজান্ডার যখন পুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাঁহার কাছে কিরূপে ব্যবহার আশা করেন; পুরু, তখন সগর্বে উত্তর দিলেন যে, তিনি রাজার মত ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন ।
প্রত্যক্ষ — আলেকজাণ্ডার যখন পুরু, কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার কাছে কিরূপে ব্যবহার আশা করেন?”পুরু, তখন সগর্বে — উত্তর দিলেন, “রাজার মত ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি।”
(২) পরোক্ষ — অর্ধরাত্রে ঝটিকা বৃষ্টি নিবারণ হইলে যুবক তাঁহাদিগকে চিন্তা না করিতে বলিলেন।তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, পরদিন প্রাতে তিনি তাঁহাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিবেন ।
প্রত্যক্ষ — অর্ধরাত্রে ঝটিকা বৃষ্টি নিবারণ হইলে, যবক কহিলেন, “চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।”
উক্তি-পরিবর্তনের আরও কিছু নমুনা
প্রত্যক্ষ:যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে আপনি সৌম্য?’ আগন্তুক উত্তর দিলেন, ‘মহারাজ, ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আমার বক্তব্য কেবল রাজকর্ণে নিবেদন করতে চাই।’ যুধিষ্ঠির বললেন, ‘সহদেব, তুমি এখন যেতে পার।’
পরোক্ষ:যুধিষ্ঠির সেই সৌম্য কে ছিলেন জানতে চাইলেন। উত্তরে আগন্তুক মহারাজাকে তাঁর ধৃষ্টতা ক্ষমা করতে অনুরোধ করে তাঁর বক্তব্য কেবল রাজকর্ণে নিবেদন করতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির সহদেবকে তখন চলে যাবার আদেশ করলেন।
প্রত্যক্ষ:ভীষ্ম বললেন, ‘মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, এই সভায় দ্যূতনীতিবিরুদ্ধ কোনও কর্ম যাতে না হয় তার বিধান আপনার কর্তব্য। আমি প্রস্তাব করছি শ্রীকৃষ্ণকে সভাপতি নিযুক্ত করা হক।’ দুর্যোধন আপত্তি তুললেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষপাতী।’ কৃষ্ণ বললেন, ‘কথাটা মিথ্যে নয়। আর আমার অগ্রজ উপস্থিত থাকতে আমি সভাপতি হতে পারি না।’
পরোক্ষ:ভীষ্ম মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ওই সভায় দ্যূতনীতিবিরুদ্ধ কোনও কর্ম যাতে না হয় তার বিধান যে তাঁর কর্তব্য তা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সভাপতি নিযুক্ত করার প্রস্তাবের কথাও বললেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষপাতী বলে দুর্যোধন আপত্তি তুললেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করলেন যে তাঁর (দুর্যোধনের) কথাটা মিথ্যে নয়। আর তাঁর অগ্রজ উপস্থিত থাকতে তিনি যে সভাপতি হতে পারেন না, তাও বললেন।
প্রত্যক্ষ:শকুনি তাঁর পাশাটি মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, ‘আমার অক্ষ কাকেও স্পর্শ করতে দেব না।’বলরাম বললেন, ‘আমি এই সভার অধ্যক্ষ, আমার আজ্ঞা অবশ্য পাল্য।’ শকুনি উত্তর দিলেন, ‘আমি তোমার আজ্ঞাবহ নই।’
পরোক্ষ:শকুনি তাঁর পাশাটি মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন যে, তাঁর অক্ষ কাকেও স্পর্শ করতে দেবেন না। উত্তরে বলরাম বললেন যে, তিনি ওই সভার অধ্যক্ষ, তাঁর আজ্ঞা অবশ্য পালা। শকুনি উত্তর দিলেন যে, তিনি তাঁর আজ্ঞাবহ নন।
প্রত্যক্ষ:যুধিষ্ঠির উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, দ্যূতপ্রসঙ্গে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। আমরা যুদ্ধ করেই হৃতরাজ্য উদ্ধার করব। জ্যেষ্ঠ তাত, প্রণাম, আমরা চললাম।’
পরোক্ষ:যুধিষ্ঠির উত্তেজিত হয়ে বললেন যে তিনি কোনও কথা শুনতে চান না, দ্যূতপ্রসঙ্গে তাঁর ঘৃণা ধরে গেছে।তাঁরা যুদ্ধ করেই হৃতরাজ্য উদ্ধার করবেন। এরপর জ্যেষ্ঠ তাতকে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের চলে আসার কথা জানালেন।
প্রত্যক্ষ:ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কার জয় হল?বলরাম বললেন, ‘যুধিষ্ঠিরের। দুই পক্ষই কূট পাশক নিয়ে খেলেছেন, অতএব কপটতার আপত্তি চলে না।’ যুধিষ্ঠির তখন জনান্তিকে বলরামকে মৎকুনির বৃত্তান্ত জানালেন। বলরাম তাঁকে বললেন, ‘আপনার কুণ্ঠার কিছুমাত্র কারণ নেই। কুট পাশকের ব্যবহার দ্যুতবিধিসম্মত।’
পরোক্ষ:ধৃতরাষ্ট্র কার জয় হল জানতে চাইলেন। উত্তরে বলরাম যুধিষ্ঠিরের কথা বললেন।তিনি আরও জানালেন যে, দুই পক্ষই কূট পাশক নিয়ে খেলেছিলেন, অতএব কপটতার আপত্তি চলে না। যুধিষ্ঠির তখন জনান্তিকে বলরামকে মৎকুনির বৃত্তান্ত জানালেন। উত্তরে বলরাম তাঁকে বললেন যে, তাঁর কুণ্ঠার কিছুমাত্র কারণ নেই। কূট পাশকের ব্যবহার যে দ্যুতবিধিসম্মত তাও তিনি বললেন।
প্রত্যক্ষ:মৎকুনি বললেন, ‘মহারাজ, স্থিরো ভব, আপনার সমস্ত সংশয় আমি ছেদন করছি।যদি আপনি ধৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষ নিয়ে খেলেন তবে আপনার পরাজয় অনিবার্য। ধূর্ত শকুনি সে অক্ষ খেলবে না, হাতে নিয়েই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় বদলে ফেলে নিজের আগেকার অক্ষেই খেলবে।’
পরোক্ষ:মৎকুনি মহারাজকে স্থির হতে বলে ও তাঁর সমস্ত সংশয় ছেদন করার কথা জানিয়ে বললেন যে, যদি তিনি ধৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষ নিয়ে খেলেন তবে তাঁর পরাজয় অনিবার্য। তিনি আরও জানালেন যে, ধূর্ত শকুনি ওই অক্ষে না খেলে হাতে নিয়েই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় বদলে ফেলে নিজের আগেকার অক্ষেই খেলবে।
প্রত্যক্ষ:নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, ‘তোমার নাম কি হে?’ ‘আজ্ঞে, গিরিশ মহাপাত্র।’ ‘একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতে কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স-বিছানা ত খানাতল্লাসী হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাক এবং পকেটে কি আছে?’
পরোক্ষ:নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহার নাম কি জানিতে চাহিলেন। উত্তরে (সে) বিনীতভাবেগিরীশ মহাপাত্র বলিয়া পরিচয় দিল। নিমাইবাবু মহাপাত্র উপাধিটিকে সামান্য ঠাট্টা করিয়া সেও তেলের খনিতে কাজ করিতেছিল কিনা তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিলেন। তাহার বাক্স-বিছানা যে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে তাহা জানাইয়া তাহার ট্যাক এবং পকেটে কি ছিল তাহা দেখিতে চাহিলেন।
প্রত্যক্ষ:নিমাইবাবু কহিলেন, ‘তুমি গাঁজা খাও?’ লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, ‘আজ্ঞে না।’ ‘তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?
পরোক্ষ:নিমাইবাবু সে গাঁজা খায় কিনা জানিতে চাহিলেন।লোকটি অসঙ্কোচে বিনীতভাবে তাহার অসম্মতি জানাইল। নিমাইবাবু ওই বস্তুটি অহেতুক পকেটে রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।
প্রত্যক্ষ:অপূর্ব প্রশ্ন করিল, ‘আপনি এখন কোথায় যাবেন?” ‘জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।’ ‘চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?’
পরোক্ষ:অপূর্ব জানিতে চাহিল তিনি তখন কোথায় যাইবেন। উত্তরে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জাহাজ ঘাটে যাওয়ার কথা বলিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য (অপূর্বকে) স্নেহের দাবি জানাইলেন। অপূর্ব সম্মতি জানাইয়া তাঁহাকে আর কোথাও যাইতে হইবে কিনা তাহাও জানিতে চাহিল।
প্রত্যক্ষ:রাজপুত বলিলেন, ‘তুমি আমাকে চেন?’ দস্যু বলিল, ‘মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে?’ তখন রাজসিংহ বলিলেন, ‘আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের সর্বস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্মে পতিত হইব।’
পরোক্ষ:রাজপুত সে (দস্যু) তাঁহাকে চিনে কিনা জানিতে চাহিলেন। দস্যু মহারাণা রাজসিংহকে যে সবাই চিনে তাহা বলিল। তখন রাজসিংহ বলিলেন যে, তিনি তাহার জীবন দান করিলেন। কিন্তু সে ব্রাহ্মণের সর্বস্ব হরণ করিয়াছিল। তিনি যদি তাহাকে কোন প্রকার দণ্ড না দেন, তবে তিনি রাজধর্মে পতিত হইবেন।
প্রত্যক্ষ:দস্যু বলিল, ‘এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুত কুলের কলঙ্ক।’ রাজসিংহ বলিলেন, ‘মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্যে নিযুক্ত হইলে, এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে – তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।’
পরোক্ষ:দস্যু বলিল যে ওই অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ, সে রাজপুতকুলের কলঙ্ক। রাজসিংহ মাণিকলালকে সেইদিন হইতে তাঁহার কার্যে নিযুক্ত হইবার আদেশ দিলেন। ওইক্ষণে সে অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইল জানাইলেন এবং তাহার কন্যা লইয়া উদয়পুর যাইতে হুকুম করিলেন। তিনি তাহাকে ভূমি দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন ও বাস করিবার অনুমতি দিলেন।
প্রত্যক্ষ:মাণিকলাল বলিল, ‘ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জনা করিবেন।’
পরোক্ষ:মাণিকলাল বলিল যে ব্রাহ্মণের যাহা তাহারা কাড়িয়া লইয়াছিল তাহা শ্রীচরণে অর্পিত হইল।সে আরও জানাইল যে, পত্র দুইখানি তাঁহারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছিল ওই অপরাধ মার্জনা করিবার সে অনুরোধ করিল।
প্রত্যক্ষ:তাপসীরা কহিতে লাগিলেন, ‘বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি; তুমি কেন অকারণে উহারে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, শান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও।’
পরোক্ষ:তাপসীরা সস্নেহে বৎসকে বলিতে লাগিলেন যে ওই সকল জন্তুকে তাঁহারা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন, তাঁহারা আরও জানিতে চাহিলেন যে সে কেন অকারণে উহাদের ক্লেশ দেয়। তাঁহাদের কথা শুনিতে, শান্ত হইতে ও সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহারা আদেশ করিলেন।
প্রত্যক্ষ:পরে রাজা তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, ‘এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; তবে এই বালক কি সংযোগে এখানে আসিল?’ তাপসী কহিলেন, ‘ইহার জননী অপ্সরা সম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন।’
পরোক্ষ:পরে রাজা তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহিলেন যে, উহা দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে;তবে ওই বালক কি সংযোগে ওখানে আসিল। তাপসী বলিলেন যে উহার জননী অপ্সরা সম্বন্ধে ওখানে আসিয়া ওই সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন।
প্রত্যক্ষ:রামসুন্দর বলিলেন, “ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি, তা-হলে তোর বাপের অপমান। আর তোরও অপমান।’নিরু কহিল, ‘টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।’
পরোক্ষ:রামসুন্দর স্নেহকাতর কণ্ঠে বলিলেন যে, অমন কথা বলিতে নাই। আর ওই টাকাটা যদি তিনি না দিতে পারেন তাহা হইলে তাহার বাপের অপমান। আর তাহারও অপমান। নিরু উত্তরে বলিল যে, টাকা দেওয়া হইলেই অপমান। তাঁহার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নাই! সে কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ তাহার দাম!